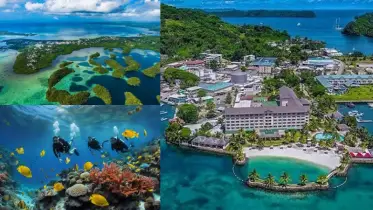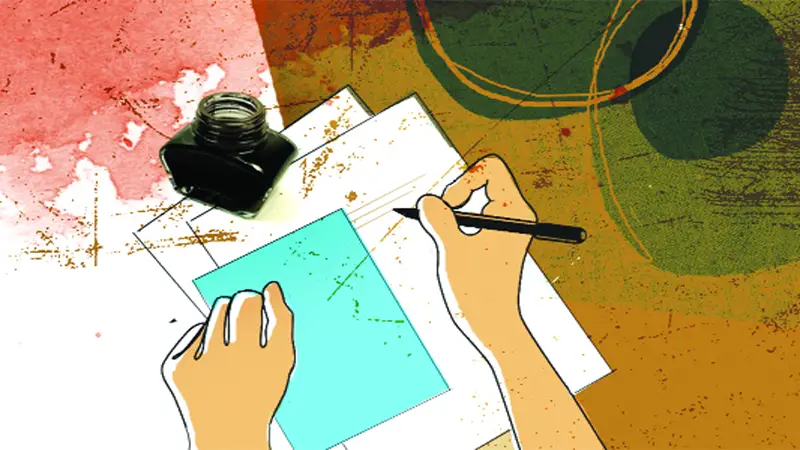
সাহিত্য হলো এক ধরনের নির্মিতি বা সৃজন প্রক্রিয়া
সাহিত্য হলো এক ধরনের নির্মিতি বা সৃজন প্রক্রিয়া, যা লিখিত আকারে বাঙময় হয়। এ সূত্রে সাহিত্যের সাথে সাহিত্যিকের স্মৃতি-সত্তার যোগসূত্র অনেকটা অলঙ্ঘনীয়। আসলে স্মৃতিই তো সাহিত্য। অভিজ্ঞতা, আলাপচারিতা, পাঠ- এসবের মাধ্যমে মননে বয়ে চলা স্মৃতির নির্যাস থেকেই তো তৈরি হয় একজন সৃজনশীল সাহিত্যিকের সৃজন-মননের আলোকিত ভুবন।
সঙ্গতকারণেই সাহিত্যে স্মৃতিকাতরতাকে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। বরং বলা চলে, সাহিত্যের সব ধারাই স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা অবলম্বনে গড়ে ওঠে। সাহিত্য আসলে বহুমাত্রিক অতীত স্মৃতির যোগফলের সাম্প্রতিকতা মাত্র।
মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্মৃতিপ্রবণ। মানুষের মনের কাজই যেন স্মৃতি রোমন্থন। অতীত স্মৃতিতে অবগাহন ছাড়া যেন মানুষের মনের কোনো কাজ নেই। শুধু মানুষ কেন পশু-পাখিও স্মৃতির সাথে বসত করে। একটি পরিণত বয়সের কুকুরকে কিছু দূরে ফেলে আসলে সে ঠিকই মনিবের দেয়া আশ্রয় খুঁজে নেয়।
পরিযায়ী পাখি খরায় খাবারের খোঁজে দেশান্তরী হলেও স্মৃতিতে ধরে রাখা পথ বেয়েই সে আবার নিজভূমে নিরাপদে ফিরে আসে। জীবনের সাথে স্মৃতি বন্ধন এতটাই নিবিড় যে, স্মৃতির চর্চায় ফেলে আসা নিবিড় মুহূর্ত শুধু পুনরুজ্জীবিতই হয় না, বরং প্রাণ পায়। আর হয়ে ওঠে সময়ের বহমান প্রবাহের দ্যোতক। স্মৃতি আসলে অস্তিত্বেরই নামান্তর, যা নিঃশব্দে সর্বত্রগামী হয়।
স্মৃতির, স্মৃতি কাতরতার এই সর্বত্রগামিতার মাঝেই উপ্ত রয়েছে সাহিত্য সৃজনের বিপুল ঐশ্বর্য্যময় সম্ভার। স্মৃতি কাতরতা চেতনার জগৎকে আলোড়িত করে নতুন সৃজনে অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করে। মানুষের জীবনে এসব স্মৃতির কোনো কোনোটা কাতরতা সৃষ্টিকারী বেদনা বিধুর, কোনো কোনোটা তরতাজা রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফকফকা, কোনো কোনোটা প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশী, আবার কোনো কোনোটা সুপ্ত প্রায় লুপ্ত- ফ্রিজে রাখা পণ্যের মতো হিমশীতল।
তবে জাগ্রত ‘স্মৃতিকাতর-সত্তা’ সবসময়ই ক্রিয়াশীল থাকে। মানুষের জীবনে যা কিছু কাক্সিক্ষত ও মহৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্মৃতি তা ধারণ করে রাখে। স্মৃতিকাতরতা অনুভবগম্য হয়ে উঠলে তা সাহিত্যে স্থান করে নেয়। স্মৃতির জন্ম তো ‘অতীত; এর ঘরেই। অতীত হয়ে যাওয়া সময়ের প্রতি বিলাপী আকুতিই তো স্মৃতিকাতরতা। ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২-১৯৪০) বলেছেন, ‘মানুষ অতীতের পকেটেই থাকে। সেখান থেকে নিয়ে সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বানায়।’ সুইডিস কবি টমাস ট্রান্সটোমারের কথায়,
‘আমার ছায়া বয়ে নিয়ে যায় আমাকে/
যেমন কালো বড় খাপে বাহিত হয়/
একটি ভায়োলিন’
‘স্মৃতিকাতরতা’ এর ইংরেজি পরিভাষা ‘নস্টালজিয়া’ শব্দটির গ্রিক মানে ‘নোস্তোস’ (ঠঙঙঞঙঈ), যার অর্থ ‘বাড়িতে ফিরে আসা’। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘স্মৃতিকাতরতা’ একটি স্বাধীন ইতিবাচক আবেগ, যা মানুষ প্রায়ই অনুভব করে। বর্তমান সময়ে ‘স্মৃতিকাতরতা’ একরৈখিক কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ এর সাথে রয়েছে সৃষ্টির প্রসব বেদনা সিক্ত বহুমুখীন চেতনাগত বিস্ময়। এটি হতে পারে ব্যক্তি,বস্তু, স্থান, প্রকৃতি, ঘটনা, সময়, এমনকি স্বপ্ন প্রসূতও, যা সৃজনী সামর্থ্যে পরিশীলিত।
সাহিত্যে এটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। এর আতুরঘরেই ঘাপটি মেরে থাকে সৃজনের বীজতলা। এজন্যই এরিক স্যান্ডবার্গ বলেছেন, ‘সাহিত্যে তার সহজাত নিয়মেই একটি স্মৃতিকাতর শিল্প, প্রায়শই, যদিও সর্বতোভাবে নয়,।’ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, ‘পকেটে যার শৈশব নেই, প্রতিভা নদীতে সে যেন সাঁতরাতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে।’ রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র কথায়,
‘ডেকে ওঠো যদি স্মৃতিভেজা ম্লান স্বরে,
উড়াও নীরবে নিভৃত রুমালখানা।
পাখিরা ফিরবে পথ চিনে চিনে ঘরে’।
‘স্মৃতিকাতরতা’ আসলে অতীত নির্ভর বিষয়, তবে তা কখনোই অতীতকে পুরাপুরি ফিরিয়ে আনতে পারে না। অবশ্য ‘স্মৃতিকাতরতা’র পথ বেয়েই পুনঃনির্মাণ হয় সাহিত্যে।
স্মৃতিকাতরতা মানুষের সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় করে তোলে। বিষয়টি সাহিত্যে এতটা প্রভাবক যে, এটি ধারণ করে কবি- লেখক একদিকে যেমন নতুন সৃজনে মেতে ওঠেন, অন্যদিকে তেমনি এটিতে আপ্লুত হয়ে পাঠক ফিরে পান নিজের হারানো স্মৃতির নান্দনিক ভুবন। স্মৃতিকাতরতার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে সাহিত্যে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ ‘সাহিত্য প্রবণতা’ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ফলত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সংগীত, নাটক- সর্বত্রই স্মৃতিকাতরতার দাপট লক্ষণীয়।
সাহিত্যে স্মৃতিকাতরতার প্রথম নমুনা হিসেবে দেখা হয় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে অন্ধকবি হোমার রচিত গ্রিক মহাকাব্য ওডিসিকে। এতে ইথাকার রাজা অডিসিয়ুসের দীর্ঘ দশ বছরের গ্রিক- ট্রোজান যুদ্ধ শেষে ট্রয় থেকে প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসার পূর্বাপর স্মৃতিকাতরতার বিষয়টি উঠে আসে, যেখানে রয়েছে তার পিতা-স্ত্রী- একমাত্র সন্তানসহ প্রিয় স্বদেশ, ‘ইথাকা, মন তো পড়ে আছে সেই ইথাকাতেই’।
টি. এস. এলিয়ট তার কালজয়ী প্রবন্ধ ‘Tradition and the Individual Talent’ এ স্মৃতিকাতরতাকে ‘ঐতিহাসিক অনুভব’ উল্লেখ করে একজন কবির মধ্যে ‘মহাকালে তার অবস্থান, নিজের সাম্প্রতিকতা সম্পর্কে সুতীক্ষè সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে এটির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলেছেন। তিনি ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মৃতির সাথে তার যুক্ততাকে বজায় রেখেই সেটিকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নেয়ার পক্ষে ছিলেন। তার বিশ্ব কাঁপানো কবিতা ‘ওয়েস্ট ল্যান্ড’ সভ্যতার মুমূর্ষু ছবি, জীবনের নানা জটিলতার সংহত প্রকাশ।
বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, ফররুখ, আবুল হাসানের মধ্যে কিছুটা স্মৃতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট নতুন পথের ইংগিত লক্ষ করা গেলেও তা ইউরোপের মতো বিশ্ব নাড়া দেয়া সাহিত্য তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে নি। এর পেছনে অন্য কারণের সাথে রয়েছে বাঙালির ব্যক্তিগত স্মৃতিনির্ভর ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য প্রীতি। অথচ ব্যক্তিগত ভাব-অনুভূতিকেও ঐতিহ্য ও নৈব্যক্তিকতার চেতনায় বহুজনীনতার ব্যঞ্জনা দেয়া সম্ভব। আশার কথা, একবিংশ শতকে এসে বিশ্বায়নের তরঙ্গে বাঙালি এ পথেই হাঁটছে।
সাহিত্য সৃজনে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই স্মৃতিকাতরতার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী, প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য, মঙ্গলকাব্যের বারোমাসি কবিতা অনেকটা স্মৃতিকাতরতায় বোনা।
স্মৃতিকাতরতা নিয়ে কিছু কবিতা বাংলা সাহিত্যে মনুমেন্ট হয়ে শিরদাঁড়া করে আছে। যেমন- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘পরাণের গহীন ভেতর’, আবুল হাসানের ‘যে তুমি হরণ করো’, রফিক আজাদের ‘চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া’, শহীদ কাদরীর ‘তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা’ ইত্যাদি। বাংলা কবিতায় স্মৃতিকাতরতা এত বিস্তৃত ডানা মেলেছে যে - দীর্ঘ আলোচনা না করেও বলা যায়, কবিতা সৃজনে স্মৃতিকাতরতা এক উর্বর বীজতলা, যা নিরন্তর সৃজনে মত্ত।
গল্প-উপন্যাসের জমিন, যাপিত জীবন- জগতের জমিন। এ জমিনের বুননে মনোজগতের ‘স্মৃতি-বিস্মৃতি’ চিন্তার অন্তহীন সূত্রধর ও আদিকল্পের উৎস ভূমি। বস্তুত স্মৃতিকাতরতা চেতনাজগতকে এমনই মথিত করে যে তা সাহিত্য চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করে, যা নতুন সৃজনে প্ররোচিত করে। এ ধরনের স্মৃতিকাতর উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো জেমস জয়েসের ‘শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস’ ‘ইউলিসিস’, যাকে ‘কঠিন ও দুষ্প্রবেশ্য সাহিত্য’ অথচ মানবজীবনের প্রকৃত চেহারার মহান উন্মোচক হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের এযাবৎকালের সেরা কাজ বলে গণ্য করা হয়।
স্মৃতি- কল্পনার মিশেলে লিখিত উপন্যাসটি একটি মাত্র দিন ১৯০৪ সালের ১৬ জুনে ডাবলিন শহরে ১৭ ঘণ্টার ঘটনাক্রম নিয়ে আবর্তিত। এতে নায়ক লিওপোল্ড ব্লুম, তার স্ত্রী মলি ব্লুম রয়েছেন কাহিনি কেন্দ্রে। মলি ব্লুম চরিত্রটি গড়ে উঠেছে জয়েসের স্ত্রী নোরা বার্নাকলের ছায়া অবলম্বনে, ১৯০৪ সালের ১৬ জুন যার সাথে জয়েস ডাবলিনের এক পার্কে নির্জন বেঞ্চে বসে সাক্ষাৎ করেছিলেন; যা পরবর্তীতে প্রেমপত্র বিনিময়, বিয়েতে গড়িয়েছিল।
এই একটি মাত্র স্মৃতিময় বিশেষ দিনকে ভাষার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য চমৎকারিত্বে দুমলাটে আবদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়। অথচ এ কঠিন কাজটিই তিনি করলেন। ২ লক্ষ ৬৫ হাজার শব্দের ৭৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি তিনি লেখা শুরু করেন ১৯১৪ সালে, যা শেষ হয় ১৯২১ সালে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের ‘শেক্সপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি’ থেকে।
গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি ডাবলিনে ছিলেন না, বহু বছর আগে থেকেই তিনি প্যারিস প্রবাসে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, প্যারিসে বসেই স্মৃতির ভেতর থেকে তিনি ডাবলিন শহরকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যাতে ডাবলিনের পানশালা, হোটেল, বেশ্যালয়, অলিগলি, রাস্তাঘাট, পরিবেশ, আবহাওয়া, দৃশ্য- সবকিছুই জীবন্ত। জয়েসের স্মৃতি থেকে নির্মিত ধ্রপদি ঘরানার এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ডাবলিনের বর্ণনা।
আপনি এই উপন্যাসটি যেখানে বসেই পড়ুন না কেন চোখের সামনে ডাবলিনকে দেখতে পাবেন। এজন্য জয়েস বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ তার ইউলিসিস পড়েই ডাবলিন শহরটিকে ফের হুবহু নির্মাণ করতে পারবে।
স্মৃতিকাতরতাকে কাহিনি কেন্দ্রে নিয়ে ফরাসি কথাসাহিত্যিক মার্শেল প্রাউস্ত রচনা করেন ‘ইন সার্চ অব লস্ট টাইম’ (১৯১৩-১৯২৭) উপন্যাস। সাত খ-ে রচিত এ উপন্যাসের কথকের স্মৃতিকাতরতা মেদুর আকুতি, “আমি যে বাস্তবতাকে চিনতাম এখন তার কোনো অস্তিত্ব নেই।...আর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সদর সড়ক, হায় পুরোনো বছরগুলোর মতোই পলাতক।
“এভাবে স্মৃতি ইশারা উৎসারিত সময় চেতনাকে ধারণ করে প্রাউস্ত গ্রামের বাড়ি, শৈশব, সাগরপাড়ে প্রথম দেখা তরুণী, জিলবার্তার সাথে ঘনিষ্ঠতা ও বসবাস ইত্যাকার নানা ফেলে আসা স্মৃতিমুখর ঘটনা পরম্পরায় আবর্তিত করেন তার উপন্যাসের জমিন, যা স্মৃতিকাতরতা ও সময়ের অদ্ভুত প্রবাহ নিয়ে হাহাকার করা এক বিপুল সম্ভার। সাহিত্যে স্মৃতির উপস্থিতি যেমন সাহিত্য সৃষ্টির পরিপূরক, তেমনি বিস্মতি, অতলান্ত যন্ত্রণার দুঃস্মৃতি সাহিত্য সৃজনের নিয়ামক হতে পারে।
এ ধরনেরই একটি উপন্যাস নৈরাজ্যের দেবতাখ্যাত কথাশিল্পী আলবেয়ার ক্যামুর ‘দ্য আউটসাইডার’ বা আগন্তুক, যার প্রথম লাইনই হলো, “মা মারা গেছেন গতকাল কিংবা আজকে, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না”। খুবই সাধারণ কথা, অথচ এর মাঝেই লুকিয়ে আছে স্মৃতি সত্তার অস্থির দোদুল্যমানতা। একইভাবে স্মৃতি শিল্পের রূপকার ফরাসি ঔপন্যাসিক জ্যঁ পাত্রিক মোদিয়ানোর কথাও আমরা প্রসঙ্গত বলতে পারি, যিনি স্মৃতি-বিস্মৃতির লুকোচুরিয় তুচ্ছ ঘটনাকেও অসাধারণ করে সৃজন করেন তার উপন্যাসের শরীর, যা অনেকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘আইসব্যাগ থিওরি’ জাত।
এ ধরনের লেখায় অনেক কিছু অব্যক্ত বা লুকায়িত থাকে, যা পাঠক নিজ জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাখ্যার ক্ষমতার মাধ্যমে বুঝে নেন। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত মোদিয়ানোর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস ‘মিসিং পারসন’ বা নিখোঁজ মানুষ’ এর কেন্দ্রে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ফ্রান্সে জার্মান দখলদারিত্বের অন্ধকার দিনগুলোতে স্মৃতি-ভ্রষ্ট এক লোকের কাহিনি যিনি নিজের নাম, পরিচয়, অতীত হারিয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে প্যারিসের পথে প্রান্তরে খুঁজে ফিরছেন - এসব কিছু।
হুটে নামের প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির এক মালিক লোকটির নাম দেয় ‘গাই রোঁলা’- যার স্মৃতিতে অতীত বলে কিছু নেই। উপন্যাসটির এক জায়গায় আছে, ‘আমি (গাই রোঁলা) কি সত্যি আমার জীবনকে খুঁজে ফিরছি? নাকি অন্য কারো জীবনকে, যার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে ঢুকে মিশে গেছি আমি?’ ‘মিসিং পারসন’ এ মোদিয়ানো এভাবে আপনাকে একটানা ঘোরাচ্ছেন প্যারিসের অলি-গলি-রাজপথে হাজারো মানুষের স্রোতে, কিন্তু আসলে আপনি ঘুরছেন সেই স্রোতের ভেতরের চোরাস্রোতে, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি বীভৎসতায় মৃত্যুভয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ- স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন নিজের ভেতর অথবা সত্যি সত্যিই বাস্তবে! যারা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অতীতের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে।
স্মৃতির নবায়ন মানে অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার পুনর্জাগরণ। স্মৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তি-পরিসরেই সবসময় সীমাবদ্ধ থাকে তা কিন্তু নয়। এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সঙ্গতকারণেই স্মৃতিকাতরতা নানাভাবে কাহিনী কেন্দ্রে এসে পড়ে। মূল কাঠামোর জন্য অনেক সময় অত্যাবশ্যক মনে না হলেও কাহিনির অনুসঙ্গ হিসেবেও পরিবেশ- পটভূমিকে পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব করে তোলার জন্য ‘স্মৃতিকাতরতা’ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বিষয়টি লক্ষ করা যায়, উপমহাদেশে ’৪৭-এর দেশভাগ এবং একাত্তরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনার ক্ষেত্রে।
এদুটি ঘটনা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থেকে আমাদের কথাসাহিত্যে গৌরবদীপ্ত সংযোজন ঘটিয়েছে। দেশভাগ ও দেশত্যাগ করা মানুষের ভাগ্য নিয়ে উপমহাদেশ জুড়ে নানা ভাষায় লেখা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়, যার বেশির ভাগই দেশপ্রেম, দেশভাগের স্মৃতি ও দেশভাগজনিত পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়াজাত। এ ধরনের উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’, আবুল ফজলের ‘রাঙা প্রভাত’, মাহমুদুল হকের ‘কালো বরফ’, হাসান আজিজুল হকের ‘আগুন পাখি’, আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’, সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’, সরদার জয়েন উদ্দীনের ‘অনেক সূর্যের আশা’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’সহ আরও অনেক গ্রন্থ।
দেশভাগ নিয়ে গল্পও কম লিখা হয়নি। এ ধরনের গল্পের মধ্যে সাদত হাসান মান্টোর ‘কালো সীমানা’, কৃষণ চন্দর এর ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নেড়ে’, সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’, আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘ছুরি’, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আমাদের কথাসাহিত্যে এক গৌরবদীপ্ত সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনের এমন এক অধ্যায়, যা বাঙালির জীবন- স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে রাবেয়া খাতুনের ‘ফেরারি সূর্য’, রিজিয়া রহমানের ‘রক্তের অক্ষরে’, শওকত ওসমানের ‘নেকড়ে অরণ্য’, সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, রশীদ হায়দারের ‘খাঁচায়’, আমজাদ হোসেনের ‘অবেলায় অসময়’, হুমায়ুন আহমেদের ‘জোছনা ও জননীর গল্প’, ইমদাদুল হক মিলনের ‘সাড়ে তিনহাত ভূমি’, মইনুল আহসান সাবেরের ‘কবেজ লেঠেল’ ইত্যাদি।
স্মৃতিকাতরতা সবচেয়ে বেশি ভর করে আত্মজৈবনিক সাহিত্যে, প্রধানত আত্মজীবনীতে। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন লিখিত আত্মজীবনী পাওয়া যায় না। তবে মধ্যযুগে কাহিনি কাব্যে ‘আত্মপরিচয়’ ধরনের আখ্যান দেখা যায়। (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)
চ-ীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম, পদ্মাবতী কাব্যে আলওল এ রকমের আত্মপরিচয় দিলেও তা আত্মজীবনী নয়। স্মৃতিকথায় ভর করে যে সব স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনী লেখা হয়েছে তৎমধ্যে রয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার’, বেগম রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবন স্মৃতি’ (১৯১২), সজনী কান্ত দাশের ‘আত্মস্মৃতি’, প্রমথ চৌধুরীর ‘আতœকথা’, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ফিরে ফিরে চাই’, জসীমউদদীনের ‘স্মৃতিপট (১৯৬৪), কাজী মোতাহার হোসেনের ’স্মতিকথা’, আবুল কালাম শামসুদ্দিনের ‘অতীত দিনের স্মৃতি’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘নীরবিন্দু’, আবদুস শাকুরের ‘কাঁটাতেও গোলাপ থাকে’, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর ‘নিন্দিত নন্দন’ হেনা দাশের ‘স্মৃতিময় দিনগুলো’ ইত্যাদি। এসব আত্মজীবনী লেখার মূল উৎস তাদের অতীত দিনের স্মৃতি, ফেলে আসা সময়ের প্রতি আচ্ছন্নতা; যা তারা প্রতিনিয়ত বয়ে চলতেন।
ভ্রমণ সাহিত্য মানেই স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে এর উপ¯ি‘তি লক্ষণীয়। সেই খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে গ্রিক ভুগোলবিদ চধঁংধহরধং লিখেছিলেন ভ্রমণ বিষয়ক স্মৃতিকথা ‘উবংপৎরঢ়ঃরড়হ ড়ভ এৎববপব’। মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪- ১৩৬৯), ভেনিসীয় পর্যটক নিক্কোলো, চীনা পর্যটক মা হুয়ান, পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোআঁ দ্য বারোসের কথা আমরা কে না জানি, যাদের এদেশ ভ্রমণের স্মতিতে আমরা খুঁজে পাই ইতিহাসের অনেক অনালোকিত অধ্যায়।
বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বড়ো ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪- ১৮৮৯) এর স্মৃতি নির্ভর ভ্রমণ কাহিনি ‘পালামৌ’। এটিকে বলা হয়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ভ্রমণ কাহিনি। এর পর অনেক ভ্রমণ গদ্য লেখা হয়েছে, যার অবলম্বন স্মৃতিকাতরতা।
এ ধরনের কিছু বই শরচ্চন্দ্র দাশ (১৮৪৯-১৯১৭) এর ‘তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত’, জলধর সেনের ‘প্রবাসচিত্র’ (১৮৯৯), বিমল মুখার্জির ‘দু চাকায় দুনিয়া (১৯৮৬), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ইউরোপ- যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১), শঙ্খ ঘোষের ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম’ (১৯৫৬), সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)।
এই যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ গদ্য- এ ধরনের বিভিন্ন সাহিত্য প্রকরণে স্মৃতি নির্ভর সৃজনের মহাসমারোহ, তা কিন্তু সম্ভব হয় স্মৃতির অন্তহীন পরিসরে কবি-সাহিত্যিকদের নিবিড় অবগাহনে। এখানে সব স্মৃতিই যে পরিশীলিত, তা কিন্তু নয়। স্মৃতি লোপের অভিঘাতে উৎকট গলিত অনুষঙ্গ কিংবা জটিলতর অনুষঙ্গও ভর করতে পারে। কারণ মানব জীবনে স্মৃতি যেমন সত্যি, বিস্মৃতিও তেমনই অনস্বীকার্য। আসলে স্মৃতির সূক্ষ প্রয়োগের উপরই নির্ভর করে সাহিত্য কতটুকু উদ্দীপক বা তিমিরাশ্রয়ী।
সাহিত্য শেষ পর্যন্ত একটা শিল্প। এর বিচরণ ভূমি বেশ বিস্তৃত ও বর্ণিল। বিচিত্র সব উপাদান, কৌশল, কারুকাজ, নানা অনুষঙ্গ সাহিত্য সৃজনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। স্মৃতিকাতরতা এসবের একটি। তবে বিষয়টি ব্যক্তি মানুষের মনোজগতে ক্রিয়াশীল বলে এটি সাহিত্য সৃজনে বেশ সক্রিয় থাকে। মানুষ নানাভাবে স্মৃতি কাতর হয়। প্রতœ নিদর্শন, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা, রোমাঞ্চকর মুহূর্ত, বিশেষ আড্ডা, আবেগময় সুর, উদ্দীপক সঙ্গীত, ঘটনা-দুর্ঘটনা- এসব নানাভাবে মানুষকে স্মৃতি কাতর করে তোলে।
স্মৃতি সুখ-দুঃখ-বেদনা- যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই তা সাহিত্য সৃজনের বীজতলা হিসেবে দিশা নির্দেশ করে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সাহিত্য কতটা নান্দনিক ও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করে স্মৃতিধর মানুষটি স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে পরিশীলিতভাবে সৃজন- মননে প্রয়োগ করে কিভাবে গ্রন্থিক রূপ দিচ্ছেন বা দিতে চাচ্ছেন,তার উপর। কবি জীবনানন্দের কথায়ঃ
‘স্মৃতিই মৃত্যুর মতো, ডাকিতেছে প্রতিধ্বণি গম্ভীর আহবানে/
ভোরের ভিকিরি তাহা সূর্যের দিকে চেয়ে বোঝে’।