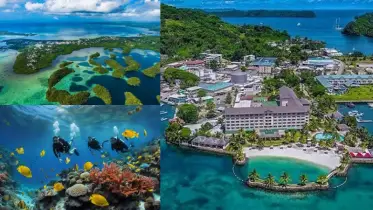ভাষা একমাত্র মানুষের আছে
ভাষা একমাত্র মানুষের আছে। অন্য কোন প্রাণীর ভাষা নেই। পাখি কথা বলতে পারে, অনেকটাই মানুষের মতো কিন্তু পাখির ভাষা মানুষের শিখিয়ে দেওয়া ভাষা। পোষা প্রাণী মানুষের কথা বুঝতে পারে সেভাবে তারা আচরণও করে কিন্তু তাকে ভাষা বলে না। কারণ তারা মানুষের মতো ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সর্বোপরি তাদের চিন্তা শক্তিও নেই। ভাষা হলো মানুষের বাগযন্ত্র থেকে উদ্ভূত উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি।
ভাষা হলো চিন্তাবহ। ভাষা সীমাবদ্ধ ভাব প্রকাশ নয়, অসংখ্য ভাব প্রকাশ করতে পারে। ভাষা বিবর্তনধর্মী, যুগে যুগে তার পরিবর্তন চলে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কবে থেকে কথা বলতে শিখলো মানুষ? এটা নিঃসন্দেহে জানা জরুরি। কিন্তু ভাষার উৎস নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে লেখালেখি হয়েছে। ভাষার পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রাচীন ভাষাগুলোর উৎসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে।
মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে আকার-ইঙ্গিতের নির্বাক অথবা প্রাক-ভাষা থেকে মৌখিক ভাষার জন্ম হয়। এর বেশি জানা নেই কারোই। বর্তমান মানব সভ্যতার কোথাও এখন সেই আদিম প্রাক ভাষার অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানীরা তাই বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের অনুমান ৮০ লাখ বছর আগে আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করত এপ-জাতীয় কিছু প্রাণী। এই এপ-জাতীয় প্রাণীগুলোর মধ্যে শিম্পাঞ্জি ও মানুষদের পূর্বপুরুষও ছিল।
এরা সম্ভবত ছিল বর্তমান গরিলাদের মতো। এরা মূলত বৃক্ষে বসবাস করত, মাটিতে চার পায়ে হাঁটত এবং বিশ-ত্রিশটার মতো ভিন্ন ডাকের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করত। আজ থেকে ২০ লাখ বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষ প্রাণীটি শিম্পাঞ্জিদের পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এই প্রাণীগুলোর ভাষা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ উন্নত; কিন্তু মানুষদের এই আদি পূর্বপুরুষদের ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারা গেছে।
আধুনিক মানুষের ভাষার উৎস নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় ধরেই তেমন গবেষণা হয়নি। কেবল অতি সম্প্রতি এসেই এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী, জিনবিজ্ঞানী, প্রাইমেটবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুজীববিজ্ঞানীদের আহরিত তথ্য কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী খতিয়ে দেখছেন।
কিন্তু আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কিরও আগে ভাষা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলন যে থিওরি দিয়েছেন তা খুবই সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত। মার্কস-এঙ্গেলসের সূত্র ধরে লেনিন ও স্ট্যালিনও ভাষা নিয়ে কথা বলেছেন যা কোনো ক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারে বলেছেন, পশুদের ভাষা নেই কারণ তাদের সমাজ নেই।
মানুষ একসঙ্গে বাস করছে না, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে না অথচ ভাষার জন্ম ও বিকাশ হচ্ছেÑ এটা অসম্ভব (মার্কস:১৯০৪১৬৬-৬৯)। শ্রমের উদ্ভব ও বিকাশ পরস্পরকে আরও কাছে টানল। কথা বলার প্রয়োজনে বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি বাগিন্দ্রিয় হিসাবে ব্যবহৃত হলো। মানববিবর্তনে অপরিহার্য প্রেরণা হিসাবে প্রথমে কাজ করেছে শ্রম তারপরে ভাষা। যদিও শ্রেণিগতভাবে ভাষার রূপ পরিচয় আলাদা।
আমরা বাংলা ভাষায় সাধু চলিত, মান ভাষা, প্রমিত ভাষা, বহুনামে ভাষাকে চিহ্নিত করলেও ভাষা যে মানুষের বিনিময় মাধ্যম এটা সর্বজন গ্রাহ্য। ‘১৮৫৭-৫৮ সালের অর্থনৈতিক পা-ুলিপিতে মার্কস বলেছিলেন ভাষাকে ছেড়ে কেউ কখনো আলাদা অবস্থান করতে পারে না।’ এছাড়াও মার্কস ডাস ক্যাপিটাল (পুঁজি) গ্রন্থেও নানা সূত্রে নানা প্রসঙ্গসূত্রে বৈজ্ঞানিক ভাষা চিন্তাকে ধারণ করেছেন।
যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তথা মার্কবাদী ভাষাতত্ত্ব। অন্যদিকে মহামতি লেনিন বলেছেন, ভাষা মানুষের চিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে গাঁথা। মানুষের চৈতন্যে বালবের প্রতিফলন তাৎপর্যম-িত হয়ে ধরা পড়ে মূলত ভাষারই মাধ্যমে।
মানুষের চিন্তাশক্তির প্রকাশ যেহেতু ভাষার মধ্য দিয়ে, তাই হয়তো ভাষা শব্দের উৎপত্তি। এমনকি ইতর প্রাণীও তার প্রয়োজন নানা প্রকার ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশ করে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, এসব ধ্বনি ভাষা নয়। ইতর প্রাণীর সঙ্গে তারা মানুষের পার্থক্য করেছেন এভাবেই। তবে এক সময় মানুষ ও পশুর ভাষার ভেতরে যে প্রভেদ ছিল না তা সত্য।
মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয়েছে মানসিক উৎকর্ষের ফলে। চিন্তাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশ রূপ পেতে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করে যে, ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীতে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ যে ইশারা-ইঙ্গিতের কিংবা সংকেতের সাহায্যে কথা বলত তার বহু নিদর্শন রয়েছে। ও সব ইঙ্গিতময়ী ভাষার পরবর্তী অবস্থাই কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবান ভাষার সৃষ্টি করেছিল।
আধুনিক ভাষাতত্ত্বে ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনি, রূপ ও পদের সংগঠন বিশ্লেষণ করা হয়। এখন ভাষা বলতে প্রধানত মুখের ভাষাকেই বোঝায়। কিন্তু ভাষার এই পরিণত অবস্থায় আসতে তিনটি স্তর পার হয়ে আসতে হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন। এই তিনটি স্তর হচ্ছে- ১. সংকেত ও ইঙ্গিত, ২. কথ্য ভাষা, ৩. লেখ্য ভাষা। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, যদি ভাষা বিবর্তন একই পথে আসে তাহলে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে ভাষার পার্থক্য কেন?
অর্থাৎ ইতিহাসে ভিন্ন ‘ভাষা সম্প্রদায়ের’ উল্লেখ পাওয়া গেলেও কেন এ ঘটনা ঘটল তার কোন ইঙ্গিত আমাদের হাতে আসেনি। তবে যতদূর চিন্তার ভেতরে টানা যায় তা হচ্ছে আলাদা ভাষা অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আলাদা ‘ভাষা সম্প্রদায়’ গড়ে উঠেছে ভূ-প্রকৃতিগত কারণে। সাধারণত যেটা বিবেচ্য তা হচ্ছে- শ্রমজীবী মানুষের ভাষাই সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা।
শ্রমজীবীদের সঙ্গে শ্রমজীবীদের সম্পর্কের কারণে তাদের ভাষাটা ক্রমশ জনগণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভদ্রলোক (বিত্তশালী) সম্প্রদায়ের ভাষা ভদ্র হলে মূল টেকচারটা গড়ে ওঠে শ্রমজীবীদের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আমরা একটা প্রভেদ সহসাই দেখতে পারি। শ্রমজীবীরাই মূল ভাষার নিয়ন্ত্রক। কিন্তু শিক্ষার সংকট তাদের ভাষাকে ভিন্ন রকমের করতে বাধ্য করেছে।
সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সারাদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা এক কিন্তু শ্রমজীবীদের ভাষা এক নয়। শিক্ষিত লোকেরা চিঠি লেখে পঠিত বইয়ের অনুসারে পাওয়া শিক্ষা থেকে আর শ্রমজীবী ভাষাকে গঠন করে ভাব আদান-প্রদানের জন্য। শ্রমজীবী মানুষেরা যে ভাষার চর্চা করে তা ছড়ায় না বলেই আঞ্চলিক ভাষার ভিন্নতা দেখা যায়। তবে এই ভিন্নতার কারণ একদম ভৌগোলিক।
ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ নদীমাতৃক হলেও বিরান সমতলভূমি, পাহাড় ও সাগরসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপাচার এখানে বিদ্যমান। ভাষার ’পরে এর প্রভার পড়ে। ফলে একটি অঞ্চলব্যাপী হলেও সুরে, বাচনে এর ব্যাপক প্রভার লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা হয়-প্রাথমিকভাবে জমিদার পরবর্তী সময় সরকারি কর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আত্মক্ষার জন্য শ্রমজীবী হতদরিদ্র মানুষেরা এসব ভাষা তৈরি করেছিল।
ঠারের সবচে’ লক্ষণীয় দিক যেটা, এর আলাদা কোনো বর্ণমালা নেই। নাগার্সিরা সম্প্রদায় মুসলমান কিন্তু অধিকাংশের নাম হিন্দুয়ানি। তাদের এমন নাম কেন জিজ্ঞেস করলে নাগার্সি সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধ গোপালগঞ্জের মুকুন্দ নাগার্সি বলেছে ভিন্ন কথা। তাদের যুক্তি হচ্ছে- বাদ্য বাজানোর অনুষ্ঠান তো হিন্দুদেরই। হিন্দুগোষ্ঠী পরিবারেরই কাজ করতে হতো- এ কারণে নামও তার দিয়েছে হিন্দুয়ানি নাম।
এতে হিন্দুরাও খুশি থাকত। কিন্তু এখন সেখানেও শিক্ষার বাতাস লেগেছে। ফলে চিকিৎসা করতে গেলে ‘ঠার’ তাদের ব্যবহার করতেই হয়। মুচি সম্প্রদায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় ঐ ভাষায় কথা বলে না। কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্রেই তারা এই ভাষার চর্চা করে থাকে।
প্রশ্ন হলো মুচিদের ভাষা সংকেতপূর্ণ কেন? তারা তো সমাজের অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে মিলে মিশেই জীবন যাপন করে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষা অন্যদের থেকে আলাদা কেন? মুচিদের পেশা ও জীবন অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা। তাই তারা নিজেদের কাজ ও পেশাকে অন্যদের থেকে আড়াল করার জন্য আঞ্চলিক উপভাষাকে ব্যবহার করে না। প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের তুলনা করা যায়।
চর্যাপদের কবিরা যে উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে মুচিরাও তাদের ভাষাকে প্রচলিত সমাজভাষার থেকে পৃথক করে নিয়েছে। তাদের এলাকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে তাঁদের বৃত্তি থেকে স্পষ্টত পৃথক। এই সাংকেতিক ভাষার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের বৃত্তিগত কাজকর্ম বা তার সঙ্গে জড়িত আচার-আচরণকে সার্থকভাবে গোপন রাখতে পারেন; বা তাকে প্রকাশ করতে পারেন ছদ্মরূপে। মুচিদের এই উপভাষার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার চর্যাগীতির সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যাবচনের তুলনা করা যেতে পারে।
অর্থাৎ একটা বিষয়ে আমরা স্পষ্ট যে, সমাজের নিঃগৃহীত ও নিম্নবর্গের জনসমাজ তাদের প্রয়োজনেই পেশার ভাষা বা ঠার-এর ব্যবহার শুরু করে ছিল। যারা করেছিল তারা কারা, নিরক্ষর বা অশিক্ষিত কিনা আমরা জানি না। তবে স্বশিক্ষিত যে, একথা বলতেই হবে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রয়োজনে ঠার ব্যবহার শুরু করলেও এর সময়কাল জানা সম্ভর হয়নি। তবে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত ‘চর্যাগীতি কোষ’কে সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়।
যেটা প্রকৃতপক্ষে সাংকেতিক ভাষার নামান্তর মাত্র। জানা যায়, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের শ্যেনদৃষ্টি থেকে ধর্মীয় আচার-আচরণকে রক্ষা করা জন্য বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ হেঁয়ালি ভাষায় চর্যাগীতি রচনা করেন। কোনো সাংকেতিক ভাষাই সহজে অনুধাবন করা যায় না। এ হলো রহস্যাবৃত ভাষা। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেছেন-‘গোগনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য বা অসৎ উদ্দেশ্য দলের লোকের কাছে প্রকৃত এবং অন্যের অবোধ্য অথচ প্রয়োজনীয় সংলাপ স্বাভাবিকভাবে চালাইয়া যাইবার জন্য বিশেষ শব্দ (এক বা একাধিক ভাষা হতে সংগৃহীত) ব্যবহার করে।
বাগব্যবহারকে অগার্থ ভাষা অথবা সংকেত ভাষা (ঈড়ফব খধহমঁধমব) বলা হয়। সন্ন্যাস বিদ্রোহের বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলত। এই সাংকেতিক ভাষাকে বলে ‘রামসিয়ানা’। দেশের অপরাধ জগতেও ঠারের প্রচলন রয়েছে। সেখানে ঠারের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান হতে ব্যস্ত। পেশা ছেড়ে এখন আর কেউ ঠার বলে না। বললে যদি ছোট হয়ে যায় এই ভয়ে।
শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে নয়, শ্রেণি বিভাজনের কারণে সমাজে শোষণ ও দলন প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষেরা বহু আগে থেকে। ঠার হচ্ছে ভাষা আগ্রাসনের দলিল। অর্থাৎ সামন্ত জমিদাররা পাকিস্তানের চেয়ে কম ছিল না। অবদমনের ক্রোধের ফসল ভঙ্গ হলেও ফসল চুরি হয়ে গেছে। কারণ ঠারের সমাজ বদল হয়নি। বদলাচ্ছে স্টাইল। অথচ অবহেলা-অযতেœ স্বশিক্ষিত মানুষের আত্মরক্ষায় তৈরি এ ভাষাটি তাই হারিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে।
ভাষাটিকে তুলে আনার জন্যই কাজ করা দরকার ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে। নতুবা সমৃদ্ধ এবং রীতিমতো তাজ্জব বনে যাওয়ার মতো এই সৃষ্টি হারিয়ে যাবে অবলীলায় চোখের সামনে। যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, গোমতী, ধলেশ্বরী, মধুমতী, জারিসারি আরও কত কি!
ব্রাত্য জনের এই ভাষাই শুধু না, দেশে প্রচলিত সব ধরনের ভাষাই সংগ্রহ করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনে আলাদা ইনস্টিটিটিউট গঠন করতে হবে। নতুবা এসব ভাষা হারিয়ে যাবে একদিন। ভদ্দরলোকে ভাষা দিয়ে ভাষাকে রক্ষা করা যায় না, ভাষা আন্দোলন আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছে।