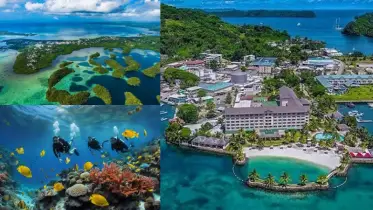একুশের চেতনা
বিগত শতকের ’৪৮ সালে পাকিস্তানের শাসক প্রধান মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ‘রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু’। তার এই ঘোষণায় তখনই বিশ^বিদ্যালয়ের কতিপয় তরুণ ছাত্র জিন্নার মুখের ওপর প্রতিবাদ করে। এতে জিন্না খুবই বিরক্ত হন, কারণ তার অহঙ্কার ছিল সে পাকিস্তানের ¯্রষ্টা এবং পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা। কেউ তার মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারে, তা ছিল তার আত্মগরিমা বিরুদ্ধে।
কারণ তিনি মনে করতেন তিনিই ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব তৈরি করেছেন। পাকিস্তানিরা ইতোমধ্যে তাঁকে রাষ্ট্র পিতায় আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু সেই যে প্রথম ‘না,’ তা ছিল পরবর্তী সময়ের নতুন চেতনা-বীজের উদয়কাল। সেই অহমিকা জিনের আঁছড়ের মতো আজও সকল নেতা/নেত্রীর মধ্যে বিদ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়। যখনই কেউ ক্ষমতা পেয়েছে সে তার অহমিকায় জনগণের আকাক্সক্ষার বিরুদ্ধতায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
[স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা পেয়ে মনে করতে থাকেন তিনিই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির একক নেতা এবং তিনিই এর অস্তিত্ব। তার এই অহমিকা সময় থেকে সময়ে আরও তীব্র হয়ে উঠলে তিনিও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল কতিপয় বদমতলবী সাঙ্গ-পাঙ্গ দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েন। জনগণ তাকে শ্রদ্ধার অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলে।]
সেদিনের প্রতিবাদের ক্রিয়ায় জনগণের মধ্যে শাসকের চিরকালীন যে দ্বন্দ্ব তা ঘনিয়ে ওঠে এবং মোহভঙ্গ শুরু হয়। ধীরে ধীরে পাকিস্তানি শাসকদের আধিপত্যবাদী মনেবৃত্তির কুৎসিত রূপটি নানা আকারে উন্মোচিত হতে থাকে সমাজ-চেতনায়।
সমাজে প্রতিনিয়ত শ্রেণিতে শ্রেণিতে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান নানা সংঘর্ষের ফলে তার মধ্য থেকে কোনো কোনো দ্বন্দ্ব বিশেষে রূপ পায়। জনশক্তি তখন তাকেই লক্ষ নির্ধারণ করে বিষ্ফোরণ উণ¥ুখ হয়ে উঠলে নেতা তৈরি হয় এবং লড়াইটা সাধারণই পরিণতির দিকে উপনীত করে।
॥ দুই ॥
বাঙালি সম্প্রদায় উপর্যুক্ত ঘটনায় অনেকখানি আলোড়িত, শাসক এবং শাসিতের দ্বন্দ্ব তখনো উতলিয়ে পড়ার অবস্থানে উপনীত না হওয়ায় অন্যদিকে রাজনৈতিক দিশার অভাব তখনই এই প্রতিবাদ কল্পনার বৃত্তরেখা ছুঁয়ে দেখার স্বপ্নে রূপ পায়নি। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায় এই প্রতিবাদেই স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন জাতির পরবর্তী আকাক্সক্ষার অদিতি উৎসব হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের ‘না’ থেকে বাঙালি মনন নতুন চিন্তা-সজ্জার রূপরেখাটিকে অনুভবে উপস্থিত করতে থাকে।
ধীরে ধীরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অভিপ্রায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আঁচ বাঙালি জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। একই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নানাভাবে বাঙালি জীবন-আচারে রাষ্ট্রের অপর অংশের সংখ্যলঘিষ্ঠ নাগরিকের ভাষা-সংস্কৃতি, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপরে চাপিয়ে দিতে তারা নানা ফন্দি আঁটে। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধের তালিকায় ফেলে। তারা ঠিকই বুঝে ছিল রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি বাঙালি চেতনায় প্রথিত ঐতিহ্য। [বাঙালিরা তখনো জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি]
বাঙালি সংস্কৃতি রীতি-নীতি সুদীর্ঘ সময় ধরে এই ভূখ-ে মানুষের মন ও মননে গেঁথে যাওয়া অপ্রতিরোধ্য সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও উপেক্ষিত ছিলেন। নানা অযুহাত তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ঘৃণ্য চেষ্টাও চলমান ছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টায়ও পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি সফলতা পায়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ/নজরুল ছিলেন বাঙালি সমাজের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
তিন.
বাস্তবত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোগত অবস্থান তৈরি হয়েছিল উপনিবেশিক শক্তির নানা ছক ও কুৎসিত চক্রান্তের ফলাফলে। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ এই ভূখ- পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল মূলত ধর্মের ভিত্তিতেÑ যা প্রায় দৈবের মতো। শুরু থেকে দুই অংশের মানুষের মধ্যে শারীরিক বৈষম্য, পরিবেশগত ও ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষাগত মানসিক দূরত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে ছিল উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা।
শাসকগোষ্ঠীর ভাষাও ছিল পারস্পরিক নৈকট্যের বিপরীত। আরও পরের সময়ে শাসন ও শাসক চরিত্রের রূপটি স্পষ্ট হতে থাকে এবং নানা রাজনৈতিক ক্রিয়ার উত্তাপ বাড়তে থাকে। দেশের এই অংশের নাগরিক সমাজ পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের তিত-তিক্ততায় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনতায় ফিরতে শুরু করে। ’৪৮ থেকে ৫২’র ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে নানা রাজনৈতিক ওলট-পালটে ছাত্র-সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিক্ষোভে নামে এবং তারা মিছিল নিয়ে তৎকালের প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশ গুলি চালায়।
হত্যা করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সালাম, বরকত, জব্বারসহ কয়েকজন ছাত্র ও জনতাকে। [পাকিস্তানিরা এই হত্যাকা-ের মধ্য দিয়ে নিজেরাই নিজদের ঘরে আগুন লাগবার উপাত্ত তৈরি করে] এই সময়ে পাকিস্তানিরা নানাভাবে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে তৎপরতা চালায়। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাঙালিদের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে এবং বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে রূপান্তরিত করার পাঁয়তারাও করে। বাঙালিরা তা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করে।
’৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানিদের চক্রান্তের বিরুদ্ধের এই বিক্ষোভে ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকৃত বাঙালি মানসকে ভবিষ্যৎ অনুধাবনের জাগৃতি এনে দেয়। এই আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যে দূরীকরণ, বাঙালি জীবনে পাকিস্তানি শাসকবর্গের আধিপত্যবাদ ও ন্যায়হীন আচরণের বিরুদ্ধে। আসলে ২১-এর ভ্রুণে যেমন বহুত্ববাদের অস্তিত্ব ছিল, ঠিক তেমনি তার বিকাশও হতে ছিল জনচেতনার বহুমুখী স্বপ্নে। যা এক সময়ে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষায় রূপ লাভ করে।
চার.
২১ কেবল মাত্র ভাষা আন্দোলন নয়, [সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনও কেবল মাত্র কোটা সংস্কার নয়, বরং তার গর্ভে বিদ্যমান স্বৈরাচারের পতনেরও আন্দোলন] যদিও সেকালের শাসন ব্যবস্থায় চলমান রাজনীতি খানিকটা বিষয়কে সামনে রেখে, খানিকটা ধামাচাপা দিয়ে, একটা আপোসি কাঠামোতে রাজনীতির রণকৌশলে মগ্ন থাকে। কিন্তু যে সাহস সামগ্রিকভাবে প্রজ্বালিত হয়েছিল তা দাবানলে পরিণত হতে আরও কয়েক বছর জাতিকে অপেক্ষা করে আবারও রক্ত দিতে প্রস্তুত হতে হয়েছে।
ভাববার কোনো কারণ নেই; এই অর্জনে কেউ খুবই দ্বিধাহীন নেতৃত্ব দিয়েছিল, এমনকি তৎকালীন বাম রাজনীতিও বিভ্রান্তিতে পড়ে। নানা তত্ত্বের অবতারণা করে বহু কর্মীর জীবন হানির কারণ হয়। তারাও খানিকটা বিদ্রোহী খানিকটা আপোসের ভূমিকায় রাজনীতিকে শ্রেয় করেছে।
বলা অসংগত নয়, নানা ভাবে পাকিস্তানিদের সৃষ্ট বৈষম্য, অবহেলা, ইত্যাদি জনগণমনে যে রোষ তৈরি করেছিল, তার ফলে দেশের এই অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও জনচাহিদার সংগে যুক্ত হয়ে আপোস/বিদ্রোহের কর্মপরিকল্পনা সাজাতে হয়েছিল। পিছুটান নিয়েই এইসব নেতারা যে রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেছিল, তার চেয়েও অগ্রগামী ছাত্র জনতা স্বাধীনতার আকাক্সক্ষাকে আরও বেশি প্রিয় করে তুলেছিল।
সংগত কারণে কেউ এই লড়াইয়ের অসংবাদিত নেতা নয়, বরং বলা যায় জন-আকাক্সক্ষার বিকাশমান ধারায় জনগণের আশুচাহিদাকে সামনে নিয়ে যে বা যিনি রাজনীতি নির্ধারণ করতে পেরেছে জনগণ তাকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে।
পাঁচ.
লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে, পাকিস্তানিদের বর্বর আক্রমণে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল দেশ। রাজনৈতিক শক্তি কোনো পশ্চাৎভূমি তৈরি প্রস্তুত না করায় কিংবা ভৌগোলিক অবস্থানে সে সুযোগ তেমন একটা না থাকায় আক্রান্ত জনতার একটা বড় অংশÑÑঅধিকাংশ নেতা ভারতে পালিয়ে যায়। কেবল মাত্র জামাতি ইসলামী ও কয়েকটা ইসলাম পন্থিদল [যারা পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছিল] লোকজন ছাড়া চেনা বাম এবং ডান সবাই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।
ভারত তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আকাক্সক্ষার বাস্তবায়নে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শেষতক নানা প্রশ্ন নিয়ে আমরা স্বাধীনতার নিয়মে একটা ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমিত ভূখ- লাভ করেছি। বেদনার বিষয় হলো এই দেশের এই অংশ তিন বার স্বাধীনতা নামে কারো না কারো অধীনতায়ই আটকে গেছে। প্রকৃত স্বাধীনতা রয়ে গেছে বহু দূরে।
ছয়.
একুশের সেই চেতনা যা ছড়িয়ে গিয়েছিল একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্নে তার আড়ালে পরবর্তীতে মিথ্যা বয়ান¯্রােতে জন কল্যাণ বিমুখ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। [যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্লোগান।] লুটপাট, কুশাসন, দুর্বিত্যায়ন, খুন, গুম নিয়ে বৈষম্য-বিদ্বেষের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কেবল মাত্র মিথ্যা এবং অশ্লীল কথাবার্তা এবং ‘চেতনা চেতনা’ বুলিদে কর্তৃত্ববাদী নেতার/নেতাদের অহমিকায় সবকিছুকে দলীয়করণ ও দখলের মনোবৃত্তিতে একুশের চেতনাকে লোপাট করেছে।
আর অন্যদিকে ‘একুশ চেতনার’ সমস্ত আত্মিক শক্তির হাত পা কেটে শহীদ মিনারকে উপলক্ষ করে সামগ্রিক উৎসব/পার্বণে পরিণত/প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পুস্তক বাণিজ্য, পুরস্কার বাণিজ্য তথাকথিত কবিসাহিত্যিক দের চরিত্রকে স্খলিত করার উপায়কে প্রবল করেছে। আজকে লড়াইটা সেই একুশের চেতনা উদ্ধারে শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা নিতে হবে ÑÑসৃষ্টির মাধ্যমে।
জনগণের চেতনা উদ্ধারে নিবেদিত করতে হবে ‘কাব্য-শিল্প-আনন্দ’। আজ সংস্কৃতির আন্দোলন জোরালো না হলে মন ও মানসে দ্বিধা সংশয় সন্দেহের বিভেদ কাটবে না। সমাজ কলুসিত করে রাজনীতিবিদরা, পরিচ্ছন্ন করে স্বাধীন মনোবৃত্তির বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, শিল্পী-কবি-সাহিত্যকরা।