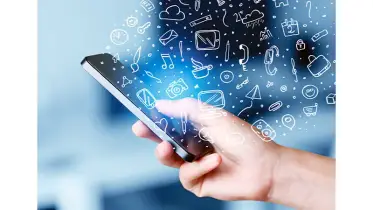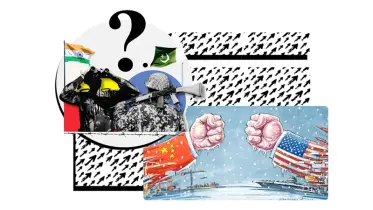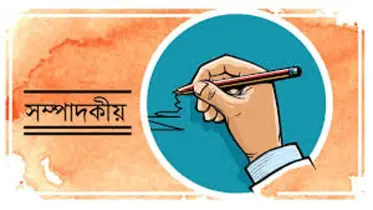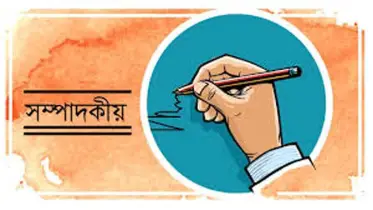শ্রেণি বিভক্ত সমাজে মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন যেন সমাজ সংস্কারের চিরায়ত বিধি। বিত্ত-নির্বিত্তের ব্যবধানে প্রতিদিনের যাপিত জীবনের ক্ষতবিক্ষত আঁচড় তাও সহনীয় অবস্থায় না থাকা কাঠামোর অভ্যন্তরে গেড়ে বসা এক করুণ আখ্যান।
বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানী কার্লমার্কস তার কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে দৃঢ়তার সঙ্গে এমন কঠিন তত্ত্বকে রূপ দিলেন। বইটি শুরু করলেন এই বলে ‘মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।’ সেখানে আদিম সাম্যবাদী সমাজকে বাদ দিলেন।
দাস সভ্যতা, সামন্ত সমাজ, ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা যা সর্বশেষে রূপ নেবে এক সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে। ঊনিবংশ শতাব্দীর এই সমাজ দার্শনিক চিন্তাবিদ সমাজ কাঠামোর রূপরেখা নির্দেশ করতে গিয়ে যে তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন তা আজও স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত।
সেখানে উৎপাদন শক্তি আর সম্পর্কের সমন্বয়ে তৈরি হয় গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা। অর্থনীতিই কোনো সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি। যার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় সে সমাজের রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরিবার এবং সার্বিক জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ।
তাই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ফারাক সেখানেই জিইয়ে থাকে বিত্ত আহরণ আর উৎপাদকের সঙ্গে শ্রমের ক্রমবিচ্ছিন্নতা। যার আছে আর যে শ্রম বিনিয়োগ করে। তেমন তাত্ত্বিক সত্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, প্রতিফলিত হওয়া মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব, কলহ যুগ-যুগান্তরের এক অসহনীয় যন্ত্রদায়ক পরিবেশ।
আর আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসও তেমন বিভাজনের নিগড়ে আটকানো বিত্ত আর নির্বিত্তের চিরায়ত সংগ্রাম বিপ্লবের যৌক্তিক পরিমণ্ডল। বলা হচ্ছে শ্রমিক আর মালিকের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব আর শোষণ প্রক্রিয়ায় প্রভু সম্পদের পাহাড় তৈরি করে।
আর নাকি শ্রমিক তার মহামূল্য শ্রম ছাড়া সব কিছু হারিয়ে বসে। কার্লমার্কস সেখানে আরও সুতীক্ষè বিভাজন দেখান। দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করেন শ্রমিক উৎপাদনে যে শ্রম বিনিয়োগ করে সেটা শুধু শ্রম নয় অতি আবশ্যিক শ্রমিকের শ্রম শক্তির নানামাত্রিক শোষণ-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত। আবশ্যিক শ্রম আর উদ্বৃত্ত শ্রম।
প্রয়োজনীয় শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক তার মজুরি পায় আর উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে মালিকের উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ধারণ তৈরি করে। সেখানে শ্রম শোষণ আর বঞ্চনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উঠে আসে কিভাবে পুঁজিপতি তার ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে আর নিঃস্ব শ্রমিক অতি আবশ্যিক শ্রম ছাড়া সব কিছু বিসর্জন দেয়।
সেখানে কারখানার শ্রমিকদের আরও করুণ দুর্দশা। শ্রমিকদের শ্রম ঘণ্টার কোনো হিসাব-নিকাশ না থাকাও বঞ্চিতদের চরম দুর্দশা। ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা শ্রম বিনিয়োগের পরিণামে হাতে যা আসত তা নগণ্যই শুধু নয়, মানবেতর জীবনযাপনকে মেনে নিয়ে অসহায় অবস্থায় টিকে থাকাও ছিল চরম এক দাবানল।
ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কোনো এক সময় অধিকার সচেতন হয়ে সংঘ হওয়াও ছিল সময়ের দাবি যা ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রম ঘণ্টা কমানো ন্যায্য মজুরি প্রদান আর মানবিক জীবনযাত্রায় সহনীয় পরিবেশ তৈরির জন্য জোর আন্দোলনে রাস্তায় নেমে আসে।
১২ ঘণ্টা থেকে শ্রম সময় কমিয়ে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করার দাবিতে উত্তাল আন্দোলনে মালিক পক্ষকে জানান দিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। দাবি পূরণের দিন ক্ষণও নির্ধারণ করে দেয় উত্তাল শ্রমিকরা। ১ মে শ্রমিক কিংবা মে দিবস হিসাবে ঘোষণার দাবি আসে সংঘবদ্ধ সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে।
১৮৮৬ সালের ৪ মে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে জোটবদ্ধভাবে একত্রিত হয় অসংখ্য শ্রমিক, আন্দোলনরত শ্রমিকদের চারপাশে ছিল সরকারি পুলিশ বাহিনী। সেখানেই সংঘর্ষ যা ঘটার তা যেন নিমিষেই হয়ে গেল। কোনো এক সময় শ্রমিকদের সভা থেকে বোমা বিস্ফোরিত হয় কর্তব্যরত পুলিশের ওপর।
ঘটনাস্থলেই মারা যান এক পুলিশ কর্মকর্তা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। পাল্টা আক্রমণেও শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে এগিয়ে আসে। পুলিশের গুলিবর্ষণে তাৎক্ষণিকভাবে ১২ জন শ্রমিক নিহত হয় বলে শ্রমিকদের দাবি।
এদিকে পুলিশ হত্যার দায়েও আটক হয় কয়েক নেতৃস্থানীয় শ্রমিক। শুধু তাই নয় বিচার প্রক্রিয়ায় ফাঁসিকাষ্টে ঝুলানো হয় আটক ছয় নেতাকে। অভিযুক্ত আর আটক করা বন্দির একজন আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে জানা যায়। অন্য জনের ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৭৮৯ সালে হয়ে যাওয়া ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্যাপন করা হয় ১৮৮৯ সালে।
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এই নজরকাড়া সম্মেলনে শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাপরম্পরা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নিয়ে আসা হয়। সারা বিশ্ব যখন ক্ষুব্ধ, প্রতিবাদে মুখর তেমন যুগ সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী শ্রমিকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা যেন ইতিহাসের দায়বদ্ধতা।
তার আগে স্পষ্ট হয় শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শ্রমজীবীর সিংহভাগেই নির্দোষ ছিলেন বলে তথ্য উপাত্তে উঠে আসে। যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম সহজেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কাল আর সময়ের আবর্তনে কত বিপ্লব যুগের দাবি হারিয়ে অদৃশ্য বাতাবরণে চলে যায় তাও ঐতিহাসিক নির্মমতা।
১৯০৪ সালে নেদারল্যান্ডসে সমাজতন্ত্রীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সামনে এসে যায় শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, মজুরি বৈষম্যের সুষম ব্যবস্থাপনায়। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠারও জোর আবেদন জানানো হয় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আহ্বানে।
এমন যুগান্তকারী আবেদনে সাড়া দিয়ে বিশ্বের প্রায় সিংহভাগ শ্রমিক সংগঠন এক পতাকার তলে সমান দাবি-দাওয়ায় একতাবদ্ধ হয়। সেখানে সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় ১ মেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার।
শুধু তাই নয়, ১ মে সরকারি ছুটির বিষয়টি নিয়ম মাফিক করার প্রত্যয় আসে আন্দোলনরত শ্রমিকের পক্ষ থেকে। শুধু তাই নয়, ১ মে কোনো শ্রমিক কারখানায় কাজ না করার প্রত্যয়ে দৃঢ় অবস্থান নেওয়াও চলমান আন্দোলনের অনন্য সফলতা। এরপর থেকেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটির তৎপর্যে কল- কারখানাসহ সমস্ত দাপ্তরিক কর্মযোগ বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত আসে।
আমাদের ক্ষুদ্র বাংলাদেশও দিবসটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করে আসছে। বাংলাদেশও উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় কল-কারখানার মালিক আর শ্রমিকদের কর্মযোগে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিভেদ-বিভাজনও সামনে আসতে দেরি লাগছে না।
২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সফল পরিণতিতে যে নতুন বাংলাদেশ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলো সেখানেও নানামাত্রিক বিভাজনকে বিলুপ্তির আবেদনে সাড়া জাগিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হতেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তাই বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশে এবার প্রথম পালিত হবে মে দিবসের মতো বিশ্বব্যাপী এক সর্বজনীন ব্যবস্থাপনার নব অঙ্গীকার।
বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মে দিবসের গুরুত্ব সর্বাধিক। বৈষম্য নিরোধক নীতিনির্ধারণ আর সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার হবে আন্তর্জাতিক মে দিবস। ’২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে যেভাবে বিলুপ্ত হয়েছে নানামাত্রিক অপসংস্কার আর অপকর্ম। এই মে দিবসও তেমন প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।
কুতুবে রব্বানী