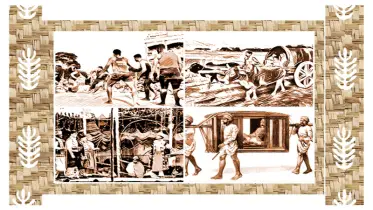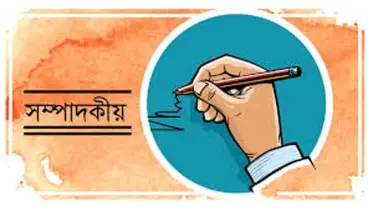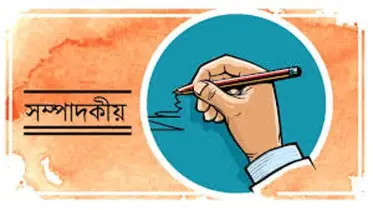বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বৈশ্বিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছে, তা মূলত একক বা ইউনিপোলার ব্যবস্থার ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থার ফলে বৈশ্বিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবে সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিবর্তন এসেছে। উদীয়মান শক্তিগুলোর উত্থান এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংকটের মুখে মাল্টিপুলারিজম বা বহুধ্রুবীয় বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে উপলব্ধি হচ্ছে। মাল্টিপুলারিজম এমন একটি ধারণা, যেখানে ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টিত থাকে। একক রাষ্ট্র বা জোট নয়, বরং একাধিক প্রভাবশালী রাষ্ট্র পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রেখে বিশ্ব পরিচালনায় ভূমিকা রাখে। এই কাঠামোতে প্রতিটি শক্তি অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য আনে। এ ব্যবস্থায় কোনো একটি দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়, যা বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও অভিন্ন উন্নয়নের জন্য সহায়ক।
একক আধিপত্যের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আত্মকেন্দ্রিক বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য যে কোনো একক শক্তি নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়, তা বহুক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তানে দীর্ঘ সামরিক উপস্থিতি, মার্কিন মদদে ইসরায়েলের ফিলিস্তিনের উপর অমানবিক আগ্রাসন চালানো, লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পরিবেশ বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এসবের ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশ্বাসহীনতা তৈরি হয়, যা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে।
বহুপাক্ষিকতা বা মাল্টিপুলারিজম এই সংকট থেকে মুক্তির একটি কার্যকর পথ। এই ব্যবস্থায় চীন, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, ব্রাজিলসহ আরও অনেক দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উঠে আসছে। আঞ্চলিক জোট যেমনÑ ইজওঈঝ, ঝঈঙ কিংবা অঝঊঅঘ এর মতো জোটসমূহও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে একটি নতুন শক্তির ভারসাম্য গড়ে উঠছে, যা একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং নতুন ধরনের সংলাপ, সহযোগিতা ও কূটনীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।
মাল্টিপুলারিজম কেবল ক্ষমতার বণ্টনের দিকেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরে যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি, মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কাঠামোর সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একক আধিপত্য যেখানে বৈচিত্র্যকে সংকুচিত করে, মাল্টিপুলারিজম সেখানে তা উদযাপন করে। এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখানে ছোট ও মাঝারি শক্তিসমূহও তাদের অবস্থান ও মতামত তুলে ধরার সুযোগ পায়।
তবে মাল্টিপুলারিজম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জও কম নয়। একাধিক শক্তির মধ্যে মতপার্থক্য, পারস্পরিক সন্দেহ ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপÑ চীন ও ভারতের সীমান্ত বিরোধ, রাশিয়া-ন্যাটোর দ্বন্দ্ব, মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি-ইরান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বহুধ্রুবীয় ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সংলাপ ও কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যও মাল্টিপুলারিজম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একক আধিপত্যের ছায়া থেকে মুক্ত হয়ে যদি বিশ্ব একটি ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি কাঠামোতে প্রবেশ করে। তবে ছোট দেশগুলো নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবে। মাল্টিপুলার বিশ্ব ব্যবস্থায় এই দেশগুলোকে আর বড় শক্তির ছায়ায় থাকতে হবে না। বরং তারা বিভিন্ন জোট ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিজেদের কূটনৈতিক শক্তি জোরদার করতে পারবে। সর্বোপরি, মাল্টিপুলারিজম একটি ন্যায্য, সুষম ও মানবিক বিশ্বব্যবস্থার সূচনা করতে পারে। যেখানে একক আধিপত্যের পরিবর্তে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্বের সব দেশের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে। একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিরাপত্তা সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ, যা কেবলমাত্র একটি বহুধ্রুবীয় বিশ্বব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই সময় এসেছে একক আধিপত্যের পরিবর্তে মাল্টিপুলারিজমকে বাস্তবায়ন ও উৎসাহিত করার, যাতে করে একটি স্থিতিশীল, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলা যায়।
লেখক : শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল