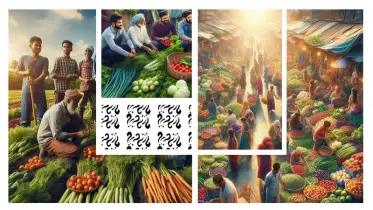বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের প্রধান প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে পর্যালোচনার আগে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা এটিকে এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। এই প্রবৃদ্ধি যা ২০১৩ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে গড়ে ৬.৫ এবং গত দশ বছরে ৭ শতাংশের একটি স্থিতিশীল জিডিপি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণিত, যা একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির সম্ভাবনা ও বিকাশের চিত্র উপস্থাপন করে। তবে এই অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম মাত্রার সামগ্রিক বিনিয়োগ, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী। যদিও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র নির্দেশ করতে পারে, এফডিআই প্রবাহের বাস্তবতা ভিন্ন গল্প বলে, যা আপাত অর্থনৈতিক গতিশীলতা সত্ত্বেও বৈদেশিক মূলধনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সম্ভাব্য অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোর ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতাংশ হিসেবে এফডিআইয়ের প্রবণতা পরীক্ষা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র উঠে আসে। ২০১৩ সালে এফডিআই জিডিপির ১.৭৪ শতাংশে পৌঁছেছিল, যা পরবর্তীতে ২০২৩ সালে মাত্র ০.৩২ শতাংশে নেমে আসে। এই উল্লেখযোগ্য হ্রাস ইঙ্গিত করে যে, সামগ্রিক অর্থনীতি যথেষ্ট প্রসারিত হলেও বৈদেশিক বিনিয়োগ সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। যা দুর্বল বিনিয়োগ আস্থা বা বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে নতুন বাধার উত্থানের ইঙ্গিত দেয়। ২০২২ সালে এফডিআই প্রবাহে কিছুটা ইতিবাচক গতি দেখা গেলেও, তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। কারণ, ২০২৩ সালে প্রবাহ হ্রাস পায় ১৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে নেট এফডিআই হয়েছে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২২ সালে ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এফডিআই প্রবাহ ৪৭৫ মিলিয়ন ডলার কমেছে। এই ওঠানামা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর প্রতি বৈদেশিক বিনিয়োগের সংবেদনশীলতাকে তুলে ধরে। এফডিআই প্রবাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সাম্প্রতিক মন্দার কারণগুলো বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের এফডিআইর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পরীক্ষা করলে আরও দেখা যায় যে, ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে এবং মাঝামাঝি সময়ে একটি প্রবৃদ্ধির সময়কাল ছিল, যা ২০১৫ সালের দিকে শীর্ষে পৌঁছেছিল। এর পর থেকে একটি সাধারণ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়, যা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনা, শাসনক্ষমতার দুর্বলতা এবং কোভিড-১৯ মহামারি ও ইউক্রেনের সংঘাতসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং বাহ্যিক কারণ উভয়ের গুরুত্বকে তুলে, ধরে যা বিনিয়োগকারীর আস্থা তৈরি করে এবং বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহকে প্রভাবিত করে।
এবারের বিনিয়োগ সম্মেলনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মূল জানার বিষয় থেকেই স্পষ্ট হয়। তারা এবার জানতে চেয়েছেন, এ দেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণমূলক যেসব সমস্যা রয়েছে, যেমন- এক নম্বর আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন, সুশাসনের অভাব, আইনের জটিলতা, প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা, সমন্বয়ের অভাব, নীতিনির্ধারকদের ঘুষ-দুর্নীতির মানসিকতা ইত্যাদি। এসব কথা অর্থনীতিবিদরা বহু বছর ধরেই বলে আসছেন। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য যে নীতিনির্ধারক প্রয়োজন, তা বাংলাদেশে নেই। তারা নবসময় আগে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকেন। স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যে শুল্কহার বেড়ে যাবে। কারণ, তখন পণ্য রপ্তানিতে বর্তমান বাজারসুবিধা থাকবে না। বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে সবচেয়ে বেশি হারে শুল্ক বাড়বে। ফলে প্রধান বাজারগুলোয় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি পরিবেশ ও শ্রমসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পরিপালনে বিনিয়োগ করতে হবে। তখনও যদি এসব সমস্যা থাকে, তবে কোনো সরকারের পক্ষেই সুস্থভাবে শাসনক্ষমতা চালানো সম্ভব হবে না। কারণ, বিশ্ব অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশীরা সেসব দেখছেও।
অথচ দেশের কৌশলগত চারটি খাতে প্রয়োজনীয় নীতিগত পদক্ষেপ নিলে প্রতি বছর এসব খাতে প্রায় ৩৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব। খাত চারটি হলো- আবাসন, পেইন্ট অ্যান্ড ডাইস, তৈরি পোশাকশিল্প ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা। দেশের আবাসন খাতে ডিজিটাল ম্যাপিং, জমি নিবন্ধন ও জমির অতিরিক্ত দাম নিয়ে জটিলতা রয়েছে। আবার শিল্পের রঙের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লাগে। শুল্কের হারও অনেক বেশি। ডিজিটাল আর্থিক সেবায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ে মার্চেন্টদের লেনদেন সীমা বাড়ানোর মতো কিছু জটিলতা আছে। কর্মসংস্থাান বাড়াতে হলে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম বড় সমস্যা অবকাঠামো। এটি সমাধান করা গেলে বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিমাণ দু-তিন গুণ বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া পরিবহন ও সরবরাহ খাত, গ্যাস-বিদ্যুতের মতো বিভিন্ন পরিষেবা এবং শুল্ক-কর নিয়েও নিয়মিত সমস্যায় পড়তে হয় । বাংলাদেশ যেহেতু এখন এলডিসি থেকে উত্তরণ-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই নতুন বাস্তবতার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো হ্রাস করতে এবং সুযোগগুলো কাজে লাগাতে একটি ব্যাপক কৌশল তৈরি করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে প্রধান অংশীদারদের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তিগুলোর জন্য সক্রিয়ভাবে আলোচনা করা, আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দেশীয় পণ্যগুলোর গুণমান ও মান উন্নত করা, উচ্চমূল্যের খাতগুলোতে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণকে সক্রিয়ভাবে প্রচার এবং কৌশলগতভাবে এই ক্ষেত্রগুলোতে এফডিআই আকর্ষণ করা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে এলডিসি-পরবর্তী অনুকূল বাণিজ্য শর্তাবলী সুরক্ষিত করার জন্য এবং জিএসপি+ এর মতো বিকল্প অন্বেষণ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ।
বিনিয়োগ সম্মেলনের প্রত্যাশা-
বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৫-এ তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ ঘোষণা প্রাপ্তির চেয়েও বেশি যেসব প্রত্যাশা ছিল, তার মধ্যে রয়েছে-
ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ : বিভিন্ন খাত যেমন- রিনিউয়েবল এনার্জি, ডিজিটাল ইকোনমি, বস্ত্র ও পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।
নীতি সংস্কারের প্রদর্শন: বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করার জন্য সরকারের গৃহীত নীতি সংস্কারগুলো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরা।
যোগাযোগ ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, নীতি নির্ধারক এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও অংশীদারিত্ব তৈরি করা।
বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি: একটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং সুযোগপূর্ণ অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।
নির্দিষ্ট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা লাভ: বিভিন্ন খাত থেকে বিনিয়োগ প্রস্তাবনা এবং সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষর করা।
বিনিয়োগ সম্মেলনের প্রাপ্তিÑ
বলা যায়, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৫ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে-
বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ: প্রায় ৫০টি দেশ থেকে ৪১৫ জন বিদেশী প্রতিনিধি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন।
প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা: শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা সমমূল্যের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। আরও বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা যায়।
সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর: সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখযোগ্য সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশের যোগদান, যা মহাকাশ অনুসন্ধানে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। এ ছাড়াও রিনিউয়েবল এনার্জি খাতে সহযোগিতার জন্য সোলার পাওয়ার ইউরোপ এবং বাংলাদেশ সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সচেতনতা বৃদ্ধি: এই শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে অথ্যন্ত সহায়ক হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।
খাতভিত্তিক আলোচনা: সম্মেলনে রিনিউয়েবল এনাজি, ডিজিটাল ইকোনমি, বস্ত্র ও পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
উদ্বেগ-চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের পথ-
কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বিশেষ করে কারখানার লাইসেন্স, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ (প্রায় দুই বছর পর্যন্ত), নীতিগত অসামঞ্জস্যতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতা এখনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এবারের সম্মেলন নিঃসন্দেহে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে সরকারের গৃহীত বিনিয়োগবান্ধব নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ নিরসনের ওপর। বিনিয়োগের প্রস্তাবনাগুলোর বাস্তবে রূপ দিতে নিয়মিত ফলো-আপ এবং একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা অপরিহার্য। একই সঙ্গে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও আকর্ষণীয় বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৫ বিদেশী বিনিয়োগের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তবে অতীতের চ্যালেঞ্জ ও অপারগতা মনে রেখেই রচনা করতে হবে সামনের পথ। এজন্য বাংলাদেশকে লক্ষ্যযুক্ত নীতি সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে, অবকাঠামোতে কৌশলগত বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং শাসন ও সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশে যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উচ্চমূল্যের বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য মানবপুঁজি ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ অপরিহার্য। বাংলাদেশকে জরুরি ভিত্তিতে তার শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার গুণমান ও প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করার ওপর মনোযোগ দিতে হবে। যাতে দেশীয় ও বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীর, বিশেষ করে উদীয়মান ও উচ্চপ্রযুক্তি খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকারী একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা যায়। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের চিহ্নিত ঘাটতি মূলত জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করছে। তাই মানবপুঁজি উন্নয়নে কৌশলগত বিনিয়োগ, শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার দৃঢ় সংযোগ গড়ে তোলার পাশাপাশি, সহজে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে সক্ষম দক্ষ কর্মীবাহিনী নিশ্চিত করতে হবে, যা বাংলাদেশকে উচ্চমূল্যের এবং প্রযুক্তিনিবিড় বিনিয়োগের জন্য একটি আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল