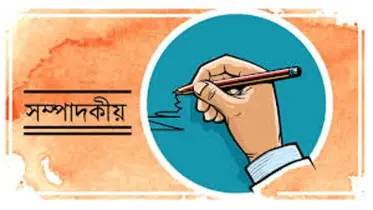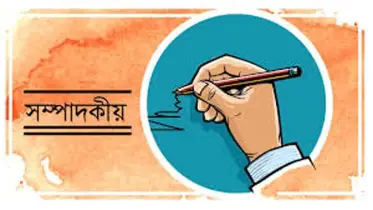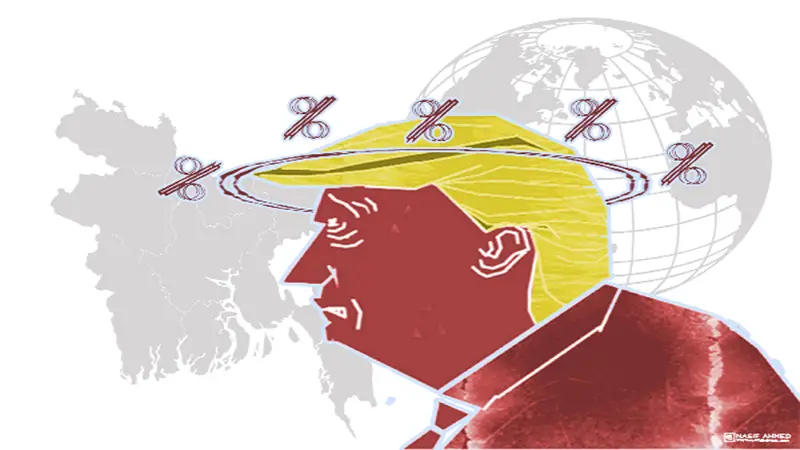
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঐতিহাসিক ‘পারস্পরিক শুল্ক’নীতি বৈশ্বিক বাণিজ্যে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছে, এর সরাসরি আঁচ লেগেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত তৈরি পোশাকেও (আরএমজি)। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর নতুন করে ৩৭ শতাংশের পর রপ্তানি শুল্ক ৫২-৫৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পোশাক খাত ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রক্রিয়াও এতে ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তানের মতো অন্যান্য দেশের ওপর আরোপিত শুল্ক ও অন্যান্য বাধা। বাংলাদেশের তুলনায় এসব দেশের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেশি। তাই তাদের শঙ্কাও বেশি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩ মাসের জন্য নতুন শুল্ক স্থগিতের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন পণ্যে শুল্ক কমানোরও প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের ৫০টি দেশ নতুন শুল্কের ব্যাপারে ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেন-দরবার শুরু করেছে। ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যে শূন্য শুল্কের প্রস্তাব করেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা নতুন শুল্ক কার্যকর করার সময় পিছিয়ে দেওয়ার আবেদনও করেছে তারা। কম্বোডিয়া বলেছে, মার্কিন পণ্যের ১৯টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যমান ৩৫ শতাংশ ওপর শুল্ক কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হবে। ভারত কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আলোকে বিষয়টির প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছে। তবে আমার কথা এই যে, আপাতত চীন ছাড়া অন্য দেশগুলোর ওপর ৯০ দিনের জন্য শুল্কারোপ স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
সামগ্রিক বাজার পর্যালোচনায় সাধারণভাবে বলা যায়, সস্তা শ্রমের ওপর ভিত্তি করে ভালো মানের পণ্য উৎপাদনকারী বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ট্রাম্পের নতুন শুল্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার উদীয়মান পোশাক রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আরও তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। তবে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। যেমন- বাংলাদেশের চেয়ে ভিয়েতনাম, চীন ও কম্বোডিয়ার ওপর মোট শুল্কের হার বেশি। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কের পোশাক খাতের ওপর বাংলাদেশের তুলনায় শুল্ক কম। এ ছাড়া দাম বাড়লে ভোক্তা চাহিদা কমতে পারে। তবে একটি ইতিবাচক দিক হলো, বাংলাদেশ মূলত মধ্য ও নিম্নমূল্যের পোশাক রপ্তানি করে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ ততটা ব্যাপক নাও হতে পারে। বাংলাদেশের মোট বৈশ্বিক রপ্তানির ১৮-২০ শতাংশ যায় সে দেশে। মার্কিন ফ্যাশন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বড়জোর বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ বাজার হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। তবে বেশকিছু সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিলে বাংলাদেশ ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে। কারণ, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যে ৮৪০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, তার মধ্যে ৭৩৪ কোটি ডলারই ছিল তৈরি পোশাক। এসব পোশাকের বেশির ভাগই আবার ছিল সস্তা ও কম মূল্য সংযোজন ক্ষমতার নন-নিট পুরুষ ও মহিলাদের স্যুট, শার্ট ও নিটওয়্যার। এ ধরনের পণ্যের চাহিদাতেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ মূল্য সংযোজন ক্ষমতার পোশাকের চাহিদায় চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, হন্ডুরাস, পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো অতিরিক্ত শুল্কের কারণে বাজার হারাতে পারে। এ ছাড়াও ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীন প্রথম অবস্থানে থাকলেও গত এক দশকে তাদের রপ্তানি প্রায় অর্ধেক কমেছে। সেই জায়গায় ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। এখন নতুন পরিস্থিতিতে প্রতিযোগীর সংখ্যা আরও বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে বাংলাদেশের প্রধান পোশাক গন্তব্য হলেও নানামুখী চাপ ও সংকট মোকাবিলা করেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারকের স্থান ধরে রেখেছে। এ খাত ২০২৪ সালে মোট জাতীয় রপ্তানির ৮৩ শতাংশ জুড়ে ছিল।
বাংলাদেশের সার্বিক ক্ষতির পর্যালোচনায় পোশাক খাতের প্রতিযোগী দেশগুলোর নতুন শুল্ক পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এতে পোশাক খাতে সংশ্লিষ্টদের হিসাব-নিকাশ, সহজ হবে। ভারতের সংবাদপত্রগুলো তাদের উগ্রবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের গভীর বন্ধুত্বের কথা বলে অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ প্রশমনের চেষ্টা করলেও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন থেকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো বাণিজ্য আলোচনায় ভারতকে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে, কেন ভারতের গড় মোস্ট ফেভারড নেশন (এমএফএন) প্রয়োগকৃত শুল্কহার ২০২৩ সালে (সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী) ছিল ১৭ শতাংশ, যা বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। মার্কিন কর্মকর্তারাও মনে করেন, যদি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এড়াতে চায়, তাহলে নয়াদিল্লিসহ বড় বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোকে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তারা চীন, ভারত, ভিয়েতনামের মতো বড় বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন যে, এসব দেশ এবার সহজে নিস্তার পাবে না। ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘দশকের পর দশক ধরে আমাদের দেশকে দূর ও নিকটবর্তী শত্রু-মিত্র সবাই মিলে লুট, ধর্ষণ, শোষণ ও ধ্বংস করেছে। এখন প্রতিশোধের সময় এসেছে। এই দিন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হয়ে থাকবে।’ মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এই হিসাবে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ৬১৫ কোটি ডলার বা ৬.১৫ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে ২০২৪ সালে চীন, ভিয়েতনাম ও ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি যথাক্রমে ২৭০, ১১৩, ৪১.৫ বিলিয়ন ডলার।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, বাংলাদেশ তাদের পণ্যের ওপর ৭৪ শতাংশ শুল্কারোপ করে। যার প্রতিক্রিয়ায় তারা বাংলাদেশী পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ ‘হ্রাসকৃত সম্পূরক শুল্ক’ আরোপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ১ শতাংশ। অন্যদিকে নতুন শুল্কের পর চীনের মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৩৯, ভিয়েতনামের ৯০, তাইওয়ানের ৬৪, জাপানের ৪৬, ভারতের ৫২, দক্ষিণ কোরিয়ার ৫০, থাইল্যান্ডের ৭২, সুইজারল্যান্ডের ৬১, ইন্দোনেশিয়ার ৬৪ এবং মালয়েশিয়ার ৪৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী তুরস্কের ওপর ১০ শতাংশ, ভারতের ওপর ২৭ শতাংশ, পাকিস্তানের ওপর ৩০ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ওপর ৪৪ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ ও কম্বোডিয়ার ওপর ৪৭ শতাংশ শুল্কারোপ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি ২৯৫ বিলিয়ন ডলার। এরপর যথাক্রমে ব্রিটেন ২৭১ বিলিয়ন ডলার, ভারত ২৪১, ফ্রান্স ১৩৭, মেক্সিকো ১৭২, ভিয়েতনাম ১২৩ এবং তুরস্ক ১০৬ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ঘাটতিতে রয়েছে। ট্রাম্প এই বাণিজ্য ঘাটতিকে সামনে এনে শুল্কঝড় শুরু করলেও অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এই বাণিজ্য ঘাটতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আসলে উপকারী। কারণ, এটি ডলারের বৈশ্বিক চাহিদা বজায় রেখে মার্কিন ডলারের রিজার্ভ মুদ্রার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে, যা আংশিকভাবে উন্মুক্ত বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৯২টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে ছিল এবং ১১১টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ছিল। এটা সত্যি যে, ট্রাম্পের নতুন আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পোশাকের চাহিদা কিছুটা কমাবে। তবে চীন ও ভিয়েতনামের ওপর উচ্চ শুল্ক বাংলাদেশের পোশাককে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে। কিন্তু ভারত ও ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য সমঝোতা করে শুল্কে ছাড় পায়, তাহলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডাসহ অন্যান্য বাজারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্যের নীতিগত ও কাঠামোগত বেশকিছু অনিশ্চয়তাসৃষ্ট প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে। যার অন্যতম হলো বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও সরবরাহ শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা।
বাণিজ্যনীতিতে অনিশ্চয়তা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্পষ্টভাবে ব্যাহত করে। যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্কারোপের ফলে অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলা নতুন করে সাজাতে বাধ্য হচ্ছে, যা উৎপাদন ব্যয় ও অদক্ষতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় অটোমোটিভ ও ইলেকট্রনিকস খাত যেমন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি তৈরি পোশাক, ভোগ্যপণ্য ও কৃষিপণ্যের মতো জটিল ও আন্তনির্ভরশীল বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের খাতগুলোও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে কেবল তাদের পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস কিংবা আমদানি বৃদ্ধি একটি সীমিতমুখী কৌশল, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের কাঠামোগত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা ও বাণিজ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের গতি শ্লথ হচ্ছে, উৎপাদন খরচ বাড়ছে, রপ্তানিমুখী শিল্প খাত ঝুঁকিতে পড়ছে এবং শ্রমবাজারে সংকোচন সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যথাক্রমে ১২.৯ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ২৩.১ শতাংশ হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, যা এই প্রভাবের বাস্তব প্রতিফলন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সামনে কেবল নিজেদের সুবিধা নয়, বরং নতুন শুল্ক ব্যবস্থার বহুমাত্রিক প্রভাবসমূহ- বিশেষত বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে-সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা জরুরি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৌশলগতভাবে বোঝানো সম্ভব হবে যে, এমন শুল্ক কাঠামো শুধু উন্নয়নশীল দেশের জন্যই নয়, বরং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকারের জন্যও হুমকি। সেইসঙ্গে কৌশলগতভাবে বিষয়টিকে একটি বহুপক্ষীয় ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। যার সমাধানে কেবল দ্বিপক্ষীয় আলোচনা নয়, বরং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় কূটনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ডব্লিউটিওর ‘বিশেষ ও পৃথক সুবিধা’ নীতিমালার আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় জোরালো অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান ছাড়াও একটি টেকসই ও ন্যায্য বাণিজ্য কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। যা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়নকামী দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়