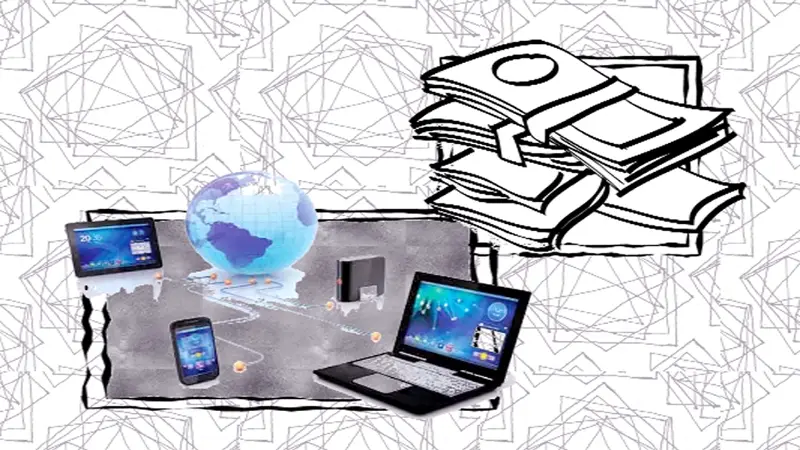
বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ছাড়া একটি দিন কল্পনাও করা যায় না। অফিস, বাসা-বাড়ি, ব্যবসাসহ আমাদের দৈনন্দিন কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে। মুভি দেখা, গান শোনা, মেইল করার মধ্যেই ইন্টারনেটের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষামূলক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, জাতীয় সেবা গ্রহণের জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেষ করা যাবে না । ই-জনেস, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ইন্টারনেটের ওপর। তাই অতীব প্রয়োজনীয় এই ইন্টারনেটের গতি থাকা চাই কাক্সিক্ষত মাত্রায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, প্রত্যাশিত গতির ইন্টারনেট আমরা পাই না। যদিও এর সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেটের গতি দুর্বল আর দাম বেশি হবার মূল কারণ হচ্ছে ইন্সপেক্টর স্পেক্টটার্মের (spectrum) উচ্চমূল্য। স্পেক্টটার্মের প্রাথমিক মূল্যই (base price) অনেক বেশি ধরা হয়, এরপর নিলামে সেই দাম আরও বেড়ে যায়। এতে সরকারের লাভ হলেও শেষ পর্যন্ত মোবাইল কোম্পানি বেশি টাকা খরচ করে বেশি স্পেক্টটার্ম কিনতে চায় না, ন্যূনতম যতটুকু দরকার ততটুকুই কিনে। ফলে গ্রাহক সংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত স্পেক্টটার্ম না থাকায় মোবাইল ইন্টারনেটের গতি দুর্বল হয়। আর যতখানি স্পেক্টটার্ম কিনেছে, তার দামও অনেক বেশি হওয়ায় গ্রাহকদেরই সেই বাড়তি খরচের বোঝা বইতে হয়, ফলে মোবাইল ইন্টারনেটের দামও বেশি হয়। পাশাপাশি মোবাইল কোম্পানিগুলোর অতি মুনাফা করার মানসিকতাও দায়ী। কম লাভে বেশিসংখ্যক মানুষকে মোবাইল ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। দেশের ১৪ কোটির বেশি ইন্টারনেট সংযোগের মধ্যে প্রায় ১৩ কোটিই মোবাইলের মাধ্যমে অন্তর্জালের সেবা নেয়। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ট্রাফিকের জন্য বেশি মূল্য দিতে হয় বলেও দেশের ইন্টারনেট সেবাদাতারা ক্যাশ সার্ভার রাখে। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো গুগল ও মেটার ক্যাশ সার্ভারগুলো। কারণ দেশের সিংহভাগ ইন্টারনেট ট্রাফিকই হয় মেটা ও গুগলের জন্য। কোন কারণে মোবাইল ডেটা ও স্থানীয় ক্যাশ সার্ভার বন্ধ থাকলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের স্পিড স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হয়।
বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা যে পরিমাণ ইন্টারনেট ট্রাফিক তৈরি করে, তার ৮০ শতাংশের বেশি পূরণ করে স্থানীয় ক্যাশ সার্ভারগুলো। ক্যাশ সার্ভার হলো তথ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করার নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক সার্ভার বা সেবা। এতে স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ওয়েবপেজ ও অন্যান্য ইন্টারনেট কনটেন্ট সেভ করা থাকে। অস্থায়ী স্টোরেজ বা ক্যাশ থেকে আগের ব্যবহৃত তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়ে ক্যাশ সার্ভার ইন্টারনেট ডেটার গতি বাড়াতে এবং একইসঙ্গে ব্যান্ডউইথের চাহিদা কমাতে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেটের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ৬,৩০০ জিবিপিএস এর বেশি। ক্যাবল বা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর ৫৫ শতাংশ ব্যবহার হয়। বাকি ৩ হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ব্যবহার হয় মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে। এসব ব্যান্ডউইথের মূল্য পরিশোধ নিয়ে আছে নানা অভিযোগ। বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৩৪টি আইআইজি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টি প্রতিষ্ঠানই সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির বকেয়া মূল্য প্রায় ৩৮৪ কোটি টাকা পরিশোধ করছে না। এর মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠানেরই বকেয়া ১৮১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানগুলো।
প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে ২৭০০-২৮০০ জিবিপিএস (গিগাবিটস পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইথ। বিএসসিসিএল সূত্রে জানা গেছে, দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের (সি-মি-উই-৫) বর্তমান সক্ষমতার (অ্যাক্টিভেট ক্যাপাসিটি) পুরোটা (১৩০০ জিবিপিএস) প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল সি-মি-উই-৪-এর সক্ষমতার ৬০০ জিবিপিএসেরও একই অবস্থা হয়। দুটি মিলিয়ে দেশের মোট ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথের মধ্যে দুই সাবমেরিন ক্যাবল থেকে আসে ১৮৫০ জিবিপিএস। বাকি ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করছে আইটিসি (ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল)। সূত্র মতে, বর্তমানে বিএসসিসিএল ৯০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথের (সি-মি-উই-৫) সার্কিট আপ (সক্রিয়) সঙ্গে নতুন ৬০০ জিবিপিএস যুক্ত হয়েছে। আরও ৩০০ জিবিপিএস একই ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার কথা। ফলে সি-মি-উই-৫-এর ব্যান্ডউইথ দাঁড়াবে ২২০০ জিবিপিএস। কিন্তু আইআইজিগুলো (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) দেশের সব জায়গায় পপ (পয়েন্ট অব প্রেজেন্স) স্থাপন করতে পারেনি। ইন্টারনেটে ধীর গতি হওয়ার এটাও আর একটা প্রধান কারণ। এজন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও মোবাইল ইন্টারনেটে উভয়ে ভর করেছে ধীরগতি। ফোর-জি নেওয়ার্কে ভিডিও দেখার সময় বাফারিং হওয়া হালে প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটেও এ সমস্যা। সব মিলিয়ে গ্রাহকের শুধুই ভোগান্তি।
যাহোক বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড বা মোবাইল ইন্টারনেটের খরচ অত্যন্ত বেশি অনেকদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন গ্রাহকরা। মোবাইল ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জিএসএমএ এর তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের মূল্য নিয়ে জরিপকারী যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান ‘ক্যাবল’ হিসাবে, বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে কম খরচ ভারতে, প্রতি জিবি ইন্টারনেটের পেছনে গড় খরচ হয় শূন্য দশমিক ৯ মার্কিন ডলার। খরচের সেই তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ১৯ নম্বরে, যেখানে প্রতি জিবি ইন্টারনেটের পেছনে গড় খরচ হয় শূন্য দশমিক ৭০ মার্কিন ডলার। গ্রাহক পর্যায়ে খরচ বেশি অথচ সেবা কমের প্রধান কারণ হলো ব্যান্ডউইথ থ্রোটলিং। ব্যান্ডউইথ থ্রোটলিং বলতে বুঝায়, ইন্টারনেটে কোনো কিছুর অ্যাক্সেস কত দ্রুত গ্রহণ করতে পারে তার গতিসীমা। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বা মোবাইল ইন্টারনেটে যে পরিমাণ গতি পাওয়ার জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয়, সে পরিমাণ গতি না দিয়ে যদি তা কমিয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে ব্যান্ডউইথ থ্রোটলিং বলে। এর আর এক নাম হলো ডাটা থ্রোটলিং বা ইন্টারনেট বটলনেক। ধরুন, আপনি যদি কোনো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের ৫ এমবিপিএস স্পিডের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের জন্য টাকা দিয়ে থাকেন আর ওই প্রতিষ্ঠান যদি আপনাকে দিনের কোনো এক সময়ে নির্ধারিত গতি আপনাকে না দিয়ে থাকে তাহলে ওই সার্ভিস প্রোভাইডার আপনার ডাটা থ্রোটলিং করছে। আবার অনেক আইএসপি টরেন্টিং করার সময় থ্রোটলিং করে থাকে। সাধারণ ইন্টারনেট গতি হয়তো ভালো পাবেন, কিন্তু টরেন্ট ব্যবহার করার সময় গতি প্রত্যাশিত থাকবে না।
ব্যান্ডউইথ থ্রোটলিং সাধারণত আপনার আইএসপি-ই করে থাকে। কিন্তু আরও অনেকভাবে ডাটা থ্রোটলিং হতে পারে। আপনার ডিভাইসের যদি ততটা গতি সমর্থন করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আপনার ফোন বা কম্পিউটারই এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বটলনেক হিসেবে কাজ করবে। ডাটা থ্রোটলিং ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। ব্যান্ডউইথ থ্রোটলিং মাধ্যমে তারা অনেক অর্থও উপার্জন করে। বিশেষ করে ডাটা থ্রোটলিং পদ্ধতিটি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডাররাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। যেমন ধরুন, আপনার আইএসপির দিনের এমন কিছু সময় যখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনেক বেড়ে যায়, তখন সবাইকে ভালো স্পিড সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তাই ইউজারদের ব্যান্ডউইথ স্পিড কমিয়ে দেয়। এতে তাদের বেশি ইউজার হ্যান্ডেল করার জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় হতো, সেটার খরচ থেকে তারা বেঁচে যায়। অনেক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনো সাইটে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে রাখে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউটিউব, ফেসবুক, অনলাইন টিভি। এই সাইটগুলোতে ডাউনলোড হয় অনেক। তবে শুধু ইন্টারনেট সার্ভিস ডাটা থ্রোটলিং করে না। শেয়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেও গ্রাহক পর্যায়ে তারা ইন্টারনেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। যাহোক, টেলিযোগাযোগ খাতে শুভংকরের ফাঁকি দিচ্ছে মোবাইল অপারেটররা। গ্রাহক সেবায় নির্ধারিত অবকাঠামো ব্যবহার করছে না তারা। কাক্সিক্ষত সেবা না পাওয়ার বিস্তর অভিযোগ জমা পড়ছে বিটিআরসিতে। সংস্থাটি বলছে, গ্রাহকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ নির্দেশনা দেয়া হলেও, সমস্যা সমাধানে মোবাইল অপারেটরদের অনীহা ও দীর্ঘসূত্রিতা এখন স্পষ্ট। অন্যদিকে অপারেটরদের অভিযোগ, লাইসেন্স ফি ও তরঙ্গের উচ্চমূল্যের কারণে, গ্রাহক সেবায় বিনিয়োগ বিঘ্নিত হচ্ছে।
লেখক : অধ্যাপক এবং তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়








