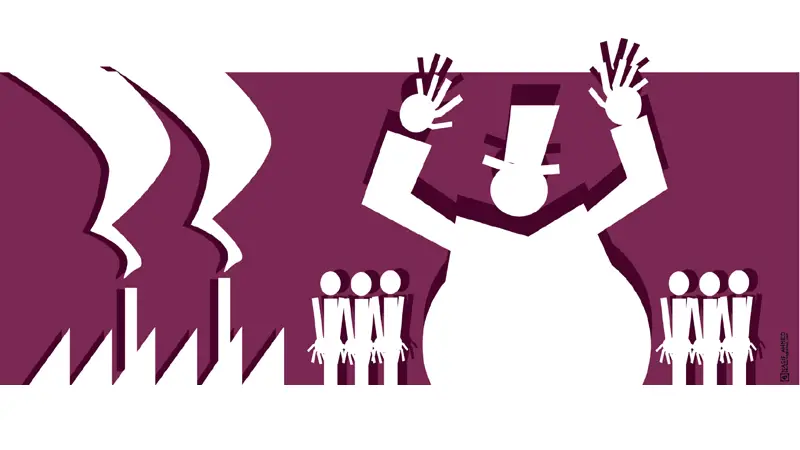
ক্যাপিটালিজম (ঈধঢ়রঃধষরংস) বা পুঁজিবাদ হলো এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, উৎপাদন উপায়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং লাভের জন্য তাদের পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে পুঁজিবাদকে একটি মুক্তবাজার অর্থনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বে জনপ্রিয় দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদ অন্যতম এবং অন্যটি হলো সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কোনো কিছুতে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পুঁজিবাদের ঠিক বিপরীতে হলো সাম্যবাদ (ঈড়সসঁহরংস)।
এই ব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কোনো কর্তৃপক্ষ থাকে না বা কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকে না এবং উৎপাদনকারীর সরবরাহ ও ভোক্তার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কি ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হবে বা একটি পণ্য কতটুকু উৎপাদন করা হবে তা ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করা হয় না। বরং উৎপাদন করা হয় একমাত্র ক্যাপিটালিস্টদের ইচ্ছা অনুযায়ী। আর তাদের একমাত্র ইচ্ছাই হলো মুনাফা অর্জন করা। অর্থাৎ যে পণ্য উৎপাদন করলে তাদের অধিক লাভ সেই পণ্যই তারা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে।
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিযোগিতা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সকল পুঁজি অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা যেহেতু ব্যক্তির কাছে থাকে, তাই সেখানে প্রতিযোগিতা থাকে বেশি। প্রতিযোগিতা হলে কেউ এগিয়ে যাবে, কেউ পিছিয়ে পড়বে। কারও এগিয়ে যাওয়া আর কারও পিছিয়ে পড়া মানে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া। এগিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা উঁচু শ্রেণিতে উঠে গিয়ে নিচের দিকে আর ফিরে তাকান না। যাঁরা নিচে পড়ে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁরা আর মেলামেশা করেন না। এখান থেকেই আসে নিঃসঙ্গতার বিষয়টি। নিঃসঙ্গতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং পুঁজিবাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে এর উন্নতি ও সংস্কার করা জরুরি।
পুঁজিবাদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অর্থ বিনিয়োগ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়, উচ্চস্তরের মজুরি শ্রম, প্রতিযোগিতাকে ব্যবহারের মধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ করার জন্য মূল্য প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূল্য সংযোজন সর্বাধিকীকরণের কারণে কাঁচামাল এবং উৎপাদনের প্রভাবসমূহের অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ ব্যবহার করা ।
পুঁজিপতিদের ব্যবসা এবং বিনিয়োগ পরিচালনার জন্য তাদের স্বার্থে কাজ করার স্বাধীনতা থাকে। তারা কখনোও ভোক্তার কথা চিন্তা করে না। পুঁজিবাদপতিরা তাহলে কাদের কথা চিন্তা করে? মূলত পুঁজিবাদপতিরা সব সময় তাদের লাভের কথা চিন্তা করে।
পুঁজিবাদীরা কাজ করে মুক্ত বাজার এবং লেসে-ফেয়ার কাঠামোতে, বাজারগুলো দামের প্রক্রিয়ার ওপর ন্যূনতম বা কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সর্বাধিক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে, যা আজ প্রায় সর্বজনীন। বাজারগুলো একটি প্রভাবশালী ভ‚মিকা পালন করে চলেছে। তবে বাজারের ব্যর্থতা সংশোধন, সামাজিক কল্যাণের প্রচার, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, তহবিল প্রতিরক্ষা এবং জননিরাপত্তা বা অন্যান্য মূল নীতি কিছু পরিমাণে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুঁজি সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ বা পরোক্ষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, বাজারগুলো নির্ভর করে।
প্রতিযোগিতা দেখা দেয় তখনই, যখন একাধিক প্রযোজক একই ক্রেতাদের কাছে একই বা অনুরূপ পণ্য বিক্রি করার চেষ্টা করে। পুঁজিবাদী তত্তে¡র অনুগামীরা বিশ্বাস করেন যে প্রতিযোগিতা উদ্ভাবন এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের দিকে নিয়ে যায়। একচেটিয়া বা কার্টেল বিকাশ করতে পারে তখন, যখন বিশেষ করে যদি কোনো প্রতিযোগিতা না থাকে। একটি একচেটিয়া ব্যাপার ঘটে যখন একটি ফার্ম একটি বাজারে একচেটিয়া অবস্থায় থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, বাজারের প্রতিযোগিতা মূলত মূল্য, পণ্য, বিতরণ এবং প্রচারের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বিক্রেতাদের মধ্যে লভ্যাংশ বৃদ্ধি, বাজার শেয়ার অর্জন এবং বিক্রয় পরিমাণ বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে বোঝায়। গবৎৎরধস-ডবনংঃবৎ-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা হলো দুটি বা তার বেশি পক্ষের মধ্যে এমন প্রচেষ্টা, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং সেরা শর্তে তৃতীয় পক্ষের ব্যবসা লাভের চেষ্টা করে। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত দ্য ওয়েলথ অব নেশনস-এ অ্যাডাম স্মিথ ও পরবর্তী অর্থনীতিবিদরা বাজার প্রতিযোগিতাকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা সম্পদের কার্যকর বরাদ্দ ও উৎপাদনশীলতাকে উৎসাহিত করে। স্মিথ ও অন্যান্য ধ্রæপদী অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, প্রতিযোগিতা কেবল বিক্রেতাদের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি মূলত মূল্য ও অমূল্যের ভিত্তিতে ক্রেতাদের মধ্যে বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
মোটকথা, বাজার প্রতিযোগিতা এমন একটি অবস্থা যেখানে ক্রেতারা একে অপরের সঙ্গে এবং বিক্রেতারা অন্যান্য বিক্রেতাদের সঙ্গে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করে। ক্রেতারা নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য কেনার জন্য বিড করে, আর বিক্রেতারা ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং তাদের সম্পদ বিনিময় করতে প্রতিযোগিতা করে। এই প্রতিযোগিতা মূলত অভাব থেকে উদ্ভূত হয়। কারণ মানুষের সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয় এবং তাই তারা বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত মানদÐের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
অ্যাডাম স্মিথের লেখায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও স্মিথের সময় পুঁজিবাদ মূলধারার অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠেনি, তিনি এটিকে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। প্রতিযোগিতা পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং স্মিথ বিশ্বাস করতেন যে, একটি সমৃদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলোÑ যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ, প্রস্থান এবং ব্যবসার ধরন পরিবর্তনের সুযোগ থাকা উচিত। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করার স্বাধীনতা একটি পুঁজিবাদী সমাজের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে সামাজিক মঙ্গল বাধাগ্রস্ত হতে পারে। স্মিথ বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে, ব্যক্তি যখন নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, তখন সমাজের সামগ্রিক উন্নতি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকলেও বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা খুব বেশি পরিবর্তিত হবে না। স্মিথ আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিযোগিতা সমাজের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মানুষ যখন একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ আরও ভালোভাবে সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। ফলে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়।
লেখক: শিক্ষার্থী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়








