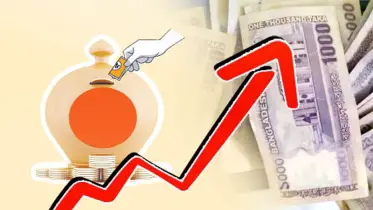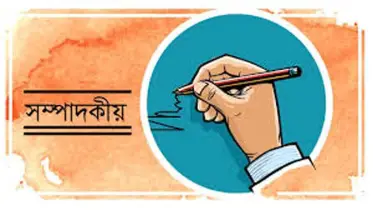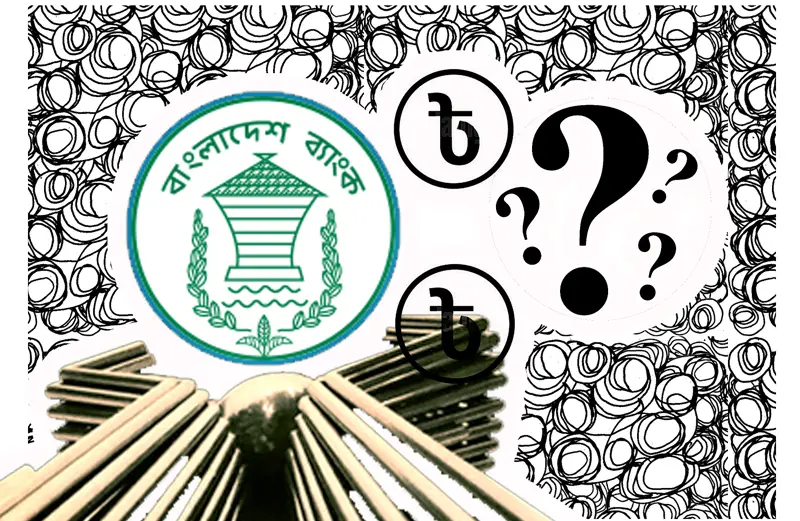
দেশের অর্থনীতির দিনকাল এখন মোটেও ভালো যাচ্ছে না
অস্বীকার বা ডিনায়াল সিনড্রমে ভোগা নীতিনির্ধারকদের নানা মুনির নানা মতের মতো বৈপরীত্যে ভরা বক্তব্যে জনমনে যে সংশয়, উৎকণ্ঠা, ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়, তা মুক্তবাজারের রেফারিদের (বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ) বলে দেওয়ার দায়িত্ব নয়। অর্থনীতিবদরা হয়তো টক শো ও গোলটেবিল মাতিয়ে, বক্তব্য-বিবৃতিবাজি করে জনমনের শঙ্কাকে আরও উস্কে দিয়েছেন। তাই বলে কি ‘অর্থনীতি বোঝেন না’ বলে সবাইকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে হবে? যদি তা-ই হয় তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন কেন বলছে, দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি
সরকার মনে না করলেও অনেকের মতে দেশের অর্থনীতির দিনকাল এখন মোটেও ভালো যাচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি অনেকটা লাগামছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতির দিকে, ডলার সংকট এবং ডলারের বিপরীতে টাকার ধারাবাহিক দরপতন ঘটছে, রপ্তানি ও রেমিটেন্স আয় কমেছে, রাজস্ব উপার্জনে ব্যর্থতা আরও বেড়েছে, বেড়েছে অর্থ পাচার, কালো টাকার বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে, বাজার ব্যবস্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে গেছে এবং সর্বোপরি মানুষের মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। অর্থনীতি সংকটে আছে বলে যারা মনে করেন তাদের অভিমত, দেশের মুদ্রানীতির ওপর নির্ভরশীল মূল্যস্ফীতি, মুদ্রার বিনিময় হার, খেলাপি ঋণ, অর্থ পাচার, কালো টাকার উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের বিষয়গুলো দেখভাল করা যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব, সেহেতু অর্থনীতির এই খাতের সংকটের জন্য এই সংস্থাটিই দায়ী।
এর কারণেই জনজীবনে যত উটকো দুর্ভোগ নেমে এসেছে। সাদা চোখে এটি সত্য বলে মনে হয়। তবে সত্য অস্বীকারের রোগজর্জরিত এই যুগে এসে ওপর থেকে যা দেখি তার সবই কি সত্যি হয়? আসলেই কি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতটাই অদক্ষ ও অথর্ব যে, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পানে চলতে থাকা দেশের অর্থনীতিকে তারা নানামুখী সংকটের মধ্যে এনে ফেলেছে? অর্থনীতি শাস্ত্রঘনিষ্ট মানুষ হিসেবে দিনকয়েক ধরেই মনের মধ্যে এসব প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু মন নিজের মতো করেই সেসবের উত্তর খুঁজেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ে মনের মধ্যে সাম্প্রতিক এসব প্রশ্ন উদয়ের শুরু মূলত সংস্থাটির দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষকে বৈঠকে ডাকার পর থেকে। সাধারণত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির নীতিনির্ধারকদের হরহামেশাই কথাবার্তা হয়, যা ব্যবসায়ীনির্ভর নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয় কালেভদ্রে, বিশেষত বাজেট ঘোষণার আগে রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে। এবার বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় ডেকেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো জানতে চাইছে কী করলে ভালো হয়, কেমন করে করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।
এ অবস্থায় কেউ কেউ বলতে পারেন দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনীতিবিদদের ‘গোনায় না ধরা’ দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতিনির্ধারকদের সাম্প্রতিক এই উদ্যোগে অর্থনীতিবিদদের তৃপ্তি পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কারণ, তাদের কদর কিছুটা হলেও তো বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সচরাচর এমনটি করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই কি এই উদ্যোগে অর্থনীতিবিদদের তৃপ্তির সুযোগ আছে, কিংবা এতে করে অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাবে? অনেকের মনে এ নিয়ে সন্দেহ আছে। কেননা, দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা ব্যক্তিবর্গ তো স্বীকারই করেন না যে, দেশের অর্থনীতিতে কোনো সংকট আছে, অর্থনীতিবিদদের কথাবার্তায় ভালো কিছু আছে। তাদের দৃষ্টিতে, যারা বলছেন দেশের অর্থনীতি ভালো নেই তারা অর্থনীতিই বোঝেন না। শুধু আশঙ্কা প্রকাশ করতেই দক্ষ।
সরকারের ভালো কিছুই দেখতে পান না। আমাদের নীতিনির্ধারকদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে অর্থনীতির মূলধারার মানুষদের বৃদ্ধিবৃত্তিক ও নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্মের সম্ভবত কোনো যোগসূত্র আছে। নীতিনির্ধারকেরা হয়তো মনে করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উচ্চতর প্রযুক্তি আর যে কোনো মূল্যেই হোক নিজের সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করার এই যুগে এসে অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাপোষা লোকদের কি মূল্য আছে? কারণ, ঘটনার ভেতরের ঘটনাটা কী, চেহারার ভেতরের আসল রূপটা কী, অন্তঃস্থিত বিষয়ের কার্যকারণগুলো কী কিংবা কী হলে কী হয়, কেন এমন হয় প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর মুক্তবাজারনির্ভর আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা হয় সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেন, না হয় ব্যাখ্যার সময় এতটাই জটিল করে ফেলেন যে, শেষে আসল কথাটুকুই হারিয়ে যায়।
এ কারণেই হয়তো অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল মূলধারার অর্থনীতিবিদদের উদ্দেশ করে বলেন, ‘এরা সবাই চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ। এরা অনেকেই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ছিলেন, কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে গেছেন। কেউ কিছুই করে দেখাতে পারেননি। আমিও অর্থনীতিবিদ, তবে আমি মূল্যায়নকারী অর্থনীতিবিদ। কারণ, আমি অ্যাকাউন্টসের ছাত্র।’
অর্থনীতি শাস্ত্রের মতে বাজার অর্থনীতিতে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি উভয়ই নীতিনির্ধারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক হাতিয়ার। এই দুই নীতির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য তা অনেকাংশেই প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক নয়। বাজেটের আকার, বাজেট ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং অর্থায়নের পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে রাজস্বনীতি। আর মুদ্রানীতি কাজ করে মুদ্রা সরবরাহ, ঋণ ও সুদের হারের ওপর তার প্রভাবের ভিত্তিতে। এই দুই নীতিই মূলত সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রে নাগরিকদের চাহিদাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ দৃষ্টিতে রাজস্বনীতি প্রণয়ন অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজ। আর মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।
এই দুই অঙ্গের সম্মিলিত প্রয়াসেই অর্থনীতির চাকা সচল থাকে, অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটে। তাই এখন যেহেতু মূল্যস্ফীতি অনেকটা লাগামছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতির দিকে, ডলার সংকট এবং ডলারের বিপরীতে টাকার ধারাবাহিক দরপতন ঘটছে, অর্থনীতিতে যদি কোনো সংকট থেকে থাকে তাহলে তার দায়ভার বাংলাদেশ ব্যাংকের। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পক্ষের লোকজন হয়তো বলবেন, নিউইয়র্কভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ‘ডি গ্রেড’ পাওয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যর্থতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই মতের অনুসারীরা এ কথা কখনো বলেন না যে, রাজনৈতিক চাপ, সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতির সংকটে বড় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।
তারা বলেন না যে, পুঁজিবাদী মুক্তবাজার ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের নিরঙ্কুশ রাজত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো আসলে বলির পাঁঠা মাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত, যদি কিছু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যেত। যেমনÑ আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আসলে কি স্বাধীন, নাকি সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন? কেন স্বাধীন বাংলাদেশে ৫২ বছরের ইতিহাসে ১২ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র একজন অর্থনীতির শিক্ষক, তিনজন পেশাদার ব্যাংকার, আর আটজন সরকারের অনুগত আমলা হলেন? কেন সাধারণ্যে ধারণা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অর্থমন্ত্রীর অধীনে চাকরি করেন? কিংবা কেনইবা বাংলাদেশ ব্যাংক নাকি অন্য কারও প্রত্যক্ষ মদদে দেশের ব্যাংক ঋণের সিংহভাগ অংশ বিপজ্জনকভাবে গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়ে আছে?
পুঁজিবাদী আর্থিকীকরণ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে মূল কাজ হলো- মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখা, মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থা দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাণিজ্যচক্রের ওঠা-নামা সমন্বয় করে অর্থনীতিকে সংযত রাখা। বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন ভালো করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন সুদের হার কম রেখে পুঁজিপতিদের সস্তায় দেদারসে ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অনুৎপাদনশীল খাতে সেসব ঋণ ব্যবহার করে পুঁজিপতিরা যখন অর্থনীতির চাকা স্থবির করার দিকে নিয়ে গেছে তখন নানা কলাকৌশলে তাদের ঋণ তফসিল, পুনঃতফসিল ও মার্জনা করা হয়েছে। পুঁজিপতিরা আবারও ঋণ নিয়েছে, টালবাহানা করেছে, তারপর আবার সুযোগ পেয়েছে। এভাবেই দীর্ঘদিন সবকিছু চলেছে।
এখন যখন অর্থনীতিতে একসঙ্গে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন সুদের হার অনেকটাই বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডলারের মূল্যমান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাজারের হাতে। এতে কিন্তু হরর মুভির জোমবির মতো দৈত্যসদৃশ পুঁজিপতিরা আরও লাভবান হয়েছেন। কারণ এখন তাদের সম্পদ, অ্যাসেট, স্টক, বাড়িঘর, দালানকোঠা, সোনাদানা, কল-কারখানা প্রভৃতির মূল্যমান বেড়ে গেছে। এই সুযোগে তারা সম্পদের পাহাড় নিয়ে অর্থের মহোৎসব করছেন, আর জাতীয় নির্বাচনসৃষ্ট ‘অনিশ্চয়তা’র ভয়ে বিপুল বিক্রমে দেদার বিদেশে নানা কৌশলে টাকা পাচার করছেন। পক্ষান্তরে, পোড়া কপালের দরিদ্র মানুষ দুমূর্ল্যরে বাজারেও ডেঙ্গুর আতঙ্কে কয়েলের পেছনেই প্রতি মাসে কয়েকশ’ করে টাকা ব্যয় করছে আর নিজের দুর্দশাগ্রস্ত ভাগ্যের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে শাপশাপান্ত করছে।
এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন- সম্প্রতি মফস্বল শহরের স্নাতকপড়ুয়া এক তরুণ ব্যাংক থেকে শিল্প কাজে লাগানোর কথা বলে ৪০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আলুর বাজারে সিন্ডিকেট করে কয়েক মাসের মধ্যে ৭০-৮০ লাখ টাকা মুনাফার লক্ষ্যের কথা স্বীকার করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মজুতদারির অভিযোগে জেলে গেছেন। আলুর সিন্ডিকেটের এই অবস্থা দেখে বোকা জনগণ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার বিশাল জয়লাভের আনন্দ নিয়ে বাজারে আলু কিনতে গেছে তখন সে বুঝেছে সর্বাবস্থায় অর্থলাভ ও প্রবৃদ্ধির উপাসনা করা পুঁজিপতি ব্যক্তি আর রাষ্ট্র আসলে তাকে নিত্যই ‘উজবুক’ বানাচ্ছে। তা না হলে ১২-১৩ টাকা উৎপাদন খরচের ১ কেজি আলু কিনতে তাকে ৪০-৫০ টাকা কেন গুনতে হচ্ছে!
এমন এক প্রেক্ষাপটের মধ্যেও এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, কোভিড ১৯ ভাইরাসের অভিঘাত ও ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও ভূ-রাজনৈতিক পালাবদলের কঠিন এই সময়ে এককালের ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বাংলাদেশ এখনো বেঁচেবর্তে ভালোই আছে। অনেক দেশের তুলনায় অর্থনীতিতে ভালো করছে। তবে এই বেঁচেবর্তে ভালো থাকাকে বেহেশতে বাস করা কিংবা না খেয়ে কেউ মারা যাচ্ছে কি না, কারও গায়ে জামাকাপড় থাকছে কি না অথবা সবার হাতে স্মার্টফোন আছে কি না, কেউ অর্থনীতি বোঝেন না ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে ‘ধ্রুব সত্য’ বলে চালিয়ে দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে উপহাস করা হয়। দেশে নিত্যপণ্যের দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত।
গত আগস্টে সরকারি হিসাবেই (বিবিএস) তো খাদ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ব্যবসায়ী শ্রেণির অতিমুনাফার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ নিজেকে এখন স্রেফ ‘অবলা জীব’ মনে করছে। কারণ, তাদের কাছে প্রকৃত মূল্যস্ফীতির চাপ আরও অনেক বেশি। প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সারিতে প্রতিদিন নতুন নতুন পরিবারের আবির্ভাব ঘটছে। শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী অনানুষ্ঠানিক খাতের দরিদ্র-শ্রমজীবী মানুষের কাছে পুষ্টি বলতে এখন আছে বড়জোর একটি ডিম। কান পাতলে শোনা যায় এই শ্রেণির মানুষের অধিকাংশের পাতে পাঁচ-ছয় মাসে এক-দুই টুকরো গরুর মাংসই উৎসবের আমেজ বয়ে আনছে।
স্বল্প আয়ের মানুষের আলু-পেঁয়াজ কিনতে কড়াইয়ের তেল শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই মানুষদের মনে জীবনের ঘানি টানতে টানতে কখনো প্রশ্ন জাগার সুযোগই হয় না যে, একচেটিয়া বড় ঋণগ্রহীতারা প্রকৃত অর্থে তেমন কিছুই কেন বন্ধক দেন না! বিপুল ঋণের বিপরীতে কোলেটারাল বা বন্ধক হিসেবে ব্যাংককে তারা কী জমা দিয়ে থাকেন? কিভাবে তারা বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে ‘করপোরেট গ্যারান্টি’ নামক মূল্যহীন একটি কাগজের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে নিচ্ছেন? তারপর কিভাবে তারা ঋণের টাকা ছয়Ñনয় করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যূনতম পুষ্টির সুযোগটুকু কেড়ে নিচ্ছেন? আর কেনইবা দরিদ্র মানুষের শ্রেণিভুক্ত হয়েও ব্যাংকে রক্ষিত সামান্য সঞ্চয়টুকু ভেঙে তাকে নিত্যদিনের চাহিদা সামাল দিতে হচ্ছে?
সবশেষে ধারকর্য করে সুদিনের আশায় জীবনের ঘানিটা কোনোমতে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে? এসব ভাবতে ভাবতে চলতি পথে আপন মনেই প্রশ্ন জাগে, এই যদি বাংলাদেশের নাগরিকদের বেহেশতের সুখ হয় তা হলে আর পাপপুণ্যের কি মূল্য থাকে? এই অবস্থা দিয়ে আমরা কিভাবে এক দশকের মধ্যে দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠাব? দুই দশকের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিক হব? এসব ভাবতেও এখন সংকোচ লাগে, পাছে না আবার কেউ নৈরাশ্য আর আশঙ্কাবাদীর তকমা লাগিয়ে দেয়।
মুক্তবাজারের বিশ্বরাজত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এক প্রান্তের বৈশ্বিক সংকটের ঢেউ আমাদের অর্থনীতির ওপরেও এসে পড়ছে। মুক্তবাজারের মাঠে খেলতে গেলে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে কি মাঠ এবড়োখেবড়ো বলে সব দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হবে? রাজস্ব আয়, ব্যাংকিং খাতের অরাজকতা, অর্থ পাচার, কালো টাকা দুর্নীতির বিস্তার আর বাজার ব্যবস্থার নৈরাজ্য ঠেকানোর ব্যর্থতার দায় তো বিশ্ব অর্থনীতির ওপর চাপিয়ে দিলে চলে না। ধীরে চলো নীতি, দেখি না কী হয়, কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে মনোভাব নিয়ে জনগণের ওপর একসঙ্গে বিশাল অঙ্কের মূল্যস্ফীতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার দায় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর ওপর চালিয়ে দেওয়া সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয় না।
অস্বীকার বা ডিনায়াল সিনড্রমে ভোগা নীতিনির্ধারকদের নানা মুনির নানা মতের মতো বৈপরীত্যে ভরা বক্তব্যে জনমনে যে সংশয়, উৎকণ্ঠা, ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় তা মুক্তবাজারের রেফারিদের (বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ) বলে দেওয়ার দায়িত্ব নয়। অর্থনীতিবদরা হয়তো টক শো ও গোলটেবিল মাতিয়ে, বক্তব্য-বিবৃতিবাজি করে জনমনের শঙ্কাকে আরও উস্কে দিয়েছেন। তাই বলে কি ‘অর্থনীতি বোঝেন না’ বলে সবাইকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে হবে? যদি তা-ই হয় তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন কেন বলছে, ‘দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তাই আমরা অর্থনীতির অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখান থেকে পরামর্শ আসবে, সে অনুযায়ী আগামী মুদ্রানীতি করা হবে।’
রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি নিয়ে আগেও তো অর্থনীতিবিদসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু রাখা হয়েছে শুধু ব্যবসায়ীদের কথা। ব্যবসায়ীরা তাই সর্বদাই আমাদের নীতিনির্ধারকদের গুণগান গেয়ে গেছেন। সরকারের অনেক ভালো অর্জন ও সাফল্য সদা মুনাফায় বিশ্বাসী এই গোষ্ঠীর কারণেই যে জনগণের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে তা এখন নীতিনির্ধারকদের কিছুটা বোঝা উচিত।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির আরাধনা করা নীতিনির্ধারকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, প্রবৃদ্ধি আর সবকিছু বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো দারিদ্র্য হ্রাস, বৈষম্য-অসমতা হ্রাস, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তাই যদি হতো তাহলে কেন নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় খোলাবাজারে (ওএমএস) চাল ও আটা এবং ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য কিনতে স্বল্প আয়ের মানুষের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে? কেন দরিদ্র রিক্সাচলককে বলতে শুনি ‘রিক্সা চালানো খুবই কষ্টের। সামান্য দানাপানি পেটে নিয়া রিক্সা চালাইয়া কয়েক মাসেই শরীর ভাইঙা যায়, বুড়া হওয়ার আগেই সব শক্তি চইলা যায়।
কিন্তু কি করমু, উপায় তো নাই। যেমনে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সংসার চালামু কেমনে? প্যাসেঞ্জারের কাছে বাড়তি ভাড়া চাইলে ‘কুত্তার মতো’ ঘেউ কইরা ওঠে। কিন্তু তারাইবা দেবে কেমনে? তাগো আয় কি বাড়ছে? কি যে অবস্থা স্যার।’ এই অবস্থায় বলতেই হয়, আমাদের চোখের সামনেই সমগ্র বিশ^ এখন এক মহাবিপর্যয়কাল অতিক্রম করছে। ভাইরাস উদ্ভূত মহামারির অভিঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বক্ষমতার ভরকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে শক্তিশালী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে আজ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই বিপর্যয়কালের শেষ কোথায়, শেষ হবে কিভাবে, তারপরে কী হবে, আমরা কেউই তা জানি না।
এই অবস্থায় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ১৮ কোটি মানুষের এই দেশকে ভালো রাখা সকলেরই দায়িত্ব। কে ভালো, কে মন্দ, কে কী করেছে এসব কথা ভুলে একসঙ্গে কাজ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। কারণ, দিনশেষে গুটিকয়েক বিদেশপ্রেমী মানুষ ছাড়া আমাদের সবাইকে তো দেশেই থাকতে হবে। এখানেই তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় হবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি