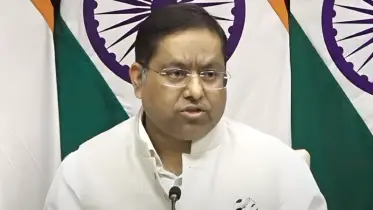ছবি: সংগৃহীত।
বাংলা নববর্ষ মানেই যেন পান্তা-ইলিশ। নববর্ষের প্রথম দিনে মাটির সানকিতে করে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার রেওয়াজ অনেকের কাছে এখন বাঙালিয়ানার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। যদিও এই ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন নয়, তবুও তা দ্রুতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে শহর থেকে গ্রামবাংলা পর্যন্ত।
বাঙালির পান্তাভাত খাওয়ার ইতিহাস কত বছর পুরনো, তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গলে পান্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের ‘কালকেতুর ভোজন’ অংশে উল্লেখ রয়েছে, “এক শ্বাসে সাত হাড়ি আমানি উজাড়ে”—যেখানে ‘আমানি’ শব্দটি পান্তার জলীয় অংশ নির্দেশ করে।
বাংলা নববর্ষে ‘আমানি’ ছিল অন্যতম প্রাচীন কৃষকীয় আয়োজন। চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় অপরিপক্ক চাল পানিতে ভিজিয়ে আমপাতা বসিয়ে রাখা হতো হাঁড়িতে। নববর্ষের সকালে সেই পানি দিয়ে ঘর ঝাড়ু দেওয়া হতো, এবং পরে সেই পান্তা ভাত পরিবারের সদস্যরা খেতেন।
পান্তাভাত মূলত সহজলভ্য কৃষকীয় খাবার। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে এটি বাঙালির প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় ছিল। গ্রামের মানুষ সাধারণত পান্তা খেতেন নুন, কাঁচা লঙ্কা, কিংবা পেঁয়াজ সহযোগে। দরিদ্র কৃষকেরা মাটির পাত্রের পরিবর্তে কচুপাতা বা কলাপাতা ব্যবহার করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, “আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত”—যেখানে ‘মান’ মানকচুর পাতা বোঝায়।
কালের বিবর্তনে পান্তার সঙ্গে যুক্ত হয় আলু ভর্তা, পোড়া বেগুন এবং সহজলভ্য মাছ যেমন পুঁটি, কৈ, টাকি, ট্যাংরা ইত্যাদি। তবে ইলিশের স্থান ছিল ভিন্ন। ইলিশের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় এটি সাধারণত গরম ভাতের সঙ্গে খাওয়া হতো। শহরের বিত্তবানদের হেঁশেলে পান্তাকে গরিবের খাবার বলেই গণ্য করা হতো।
তবে আশির দশকে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পান্তা-ইলিশের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৮০/৮১ সালে সাংবাদিক বোরহানউদ্দিন আহমেদ প্রথমবারের মতো নববর্ষে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার ধারণা দেন। বন্ধুদের চাঁদা তুলে আয়োজন করা হয় পান্তা-ইলিশের।
পরের বছর গীতিকার শহিদুল হক খান রমনায় পান্তা-ইলিশের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করেন ও পোস্টার ছাপিয়ে তা জনপ্রিয় করে তোলেন। এরপর থেকে নববর্ষে রমনায় পান্তা-ইলিশ আয়োজন শহুরে সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পান্তা-ইলিশ বিক্রি করে বাড়তি আয়ের পথও তৈরি করেন।
আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পান্তা-ইলিশ সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নব্বইয়ের দশকে এ খাবার হয়ে ওঠে নববর্ষ উদযাপনের প্রধান অনুষঙ্গ। ঢাকা ছাড়িয়ে বিভাগীয় শহর, এমনকি জেলা শহরের অলিগলিতে পান্তা-ইলিশ বিক্রি হতে থাকে নববর্ষে।
তবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইলিশের চাহিদা বাড়ে। যার ফলে শুরু হয় জাটকা নিধন। সরকার বাধ্য হয় মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করতে। এই সময়ে পদ্মা, মেঘনা, কালাবদর, তেঁতুলিয়াসহ পাঁচটি নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকে।
যদিও নিষেধাজ্ঞা চলাকালেও ব্যবসায়ীরা মাঘ মাস থেকেই হিমাগারে ইলিশ সংরক্ষণ শুরু করেন। ফলে নববর্ষে শহুরে পান্তা-ইলিশ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। এই অবস্থায় পান্তা-ইলিশ যতটা না সংস্কৃতির দাবিদার, তার চেয়েও বেশি হয়ে ওঠে ব্যবসায়িক সফলতার দৃষ্টান্ত।
তবে পান্তা ভাত বরাবরই ছিল বাঙালির নিত্যদিনের খাবার। নববর্ষের দিনে ভালো খাবারের আয়োজনের রীতি বহু পুরনো। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ‘শাকান্ন’ খাওয়ার রেওয়াজ এখনো বহু পরিবারে রয়েছে। সেই দিন বউ-ঝিরা বাড়ির আশেপাশের অনাবাদী জায়গা থেকে তোলা শাক দিয়ে রান্না করতেন চৌদ্দ পদের শাকান্ন, যেখানে মাছ-মাংস রান্না নিষিদ্ধ থাকত।
অর্থাৎ, পান্তা-ইলিশের আধুনিকতর সংস্করণ যতটা শহুরে জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক কৌশলের ফল, ততটাই তার মূল শিকড় রয়েছে কৃষিপ্রধান বাঙালির জীবনে।
সায়মা ইসলাম