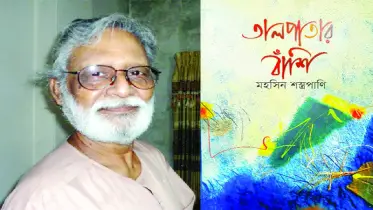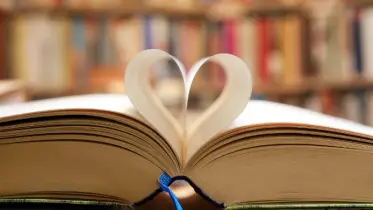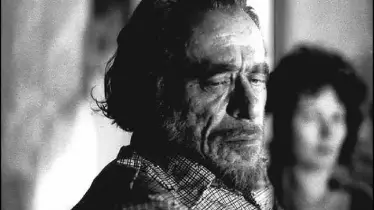বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরেই হয়ে আসছে। যেমন আধুনিক উপন্যাসে, নাটকে নির্বাচিত অঞ্চলের বিশিষ্টতা তুলে ধরার জন্য, ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিক চরিত্র উপস্থাপন করার জন্য আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর বাংলা কবিতায় প্রাচীন সময় থেকেই লোকজীবনের কথা আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপিত। যেমন, বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থিরা যেদিন লোকসমাজের কাছে তথাগতের বাণী ও সাধনপ্রণালীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লোকসাধারণের ভাষায় নির্মাণ করেছিলেন চর্যাগীতি সেদিনই রচিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার কবিতা। চর্যাপদের কবিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্গের বা অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ের মানুষ। বর্ণাশ্রম প্রথা ও অস্পৃশ্যতা উৎকটভাবে বিদ্যমান থাকায় অভিজাত শ্রেণির ঘৃণা ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছিলেন তারা। এই অবজ্ঞা ও ঘৃণার কারণে তারা উচ্চবর্গের অভিজাতদেব ভাষাকে (সংস্কৃত ভাষা) বর্জন করে লোকসাধারণের অখ্যাত ভাষাকে তুলে ধরেছিলেন। চর্যাপদের অন্যতম একজন কবি কাহ্নপার একটি পদ থেকে জানা যায় সে-যুগে অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা উচ্চবর্ণ ও ধনিক শ্রেণি অধ্যুষিত নগরে বসবাস করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কাহ্নপা লিখেছেন,
‘নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহারি কুড়িআ
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ ॥’
চর্যাযুগের এইসব তথাকথিত নিম্নবর্গ ও অন্ত্যজ শ্রেণির কবিরা সেদিন উচ্চবর্গের দেবভাষার অভিজাত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে না এলে আমরা আমাদের বহুসাধের বাংলা ভাষাকে খুঁজে পেতাম না, পেতাম না আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যময় সম্ভার।
মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দী অবধি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের মতন মঙ্গলকাব্যগুলিতে বা তারও আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও বৈষ্ণবপদাবলীতে এবং পরবর্তীকালের চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে লোকসাধারণের চালচিত্র তাদের ভাষাবোধের গভীর ব্যঞ্জনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে দেবতা-মাহাত্ম্য ও দেবকল্পের আশ্রয়ে কবিতার নির্ভার সত্তাকে প্রাণবন্ত করেছে।
মঙ্গলকাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার মতন অন্ত্যজ মানুষজনের সুখদুঃখ মাখা জীবনের জলছবিতে লোকমানুষের অবদমিত ধর্মীয় চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে; যা মধ্য যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমালোচকদের কাছে চিহ্নিত।
মধ্যযুগের দৈবী পরিমণ্ডলের কাব্যসাহিত্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আরাকান রাজসভার কবি দৌলতকাজীর দসতী ময়নামতী’ বা ‘লোরচন্দ্রাণী’ এবং সৈয়দ আলাওলের দপদ্মাবতী’। মানবতাবাদের মহিমায় উজ্জ্বল এই কাব্য লোকজীবনের সংস্কৃতি ও ভাষা প্রয়োগে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। দেবদেবীর মাহাত্ম্য রচনার মধ্যযুগীয় বৃত্তের বাইরে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন ভাবচেতনায় নির্মিত হয় এই লোকজীবনের আখ্যান।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর দঅন্নদামঙ্গল’-এ দৈবী চরিত্রের লোকায়ত রূপ ফুটিয়ে তোলেন লোকভাষার ব্যবহারে। অন্নদামঙ্গলে লোকসাধারণের প্রতিনিধি ঈশ্বরী পাটনীর লোককণ্ঠে সাধারণ মানুষের চিরায়ত আর্তির কথা নিবেদিত হয়েছে দেবী অন্নদার কাছে, আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’। লোককণ্ঠে আধুনিক বাংলা ভাষা নির্মিতর প্রথম প্রয়াস বলা যায় যাকে।
এরপর শুরু হলো বাংলা আধুনিক কবিতার যুগ। ইউরোপীয় রোমান্টিকতার আবেগ ও নবজাগরণের প্রভাবে নতুন ধারার কাব্যরীতি এবং কাব্যচর্চার অঙ্গন থেকে বহুদূরে সরে গেলেন বাংলার প্রান্তিক মানুষেরা।
এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা লোকমানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ‘ঐকতান’ জানান:
‘কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/ কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,/ যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।/ সাহিত্যের আনন্দের ভোজে/ নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।/ সেটা সত্য হোক,/ শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।/ সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি/ ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।’
উল্লেখ্য, এই ব্যাকুল আততি রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের স্পর্শ করেনি। ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ব্যক্তিসত্তার একাকিত্বের বলয়ের বাইরে তারা বেরুতে চাইলেন না। তবে বিষ্ণু দে সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেছেন। লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একদা ‘নববাবুভাষা’ ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি: ‘রেখো না বিলাসী কোনো আশা, নববাবু ভাষা ছাড়ো মন.. গ্রামে ও শহরে পাবে কবিতার ভাষা।’
ত্রিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার সৌরভ বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছেন কবি জসীমউদ্দীন। তাঁর কবিতায় লোকজীবন ও সংস্কৃতি নিবিড় পরিচর্যায় আবহমানকালের ঐতিহ্যের নান্দনিক ভিত নিয়ে উপস্থিত। কবিতায় পরিবেশ ও সমাজচিত্র সাবলীল লোকশব্দের গাঁথুনির ভেতর সাধুরীতির কাঠামো অনুসৃত আধুনিক কথ্যরীতির নতুন একটি ধারা নির্মাণ করেছে। জসীমউদ্দীন যেন রবীন্দ্রনাথের ঐক্যতান’ কবিতার’ আর্তি শুনেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানের উত্তরে তিনি জানান:
“অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে
এদেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান
পেতে রহি কভু শোনা যায় যদি কি কহে মাটির প্রাণ” ।
বলা যেতে পারে, তাঁর মতন বাংলার লোকজীবনে অন্বেষণের দৃষ্টি ফেলে এতো গভীরভাবে লোকমানুষ ও প্রকৃতির প্রাণের কথা শুনতে পাননি কল্লোলের নাগরিক কবিরা। মানুষ ও প্রকৃতির অভেদাত্মক সম্পর্কের এমন সব লাইন উঠে এসেছে তার কবিতায় যার কথা কল্লোলের অন্য কবিরা কল্পনাও করতে পারতেন না। যেমন দরাখাল ছেলে’ কবিতায় তিনি লেখেন:
“রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথায় ধাও,
পূব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।’
‘ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া ভাই,
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু-খান পা,
বলছে ডেকে, ‘গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!’
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে ভাই!
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই!”
লক্ষণীয় লোকবাংলার এই অনুষঙ্গ, এই রূপকল্প বাংলা কবিতায় ইতোপূর্বে আসেনি কখনও। মটরশুঁটি গাঁয়ের রাখালের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে তাকে খেলতে ডাকছে; প্রকৃতি ও মানুষের এমন বন্ধনের সূত্র কল্লোল যুগের আধুনিক কবিদের মনোজগতের বাইরের বিষয়।
দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় মনীশ ঘটক, অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, অনিল বরণ দত্ত, অমল ত্রিবেদী, অসিত কুমার মাজী, সৌমিত্র ব্যানার্জ্জী, সুনীতি গাঁতাইত, রাজারাম, রামকৃষ্ণ দত্ত, তুষার দত্ত, উদয়ন হাজরা, দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, ভবতোষ শতপথী, দেবব্রত সিংহ প্রমুখের হাতে আঞ্চলিক ভাষার চর্চা ও বিকাশ হতে দেখা গেছে। আর পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের কবিতায় লোকজীবন ও সংস্কৃতির সৃজনশীল ধারার বিকাশ ঘটেছে আল মাহমুদের কবিতায়। আঞ্চলিক শব্দকে কাব্যিক দ্যোতনায় আধুনিক মননদীপ্ত বোধে সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছেন। দৃষ্টান্ত:
“ঘুরিয়ে গলার বাঁক ওঠো বুনো হংসিনী আমার
পালক উদাম করে দাও উষ্ণ অঙ্গের আরাম,
নিসর্গ নমিত করে যায় দিন, পুলকের দ্বার
মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।
কক্কর শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ
আঠারোটি ডাক দেয় কান পেতে শোনো অষ্টাদশী,
আঙুলে লুলিত করো বন্ধবেণী, সাপিনী বিশেষ
সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।
ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দুটি জলের আওয়াজে-
তুলে মিশে যাই চলো আকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়।”
(সোনালি কাবিন: ৩ সংখ্যক সনেট)
শামসুর রাহমানও তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন; বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার লোকসংস্কৃতি, জীবন ও ভাষার নিপুণ প্রয়োগ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। দৃষ্টান্ত:
“আমার গলায় কার গীত হুনি ঠাণ্ডা আঁসুভরা?
আসলে কেউগা আমি? কোন্হানতে আইছি হালায়
দাগাবাজ দুনিয়ায়? কৈবা যামু আখেরে ওস্তাদ?
চুড়িহাট্টা, চান খাঁর পুল, চকবাজার, আশক
জমাদার লেইন, বংশাল; যেহানেই মকানের
ঠিকানা থাউক, আমি হেই একই মানু, গোলগাল
মাথায় বাবরি; থুতনিতে ফুদ্দি দাড়ি, গালে দাগ,
যেমুন আধলি একখান খুব দূর জামানার।”
(এই মাতোয়ারা রাইত)
সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার নান্দনিক সৌন্দর্য রাজনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষায় উপস্থিত। দৃষ্টান্ত:
“জামার ভিতর থিকা যাদুমন্ত্রে বারায় ডাহুক,
চুলের ভিতর থিকা আকবর বাদশার মোহর,
মানুষ বেকুব চুপ, হাটবারে সকলে দেখুক
কেমন মোচড় দিয়া টাকা নিয়া যায় বাজিকর।
চক্ষের ভিতর থিকা সোহাগের পাখিরে উড়াও,
বুকের ভিতর থিকা পিরীতের পূর্ণিমার চান,
নিজেই তাজ্জব তুমিÑ একদিকে যাইবার চাও
অথচ আরেক দিকে খুব জোরে দেয় কেউ টান।
সে তোমার পাওনার এতটুকু পরোয়া করে না,
খেলা যে দেখায় তার দ্যাখানের ইচ্ছায় দেখায়,
ডাহুক উড়ায়া দিয়া তারপর আবার ধরে না,
সোনার মোহর তার পড়া থাকে পথের ধুলায়।
এ বড় দারুণ বাজি, তারে কই বড় বাজিকর
যে তার রুমাল নাড়ে পরানের গহীন ভিতর।”
(পরানের গহীন ভিতর: ১)
কবিতায় আঞ্চলিক ভাষা ও এর প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কবি ওমর আলী, মোহাম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজল শাহনেওয়াজ, কফিল আহমেদ প্রমুখ।
বর্তমানে বাংলা কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ উত্তরাধুনিক শিল্পকাঠামোর একটি রীতি হিসেবে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আঞ্চলিক ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রমিত ভাষাকাঠামোয় নিজের অবস্থান করে নিয়ে বাংলা কবিদের হাতে কবিতার শরীরে অলংকার হয়ে উঠছে। বাঙালি মানুষের জীবনযাপন, তার ধরনে নিত্য পরিবর্তন, কতো নতুন জিনিসের আবিষ্কার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি প্রতিনিয়ত শব্দভাণ্ডারে নতুন নতুন শব্দ সংযোগ করে চলেছে। মানুষ তার জীবনযাপনে এই পরিবর্তনগুলিকে যেমন আপন করে নিচ্ছে, ভাষাও তেমন এই পরিবর্তনগুলির সূত্র ধরে নিত্যনতুন সাজে সেজে উঠছে। ফলে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাও নতুন রূপ পরিগ্রহ করে বাংলা কবিতায় ভিন্ন মাত্রার যোগ ঘটাচ্ছে।
এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার একটি ধর্ম হলো প্রতি দশ কিমি অন্তর ভাষার যে কথ্য রূপ তা পরিবর্তিত হয়ে চলে। তার সঙ্গে রয়েছে নানা ভৌগোলিক অঞ্চলের, তার নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত কিছু শব্দভাণ্ডারের ঐতিহ্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ভাষার এই বহু বিচিত্রতা এবং নিত্য পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলে। এর মধ্যে দিয়ে ভাষা জীবন্ত থাকে। ভাষার যেরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, তা বেঁচে থাকে সেই রূপকে সাহিত্যে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এজন্যই সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কাক্সিক্ষত। এই ধরনের রচনায় শব্দ চয়ন ও শব্দ প্রয়োগ, আঙ্গিকের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষ করে কবিতায় ভাবগত দিক, রূপগত নির্মিতির দিকেও আঞ্চলিক ভাষার তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে, যেমন বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি লালমাটির দেশের ভাষা, মালদা দিনাজপুর অঞ্চলের ভাষা, রংপুর, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের ভাষা, খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চলের ভাষা, যশোর, কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভাষা, ফরিদপুর, বরিশালের ভাষা, পাবনা, সিরাজগঞ্জের ভাষা, বগুড়া, গাইবান্ধার ভাষা, নওগাঁ, জয়পুরহাটের ভাষা, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষা, নরসিংদী, কুমিল্লার ভাষা, নোয়াখালীর ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষা, সিলেটের ভাষা, বিক্রমপুর অঞ্চলের ভাষা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের ভাষা, ঢাকাইয়া ভাষা— প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব আকর্ষণ আছে।
এইসব ভাষায় রূপবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আঞ্চলিক কবিতার জনপ্রিয় ঐতিহ্যও রয়েছে।
মূলত কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতার আরও খাঁটি এবং সূক্ষ্ম প্রকাশের সুযোগ করে দেয়, কাব্যিক ভূদৃশ্যকে সমৃদ্ধ করে এবং ভাষা, মানুষ এবং ভূমির মধ্যে গভীর সংযোগ গড়ে তোলে।
আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা এবং স্থানীয় ভাষাগুলি বিশ্বের সাহিত্য পরিমণ্ডলের উপর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং তার জনগণের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।
যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধ মৌখিক ঐতিহ্য রক্ষায় কবিতা সংরক্ষক ও সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে।
কথ্য শব্দ কবিতায় বহুভাষিক মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে একটা প্রমিত প্রত্যয়ে পরিণত হবার সম্ভাবনা জাগায়।
কবিতা আঞ্চলিক ভাষার গঠন এবং শব্দভাণ্ডার প্রকাশে বৈভব, নমনীয়তা এবং সূক্ষ্মতা প্রদান করে থাকে,যা জাতীয় সাহিত্যের আঙ্গিককে বিস্তৃত করে।
মূলত আঞ্চলিক ভাষার কবিতা বাংলা অঞ্চলের নিজস্ব পরিচয়, স্বত্ব এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে মূল দায়িত্ব পালন করে বাঙালি সংস্কৃতির অন্বেষণ প্রবাহিত রেখেছে; সেই সঙ্গে বাঙালির আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্র্যময় সাহিত্য পরিমণ্ডল বিনির্মাণে ভূমিকা রেখে চলেছে।
প্যানেল