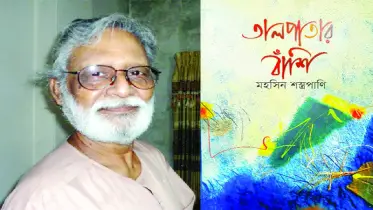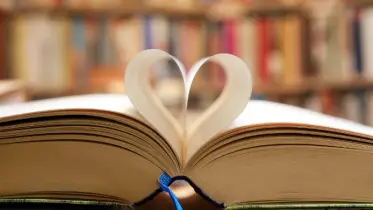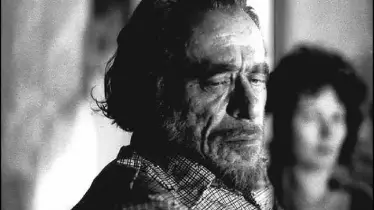‘আজ আপনাদের বারোয়ারী সভায় আমার ‘নন্দিনী’র পালা অভিনয়’-এভাবেই রক্তকরবী নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে উপস্থাপন করেছিলেন। আর বলেছিলেন ‘আমার এই পালাটি যাঁরা শ্রদ্ধা ক’রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক’। রক্তকরবী নাটকটিকে কেন তিনি শুধু ‘পালা’ বলে অভিহিত করেছিলেন সে প্রশ্ন অনেক বিদ্বজ্জনকেই ভাবিয়েছে। কিন্তু একটি নাটক শতবছর অতিক্রম করলেও আলোচনা-সমালোচনার জায়গা থেকে যে একটুও সরে যায়নি কিংবা উৎকর্ষতা ও মনোযোগ কোনটাই হারায়নি, এই বাস্তবতায় রক্তকরবী আজও প্রাসঙ্গিক। খুব সরলভাবে নাটকের ভাব ও বিষয়বস্তু যে সাধারণের জন্য একান্ত সহজবোধ্য, এখানে বিষয়টি তেমন নয়। এই নাটকটির প্রহেলিকা আচ্ছন্ন ভাবের আড়ালে এক চিরন্তন সত্য লুকিয়ে আছে। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন ‘যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃদপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে তার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে’। তিনি আরও লিখছেন ‘এইটি মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি’। নাটকের শেষটা যখন সংকীর্ণতার অন্ধকার থেকে ‘আচমকা আলোয়’ ভরে উঠে, সেই মুক্ত আলোকশিখা হাতে করেই এসেছিল নন্দিনী। কাজেই নাটকের শুরু থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে অন্যন্য চরিত্র, কাহিনী-সংলাপ, আর নাটকের ভাবটুকুও এগিয়ে নেয়ার সূত্রধর সে যেন একাই নন্দিনী। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তকরবী নাটকের আলোচনায় ‘রবি-রশ্মি’ গ্রন্থে লিখছেন ‘নন্দিনী জীবন-শ্রী প্রেম-কল্যাণময়ী-লক্ষ্মী লোভীকে সে লোভ ভোলায়, পণ্ডিতকে তাহার পান্ডিত্য ভোলায়। যে নারী সর্ম্পূণতার আদর্শকে পরিব্যক্ত করে, সে সকলের মধ্যকার সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, প্রকাশ করে’। প্রাণের স্বাধীন সত্তা, মুক্তচিন্তা ও বন্ধনমুক্তি মানুষের চির আরাধ্য, সে সত্য ও সুন্দরের পূজারী, সংকীর্ণতা ও জড়ের বিরুদ্ধে চৈতন্যের বিজয়, এই চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক নন্দিনী। প্রেক্ষাপট একটি কাল্পনিক রাজ্য তার নাম যক্ষপুরী। এখানে স্বভাবতই একজন রাজা আছেন। যার নাম মকররাজ। তিনি তার রাজমহলের অর্গল বন্ধ করে রাখেন। বাইরের দেয়ালে একটিমাত্র জালে আচ্ছাদিত জানালা দিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছে বা প্রয়োজনমতো প্রজাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। পৌরাণিক ভাবনার যক্ষরাজ কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন আর তার বিপুল ঐশ^র্যমন্ডিত পাতালপুরী এটা নয়। তবে এখানে মাটির নিচে সোনার খনি। সেখানে তাল তাল সোনা সঞ্চিত আছে। তারই সন্ধান পেয়ে সুড়ঙ্গ কেটে সেই সোনা আহরণ করে চলেছে একদল পরিশ্রমী মজুর। নাটকে যাদের বলা হচ্ছে ‘খোদাইকর’। কিশোর, গোকুল, ফাগুলাল, বিশু এরাই রাতদিন খনি থেকে সোনা তুলে আনে। খোদাইকরেরা সারাদিন মদের নেশায় চুড় হয়ে থাকে। যক্ষপুরীতে মুনাফা অর্জনই যেন তাদের একমাত্র লক্ষ্য। দয়া-মায়া মানবিকতা এখানে উপেক্ষিত। রাজা প্রজাদের শোষণ করছে আর রাজভান্ডার সমৃদ্ধ করতে খনি-মজুরেরা যন্ত্রের মত সোনা তুলে চলেছে। এরাই উনিশ-বিশ শতকের শিল্পায়ন আর নগরায়নের দাপটে ভূমি আর কৃষিজীবন থেকে উৎপাটিত কৃষককূল কিংবা কৃষিমজুর। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা, দ্বেষহিংসা, বিলাসবিভ্রম, সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মত’। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন ‘কর্ষণজীবী আর আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে’। আবার বলছেন ‘কৃষি দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষিরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন’। কর্ষণজীবী সেই উৎপাদক শ্রেণী যাদের শ্রমে-ঘামে সৃষ্টি হয় সম্পদ আর আকর্ষণ-জীবী তারাই যারা এই শ্রমের ’উদ্বৃত্ত মূল্যে’ ভাগ বসিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। শিক্ষা, মুক্তচিন্তা আর মানবিক জীবনবোধের যে সংস্কৃতি তার বিকাশের পথ তো সেখানে রূদ্ধ থাকবেই। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘আমার নাটকও একইকালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণির’। শাশ^তকালের শ্রেণি বিভাজিত সমাজের এই অনিবার্য দ্বন্দ্বটিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। খনি মজুর ছাড়াও আছে ‘সর্দার’, তারা বহুদর্শী এরাই রাজার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এদের পরিকল্পনা আর তত্ত্বাবধানে খনি মজুরদের কাজে ফাঁক পড়বার কোন সুযোগ নেই। তাদের কারণেই রাজভান্ডার সম্পদে স্ফীত হতে থাকে। আর আছে ‘মোড়ল’ যারা একসময় খোদাইকর ছিল। যোগ্যতাগুণে তারা আজ মোড়লের পদলাভ করেছে। এরা কখনো কখনো কর্মকুশলতায় সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। রাজার অন্যায় কাজের ভার মূলত মোড়লদের হাতেই। পারিষদ আর আমলাদের চিরন্তন শীতলযুদ্ধ নাট্যভাবনায় উপেক্ষিত হয়নি।
নাটকের একটি চরিত্র ‘গোঁসাইজি’। বলা হয়েছে ‘তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের’। যখনই মজুরেরা সর্দারদের কথার অবাধ্য হয় তখনই গোঁসাইকে পাঠানো হয় সেখানে তাদের ধর্মকথা শোনাবার জন্য। যেখানে গোঁসাই তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না তখন সর্দারকে বলে সে পাড়ায় আরও কিছুদিন রাজার ফৌজ রেখে দিতে, ‘ফৌজের চাপে অহংকারটা দমন হয় তারপর আমাদের পালা’। খোদাইকর ফাগুলাল, সর্দারের উপস্থিতিতে গোঁসাইকে উদ্দেশ্য করে বলে ‘প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইবো না’। চিরকাল পুরোহিত শ্রেণি ধর্ম দিয়ে সাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। প্রজাশোষণের হাতিয়ার হয়েছে। রবীন্দ্রভাবনায় এই নাটকে তা ঠিকই ধরা দিয়েছে। এই নাটকে একটি গৌণ চরিত্র অধ্যাপক, তত্বকথার আড়ালে যিনি রাজার সৃষ্ট ব্যবস্থা ও যক্ষপুরীর নিয়মের কাছে বাঁধা পড়ে রয়েছেন। অধ্যাপক নন্দিনীকে বলছে ‘আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; আবার নন্দিনী অধ্যাপককে বলছেন তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুড়েই চলেছ’। কিশোর নন্দিনীকে ভালোবাসে তাই অনেক অত্যাচার আর মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে নন্দিনীর জন্য খুঁজে আনে রক্তকরবী। কিশোর বলেছিল ‘একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী’। ফাগুলাল একজন খোদাইকর। ছুটির দিনে সে মদ চায়, তার স্ত্রী চন্দ্রা বলে গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটির দিনটা তো তুমি এভাবে কাটাতে না। ফাগুলাল বলে বনের পাখি ছাড়া পেলে উড়তে চাইবে কিন্তু খাঁচায় বাঁধা পাখি খাঁচার মধ্যে ছাড়া পেলে সে মাথা ঠুকে মরে। চন্দ্রা তাকে গ্রামে ফিরে যেতে বললে ফাগুলাল বলে ‘ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি’? বিশু নন্দিনীকে ভালোবাসে। বিশু নন্দিনীকে বলছে ‘তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দ্যুতি। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে’ নন্দিনীকে নিজের করে না পেয়ে সে একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলো যক্ষপুরীতে। এখন সে গান গায়। ‘মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে /লাগল পালে নেশার হাওয়া/ পাগল পরান চলে গেয়ে’। চন্দ্রা বলে ‘তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম তোমার সেই সাধের নন্দিনী’। চন্দ্রা বিশুকেও বলে গ্রামে ফিরে যেতে। বিশু উত্তরে জানায় ‘সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে’। এভাবেই রক্তকরবীর প্রায় সব চরিত্র বাঁধা পড়ে আছে যক্ষপুরীর যান্ত্রিক জীবন আর লৌহ যবনিকার আড়ালে। রঞ্জন নন্দিনীর প্রেমাস্পদ। সে এই নাটকের প্রতিবাদী সত্বা, সে স্রোতস্বিনী নদীর মতো।
নাটকের এক পর্যায়ে প্রহরীদের হাতে বিশু বন্দী হয়। বন্দি হয় কিশোর। খনির মজুররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বন্দীশালা চুরমার করে ভেঙে ফেলতে এগিয়ে চলে কারিগরপাড়া থেকে সব মজুরেরা। এদিকে রাজাকে না জানিয়ে রঞ্জনকেও কৌশলে বন্দি করে সর্দারেরা। রক্তকরবীর রাজা চরিত্রটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন দ্বৈতসত্বা। বলছেন ‘একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে’। একই দেহে মানব ও দেব সত্বা। নন্দিনী যক্ষপুরী আসলে তার আবহ বদলে যাচ্ছে, তাই রাজা নন্দিনীর প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারেননি। আবার নন্দিনী কোনো বিদ্রোহী নারীও নয়। প্রতিশোধ পরায়ণতা নিয়ে রাজাকে জয় করার বাসনা তার ছিল না। তার হাতে ছিল মুক্তজীবনের আলোকবর্র্তিকা। নন্দিনীর যেটুকু বিদ্রোহ তা যক্ষপুরীর অচলায়তন ভেঙে মুক্ত বাতাস বইয়ে দেয়ার জন্য বিদ্রোহ। রাজা নিজেকে পাহাড়ের চূড়ার মতো নিঃসঙ্গ বলেছেন। নন্দিনীর ভালোবাসার কাছে রাজা হার মেনেছিলেন।
মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নন্দিনীর সাথে রঞ্জনের। শেষ পর্যন্ত রাজা তার প্রাসাদের দ্বার খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রঞ্জনের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে। নন্দিনীর মুখে রাজা জানলেন এই রঞ্জন। সর্দাররা রঞ্জনের পরিচয় গোপন রেখেছিল রাজার কাছে। রাজা অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন, ‘আমি যৌবনকে মেরেছি- এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে’।
ধ্বজাপূজার দণ্ড তিনি নিজ হাতে ভেঙে ফেললেন, ছিঁড়ে ফেললেন ওর কেতন। শেষতক রাজা বলছেন ‘এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?’ নন্দিনী বলছে, ‘যাব আমি’। এদিকে কুন্দফুলের মালা বর্শার আগে বেঁধে সর্দার এগিয়ে আসছে। নন্দিনী বলছে ‘ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রং করে দিয়ে যাব’। এদিকে কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে। সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, নন্দিনীর জয়!
প্যানেল