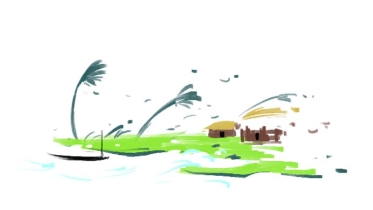চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই পদসমূহ বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান আধ্যাত্মিক সংগীত সমষ্টি। এগুলোর সঠিক বয়স আজ পর্যন্ত নিরুপন করা সম্ভব না হলেও এসব যে বাংলা সাহিত্যের আদি সম্পদ, একথা সকল ভাষা পণ্ডিতরাই স্বীকার করেছেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে এর মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপিতে এর নাম ছিল ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থটির নাম দেন ‘হাজার বছরের পুরান বাংলাভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা’। বলাবাহুল্য, এই সংগীতগুলো বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন বিধায় শাস্ত্রী মহাশয গ্রন্থখানির অনুরূপ নামকরণ করেন। পরে ডক্টর প্রমোদচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের অনুবাদের যে সংকলনটি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন, তাতে মোট ৫১টি সম্পূর্ণ পদ ছিল। এরপর আর নতুন কোনো সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় চর্যাপদের মোট সংখ্যা এটাই বলে পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছিলেন। অবশ্য অনেক পরে ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত, ডক্টর আর্নল্ড বাকে প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ আরও কিছু চর্যাপদের সন্ধান পেলেও ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ব সংগৃহীত সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় সেগুলোকে খাঁটি চর্যাপদ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি; বরং ওগুলো চর্যাপদের অনুসৃষ্ট বলে বিশ^াস করা হয়েছে।
চর্যাপদগুলো কাব্যাকারে রচিত। এগুলোর রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহ পাদ, কলম্বপাদ, চাটিলপাদ, শান্তিপাদ, লুইপাদ, শবরপাদ, গুন্ডরীপাদ, মহীধরপাদ, বীনাপাদ, আর্যদেবপাদ, ঢেন্ডনপাদ. দারিকপাদ, আড়কপাদ, ধামপাদ, তান্তীপাদ, কক্কুরীপাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পদের রচয়িতা বলে এঁদের নামের সঙ্গে ‘পাদ’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে।
আগেই বলা হয়েছে, চর্যাপদগুলো বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম সংগীত সমষ্টি। এ সব সংগীত ইহকালের সমস্যা সংকুল জীবনযাত্রা এবং তা থেকে নির্বানলাভ পূর্বক মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের আকাক্সক্ষা এবং তার উপায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, তা সরাসরিভাবে বর্ণনা না করে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমেই বলা হয়েছে। আর এই রূপক সমূহের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
চর্যাপদে তৎকালীন বাঙালিদের যাতায়াতের জন্য প্রধান বাহন হিসেবে নৌকার ব্যবহার ছিল। বহুসংখ্যক পদে নৌকার নামোল্লেখ এবং এর ব্যবহারিকতার বর্ণনা রয়েছে। অনেক সময় দূরের যাত্রাপথে উজানগুণ টেনে নিয়ে নৌকা চালানো হতো। সে সময় নৌপথে দস্যুর ভয় ছিল। এমন একটা বর্ণনা আছে নরহপাদের ৩৮ সংখ্যক পদেÑ
‘কাএ নাবড়ি খানটিমন কাড় আল।
সদগুরু বঅনে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাঙ্গ।
আল উপাএ পারদ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টানই গুণে।
মেলি মিন সহজে জানই আনত ॥
বাটত ভএ খান্ট বি বলআ।
ভব উলোলে সরবি বেড়িয়া ॥
ফুল লই ঘরএ সোন্ত উজাই
সর ভনই গঅনে সমাই ॥’
অর্থাৎ কায়ারূপ নৌকাতে মনবৈঠা ও সদগুরু বচনরূপ হাল ধরো। চিত্ত স্থির করে হাল ধরো। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যাবে না। নৌবাহী গুণে নৌকা টানে। সহজে মিলে যাও, অন্যপথে যেও না।
পথে ভয়। দস্যু বলবান। তবে সমুদ্রের উল্লাসে সবই বিনষ্ট। সরহ বরলন, কূল ধরে খরস্রোতে উজান বেয়ে চললে (নৌকা) গগণে প্রবেশ করে।
সাধারণত ডোম্বীরা কিছু পয়সার বিনিময়ে পারাপার করত। আবার অনেক সময় বিনে পয়সাতেও। পয়সা হিসেবে কড়ি, বুড়ির উল্লেখ আছে। যেমনÑ
‘কবড়ী লেই, কবড়ী নলেই
কুচ্ছেল পর করেই।’
(ডোম্বীপদ : ১৪ সংখ্যক)
অর্থাৎ ডোম্বী কড়িবুড়ি না নিয়ে স্বেচ্ছায় নৌকা পার করে দেয়।
চর্যার বিভিন্ন পদে নৌকার বিভিন্ন অংশ এবং সরঞ্জামের উল্লেখ আছে। যেমনÑ কেড় আল-দাঁড়, পতবাল-হাল, পুলিন্দা-মাস্তুন, মাঞ্জ-লুই ইত্যাদি।
অনেক ক্ষেত্রে পারাপারের মাধ্যম হিসেবে ভেলাও ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তিপাদের ১৫ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘মাআ মোহ সমুদারে অন্তন
বুঝসি যাহ্
াআগে ন বন ভেলা দীসইÑ
ভান্তি ন পুছসি নাহা ॥’
অর্থাৎ মায়ামোহ রূপ সমুদ্রের অন্ত বুঝে না, গভীরতা বুঝে না। সামনে নৌকা বা ভেলা কিছুই দেখা যাচ্ছে না।
ছোট নদী পারাপারের জন্য গাছ কেটে জোড়া দিয়ে সাঁকো তৈরি করা হতো। চাট্টিলাপাদের ৬ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘ভবনই গহন গম্ভীরে বেগে বাহি।
দু অন্তে চিখিল মাঝো থাহি ॥
ধামাথে চটি সবঙ্কম গঢ়ই ।
পারগামী লোঅ ভির তরই ॥
ফাড়ি মোহ তরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ়ি টাঙ্গি
নিবানে কোড়িঅ ॥’
অর্থাৎ গহন ও গভীর ভবনদী বেগে বয়ে যাচ্ছে। এর দুধারে কাদা, মাঝখানে থই নেই। ধর্মসাধনার জন্য সাঁকো বানালেন (যাতে) পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে পার হতে পারে। মহীতরু চিরে পাটি জোড়া দেওয়া হল।
বর্তমানের মতো প্রাচীন বাঙালি সমাজেও অতি ধুমধামের সঙ্গে বিবাহকার্য সমাধা হতো। বর ঢাক-ঢোল, কাসি-ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিয়ে বিয়ে করতে কনের বাড়িতে যেত। বিয়েতে যৌতুকপ্রথা ছিল। নববধূর বাসর যাপনের ব্যবস্থাও ছিল। কৃষ্ণপাদের ১৯ সংখ্যক পদে আমরা দেখিÑ
‘ভব নির্বানে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেনি করন্ড ফাসালো ॥
জয় জয় দুন্দহি সাছ উছলিআ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিলা ॥
ডোম্বি বিবাহিয়া আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ অনুত্তর ধাম ॥
অহনিশি ফুরআ প্রসঙ্গে জাইি।
জেইনি জালে রঅনি পোহাই ॥
ডোয়ী এর সঙ্গে জো জোই রও।
খনই দূরে ছাড়ই সহজ উন্মত্ত ॥’
অর্থাৎ ভব নির্মাণকে পটই ও মাদল, মন-পবনকে করন্ড ও ফাঁসি করা হল। দুন্দুভি শব্দে জয় জয় শব্দ উছলে উঠল। কাহ্নপাদ ডোম্বিকে বিয়ে করতে চললো। ডোম্বীকে বিয়ে করে জন্ম নাশ করল। যৌতুক হিসেবে পেল অনত্তর ধাম। দিনরাত সুরভ প্রসঙ্গে যায়। যোগিনী জালে রাত্রি পোহায়। ডোমীর সঙ্গে সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত, সে সহজও হয়ে ক্ষণমাত্রও ডোম্বীকে ছেড়ে যায় না। এপর স্বামীর সঙ্গে বধূ চলে আসতো স্বামীর বাড়িতে। শ^শুর-শাশুড়ি, ননদের সঙ্গে একই সংসারে সে ঘর করত।
অসতী বধূর কথাও উল্লেখ আছে কুক্কুরিপাদের ২ সংখ্যক পদে+
‘ছিবসহি বহড়ী কাউহি
ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু ছাই ॥’
অর্থাৎ রাতে বধূ ঘরে ভয়ে ভীতা, রাতে সে কামরূপে যায়। এমন অসতী বধূকে কড়া শাসনে রাখার জন্য কড়া শাশুড়ির উল্লেখ আছে।
মেয়েরা খোঁপা বাঁধত। নূপুর (নেউর), মুক্তহার (মতিহার), কর্ণদুল (কানেরু) ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করত। শবরীপাদের ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায়, আধুনিককালের উপজাতিদের মতো প্রাচীনকালের অনেক বাঙালি নারীরা ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করত। চর্যাপদ থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় তখনকার বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ এবং মাংস। তারমধ্যে হরিণের মাংসই ছিল প্রধান। অনেক চর্যাপদে গাভী-বলদের কথাও উল্লেখ আছে। গাভী দোহনের কথা আছে ঢেন্ডনপাদের ৩৬ সংখ্যক পদে। দুধ থেকে মাখন তোলার উল্লেখ আছে কাহ্নপাদের ৪২ সংখ্যক পদে। তাতে মনে হয় দুধ এবং মাখনও তারা খেত। মদ তাদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল। মদ্যপানের জন্য তারা শুড়িখানাতেও যেত। বিরুবাপাদের ৩ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘এক সে শুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধই।
চী অন বাকলও বনুনী বান্ধই ॥
সহজে থির থির করি বারুনী সান্ধ।
জে আজরামের ছোই ছোই কান্ধ ॥
দশমি দুঅরেত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরদেক আপনে বাই আ ॥
চউশঠী ঘড়িএ দেউ পসারা।
পইবেন গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক ঘড় লী সরুআ নালে।
ভনন্তি, বিরুআ থির করি চালে ॥’
অর্থাৎ এক শুড়িনী দুই ঘরে প্রবেশ করে। চিকন থাকলে বারনী (মদ) বাধে। সহজে স্থির করে বারনী চোলাই কর, যাতে তুমি অজয়-অমর এবং দৃঢ় হতে পার। দশম দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে এলো। চৌষট্টি ঘোড়ার পসরা (মদের) দেওয়া হল। গ্রাক ঢুকলো, তার আর নিষ্ক্রমণ নেই। একটি ছোট ঘড়া, সরু নল। বিরুবা বলছে, স্থিরভাবে চাল দাও।
চর্যাপদে বিভিন্ন গৃহজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শিকারি মাঝি, নর্তকী, গায়ক, বেদে, কাপালিক, পসারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভুসুকুপাদের ৬ এবং ২৩ সংখ্যক হরিণ শিকারের উল্লেখ আছে। সাধারণত ডোম্বীরাই নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাদের এ পারদর্শিতার কথা ভুসুকুপাদের ১০ সংখ্যক পদেÑ
‘একসো পদমা ছৌষট্টি পাখড়ী।
তা চড়ি নাচই ভোয়ী বাইড়ি।’
অর্থাৎ অর্থাৎ এক পদ্ম। তাতে চৌষট্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে ভোয়া বেচারি নাচে।
নাচ-গানের সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্রও বাজানে হতো। এগুলোর মধ্যে একতারা, বীণা, বাঁশী, ঘণ্টা, মাদল, গোপীযন্ত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
অনেকে তুলাধুনার কাজ করত। জাতিভেদ প্রথা তখনও ছিল। সমাজে ডোয়ারীই ছিল সর্বনিম্ন জাতের। কিন্তু তারাই ছিল সর্বগুণে গুণান্বিত। নাচ-গান ছাড়াও তারা তাঁত বুনত, চাঙারি তৈরি করে বিক্রি করত এবং নৌকা চালাত। নিম্নশ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব গুণের জন্য তারা উচ্চশ্রেণির কাপালিক ব্রাহ্মণদেরও কাম্য ছিল। কাহ্নপাদের ১০ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘নগর বাহিরিরে ডোম্বী
তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহসো
বামহন নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বী তো এ সম
করিব মো সাঙ্গে।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি, জোই লাঙ্গে ॥’
অর্থাৎ নগরের বাহিরে ডোম্বী তোমার কুঁড়েঘর। তুমি নেড়া ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোম্বী, আমি তোমাকে সঙ্গী করব। আমি নিঘৃণ, উলংগ লাগী কাহ্ন কাপালিক।
এই ডোম্বীরা নিচুজাতের হওয়াতে এ ঘরের মধ্যে বসবাস করার অধিকার তাদের ছিল না। তাই তারা নগরের বাইরে যেয়ে কুঁড়েঘরে বাস করত। উপরোক্ত চর্যাপদটি এ তথ্য আমরা জানতে পারি। সমাজে চন্ডাল নামে আর একটি নিচু সম্প্রদায় ছিল। অপরদিকে সবরি নামে একটি উচ্চসম্প্রদায় বর্তমান পর্বতের ওপর মহাসুখে বসবাস করত। শবরপাদের ২৮ সংখ্যক পদে আমরা দেখিÑ
‘উষ্ণ উষ্ণ পাবত তহি
বসই সবরি বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরিবহান সবরী
গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা
কর গুলি গুহারী।
তোহারী নিঅ ঘরিনী নামে
সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর শৌললরে
গঅনত লাগেলী ডালী।
এ কেলী সবরী এ বনহিগুই
কর্ণ কুন্তল বজ্রধারী ॥
তিআ ধাড খাঁট পড়িলা সবরো
মহাকুহে সেজি ছাইলি।
সবরো ভুজঙ্গ নইরা মনি দারী পেখরতি পোহাইনি ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাকুহে
কাপুর খাই।
মুন নৈরামনি কণ্ঠে লইআ
মহাকুহে রাত পোহাই ॥’
অর্থাৎ উঁচা উঁচা পর্বত, সেখানে সবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পনিধান করে। সবরীর গলায় গুঞ্জরীমালা। উন্নত সবর, পাগল সর্বর, গোলমাল করো না। তোমার নিজ গৃহিণী সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হল। আকাশে লাগল ভালো। কণ্ঠ কুন্তল বজ্রধারী সবরী একা এই বনেবিহার করে। তিন ধাতুর খাটপালংক হল। সবর মহাসুখে শয্যা বিছাল। সবর ভুজঙ্গ নৈরামনি রমন প্রেমে রাত কেটে গেল। হৃদয় তাম্বলে মহাসুখে কর্পূর খায় এবং শূন্য নৈরামনিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রিযাপন করে।
বলাবাহুল্য, জীবনযাত্রার এ চিত্রের সঙ্গে বর্তমান সমাজচিত্রের অনেকখানি মিল রয়েছে।
বর্তমানকালের মতো তখনও ব্রাহ্মণরা পূজাঅর্চনার কাজে রত থাকত। তারা বেদ পাঠও ও হেসে প্রদান করত। কাপালিকেরা গলায় হাড়ের মালা, কানে কুন্তল এবং পায়ে মল পরিধান করে গায়ে ছাই মেখে উলংগ অবস্থায় থাকত।
কাহ্নপাদের ৪০ সংখ্যক এবং ভুসুকুপাদের ২১ সংখ্যক পদ থেকে আমার জানতে পারি যে, প্রাচীন বাঙালি সমাজেও গুরু-শিষ্য প্রথা প্রচলিত ছিল।
তৎকালীন সমাজে শবদাহের উল্লেখ আছে শবরপাদের ৫০ সংখ্যক পদে।
চিত্তবিনোদনের জন্যনয়বল বা দাবা খেলার প্রচলন ছিল। কাহ্নপাদের ১২ সংখ্যক পদে এ খেলার বিবরণ নিম্নরূপÑ
‘করুণা পীঢ়িহি খেলছ
নঅবল।
সদুগুরু বোহে জিতেল
ভববল।।
ফটিউ দুআ আদেসিরে
ঠাকুর।
উআরি উএসে কাহ্ন
নিঅড় জিনউর ॥
গহিলে তেলিআ বড়িআ
মরাড়িউ।
গঅবরে তোলিআ
পাঞ্চজনা খেলিউ ॥
অবস করিআ ভববল জিত্তা ॥
ভনই কাহ্ন আমহে তলি
দাহ দেহুঁ
চৌষটঠী কোঠা গুণিয়া
লেহু’
অর্থাৎ করুণাপিঁড়িতে নয়বল খেলে সদগুরু বেঁধে ভববল জিতলাম। দুআ (দুটি আভাস) সরিয়ে ঠাকুরকে মারা হলো। উপকারীর উপদেশে এখন কাহ্নর নিকট জিনপুর। প্রথমে সবলে বড় গুলিকে মারা হলো। তারপর গজ দ্বারা পাঁচজনকে ঘায়েল করে মন্ত্রীর সাহায্যে ঠাকুরকে নিবৃত্ত অবস করত ভববল জেতা হলো। কাহ্নপাদ বলছে, আমি ভালো দান দেই। ছকের চৌষট্টি, কোঠা গুণে লই।
এতে দেখা যাচ্ছে, তখনকারও দাবাখেলার নিয়ম-কানুন বর্তমানের মতোই ছিল।
চর্যাপদে আমরা প্রাচীন বাঙালি সমাজের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছু সংখ্যক জিনিসের উল্লেখ পাই, যা আমাদের বর্তমান সমাজেও রয়েছে। যেমনÑ বংশদন্ড (বাখোড়), পিঁড়ি (পাটিহ), দাড় (কেড়আল), দর্পন ( দাপন), রজ্জু (রাজ), দোহনপাত্র (পিটা), কুঠার (কুরাড়ী), বাঁশের চাচরী (চঞ্চালী), ঘড়া (ঘড়ি, ঘড়লী), তালা (তাল), হাঁড়ি (হাঁড়ী ইত্যাদি।
আধুনিক কালের অনেকগুলো পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাণি ও জীবজন্তুর সঙ্গে তৎকালীন বাঙালিরও পরিচিত ছিল। এ সবের মধ্যে ময়ূর (মোরঙ্গ), শকুন (সগুন), কচ্ছপ (ছল), গাভী (গোবআ), বলদ (বলদ), ব্যাঙ (বেঙ্গ), হাঁস (হংস), হস্তি (করিনি) ইত্যাদি।
লাউ (লাউ), তেঁতুল (তেন্তল) প্রভৃতি ফল তখনও পাওয়া যেত।
প্রাচীন বাঙালিরা বিভিন্ন রাগ-রাগিনীতে সংগীতসাধনা করত। প্রতিটি চর্যাপদের প্রথমে বিভিন্নরাগ-রাগিনীর উল্লেখ এর প্রমাণ। চর্যাপদের অনেক রাগ-রাগিনী এখনও আমাদের সংগীত জগতে প্রচলিত আছে। যথাÑ ভৈরবী মল্লারী, রামক্রী ( রামকেলী) ধনসী (ধানশ্রী) ইত্যাদি। এমভিাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, চর্যাকারগণ আধ্যাত্মিক গীতি রচনা করতে গিয়ে সমাজের যে সব জিনিসকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারমধ্যে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাই এগুলো আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক অমূল্য সম্পদ। আ. শ. ম. বাবর আলী
চর্যাপদে বাংলার সমাজচিত্র
চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই পদসমূহ বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান আধ্যাত্মিক সংগীত সমষ্টি। এগুলোর সঠিক বয়স আজ পর্যন্ত নিরুপন করা সম্ভব না হলেও এসব যে বাংলা সাহিত্যের আদি সম্পদ, একথা সকল ভাষা পণ্ডিতরাই স্বীকার করেছেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে এর মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপিতে এর নাম ছিল ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থটির নাম দেন ‘হাজার বছরের পুরান বাংলাভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা’। বলাবাহুল্য, এই সংগীতগুলো বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন বিধায় শাস্ত্রী মহাশয গ্রন্থখানির অনুরূপ নামকরণ করেন। পরে ডক্টর প্রমোদচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের অনুবাদের যে সংকলনটি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন, তাতে মোট ৫১টি সম্পূর্ণ পদ ছিল। এরপর আর নতুন কোনো সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় চর্যাপদের মোট সংখ্যা এটাই বলে পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছিলেন। অবশ্য অনেক পরে ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত, ডক্টর আর্নল্ড বাকে প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ আরও কিছু চর্যাপদের সন্ধান পেলেও ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ব সংগৃহীত সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় সেগুলোকে খাঁটি চর্যাপদ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি; বরং ওগুলো চর্যাপদের অনুসৃষ্ট বলে বিশ^াস করা হয়েছে।
চর্যাপদগুলো কাব্যাকারে রচিত। এগুলোর রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহ পাদ, কলম্বপাদ, চাটিলপাদ, শান্তিপাদ, লুইপাদ, শবরপাদ, গুন্ডরীপাদ, মহীধরপাদ, বীনাপাদ, আর্যদেবপাদ, ঢেন্ডনপাদ. দারিকপাদ, আড়কপাদ, ধামপাদ, তান্তীপাদ, কক্কুরীপাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পদের রচয়িতা বলে এঁদের নামের সঙ্গে ‘পাদ’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে।
আগেই বলা হয়েছে, চর্যাপদগুলো বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম সংগীত সমষ্টি। এ সব সংগীত ইহকালের সমস্যা সংকুল জীবনযাত্রা এবং তা থেকে নির্বানলাভ পূর্বক মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের আকাক্সক্ষা এবং তার উপায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, তা সরাসরিভাবে বর্ণনা না করে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমেই বলা হয়েছে। আর এই রূপক সমূহের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
চর্যাপদে তৎকালীন বাঙালিদের যাতায়াতের জন্য প্রধান বাহন হিসেবে নৌকার ব্যবহার ছিল। বহুসংখ্যক পদে নৌকার নামোল্লেখ এবং এর ব্যবহারিকতার বর্ণনা রয়েছে। অনেক সময় দূরের যাত্রাপথে উজানগুণ টেনে নিয়ে নৌকা চালানো হতো। সে সময় নৌপথে দস্যুর ভয় ছিল। এমন একটা বর্ণনা আছে নরহপাদের ৩৮ সংখ্যক পদেÑ
‘কাএ নাবড়ি খানটিমন কাড় আল।
সদগুরু বঅনে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাঙ্গ।
আল উপাএ পারদ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টানই গুণে।
মেলি মিন সহজে জানই আনত ॥
বাটত ভএ খান্ট বি বলআ।
ভব উলোলে সরবি বেড়িয়া ॥
ফুল লই ঘরএ সোন্ত উজাই
সর ভনই গঅনে সমাই ॥’
অর্থাৎ কায়ারূপ নৌকাতে মনবৈঠা ও সদগুরু বচনরূপ হাল ধরো। চিত্ত স্থির করে হাল ধরো। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যাবে না। নৌবাহী গুণে নৌকা টানে। সহজে মিলে যাও, অন্যপথে যেও না।
পথে ভয়। দস্যু বলবান। তবে সমুদ্রের উল্লাসে সবই বিনষ্ট। সরহ বরলন, কূল ধরে খরস্রোতে উজান বেয়ে চললে (নৌকা) গগণে প্রবেশ করে।
সাধারণত ডোম্বীরা কিছু পয়সার বিনিময়ে পারাপার করত। আবার অনেক সময় বিনে পয়সাতেও। পয়সা হিসেবে কড়ি, বুড়ির উল্লেখ আছে। যেমনÑ
‘কবড়ী লেই, কবড়ী নলেই
কুচ্ছেল পর করেই।’
(ডোম্বীপদ : ১৪ সংখ্যক)
অর্থাৎ ডোম্বী কড়িবুড়ি না নিয়ে স্বেচ্ছায় নৌকা পার করে দেয়।
চর্যার বিভিন্ন পদে নৌকার বিভিন্ন অংশ এবং সরঞ্জামের উল্লেখ আছে। যেমনÑ কেড় আল-দাঁড়, পতবাল-হাল, পুলিন্দা-মাস্তুন, মাঞ্জ-লুই ইত্যাদি।
অনেক ক্ষেত্রে পারাপারের মাধ্যম হিসেবে ভেলাও ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তিপাদের ১৫ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘মাআ মোহ সমুদারে অন্তন
বুঝসি যাহ্
াআগে ন বন ভেলা দীসইÑ
ভান্তি ন পুছসি নাহা ॥’
অর্থাৎ মায়ামোহ রূপ সমুদ্রের অন্ত বুঝে না, গভীরতা বুঝে না। সামনে নৌকা বা ভেলা কিছুই দেখা যাচ্ছে না।
ছোট নদী পারাপারের জন্য গাছ কেটে জোড়া দিয়ে সাঁকো তৈরি করা হতো। চাট্টিলাপাদের ৬ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘ভবনই গহন গম্ভীরে বেগে বাহি।
দু অন্তে চিখিল মাঝো থাহি ॥
ধামাথে চটি সবঙ্কম গঢ়ই ।
পারগামী লোঅ ভির তরই ॥
ফাড়ি মোহ তরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ়ি টাঙ্গি
নিবানে কোড়িঅ ॥’
অর্থাৎ গহন ও গভীর ভবনদী বেগে বয়ে যাচ্ছে। এর দুধারে কাদা, মাঝখানে থই নেই। ধর্মসাধনার জন্য সাঁকো বানালেন (যাতে) পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে পার হতে পারে। মহীতরু চিরে পাটি জোড়া দেওয়া হল।
বর্তমানের মতো প্রাচীন বাঙালি সমাজেও অতি ধুমধামের সঙ্গে বিবাহকার্য সমাধা হতো। বর ঢাক-ঢোল, কাসি-ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিয়ে বিয়ে করতে কনের বাড়িতে যেত। বিয়েতে যৌতুকপ্রথা ছিল। নববধূর বাসর যাপনের ব্যবস্থাও ছিল। কৃষ্ণপাদের ১৯ সংখ্যক পদে আমরা দেখিÑ
‘ভব নির্বানে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেনি করন্ড ফাসালো ॥
জয় জয় দুন্দহি সাছ উছলিআ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিলা ॥
ডোম্বি বিবাহিয়া আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ অনুত্তর ধাম ॥
অহনিশি ফুরআ প্রসঙ্গে জাইি।
জেইনি জালে রঅনি পোহাই ॥
ডোয়ী এর সঙ্গে জো জোই রও।
খনই দূরে ছাড়ই সহজ উন্মত্ত ॥’
অর্থাৎ ভব নির্মাণকে পটই ও মাদল, মন-পবনকে করন্ড ও ফাঁসি করা হল। দুন্দুভি শব্দে জয় জয় শব্দ উছলে উঠল। কাহ্নপাদ ডোম্বিকে বিয়ে করতে চললো। ডোম্বীকে বিয়ে করে জন্ম নাশ করল। যৌতুক হিসেবে পেল অনত্তর ধাম। দিনরাত সুরভ প্রসঙ্গে যায়। যোগিনী জালে রাত্রি পোহায়। ডোমীর সঙ্গে সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত, সে সহজও হয়ে ক্ষণমাত্রও ডোম্বীকে ছেড়ে যায় না। এপর স্বামীর সঙ্গে বধূ চলে আসতো স্বামীর বাড়িতে। শ^শুর-শাশুড়ি, ননদের সঙ্গে একই সংসারে সে ঘর করত।
অসতী বধূর কথাও উল্লেখ আছে কুক্কুরিপাদের ২ সংখ্যক পদে+
‘ছিবসহি বহড়ী কাউহি
ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু ছাই ॥’
অর্থাৎ রাতে বধূ ঘরে ভয়ে ভীতা, রাতে সে কামরূপে যায়। এমন অসতী বধূকে কড়া শাসনে রাখার জন্য কড়া শাশুড়ির উল্লেখ আছে।
মেয়েরা খোঁপা বাঁধত। নূপুর (নেউর), মুক্তহার (মতিহার), কর্ণদুল (কানেরু) ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করত। শবরীপাদের ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায়, আধুনিককালের উপজাতিদের মতো প্রাচীনকালের অনেক বাঙালি নারীরা ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করত। চর্যাপদ থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় তখনকার বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ এবং মাংস। তারমধ্যে হরিণের মাংসই ছিল প্রধান। অনেক চর্যাপদে গাভী-বলদের কথাও উল্লেখ আছে। গাভী দোহনের কথা আছে ঢেন্ডনপাদের ৩৬ সংখ্যক পদে। দুধ থেকে মাখন তোলার উল্লেখ আছে কাহ্নপাদের ৪২ সংখ্যক পদে। তাতে মনে হয় দুধ এবং মাখনও তারা খেত। মদ তাদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল। মদ্যপানের জন্য তারা শুড়িখানাতেও যেত। বিরুবাপাদের ৩ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘এক সে শুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধই।
চী অন বাকলও বনুনী বান্ধই ॥
সহজে থির থির করি বারুনী সান্ধ।
জে আজরামের ছোই ছোই কান্ধ ॥
দশমি দুঅরেত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরদেক আপনে বাই আ ॥
চউশঠী ঘড়িএ দেউ পসারা।
পইবেন গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক ঘড় লী সরুআ নালে।
ভনন্তি, বিরুআ থির করি চালে ॥’
অর্থাৎ এক শুড়িনী দুই ঘরে প্রবেশ করে। চিকন থাকলে বারনী (মদ) বাধে। সহজে স্থির করে বারনী চোলাই কর, যাতে তুমি অজয়-অমর এবং দৃঢ় হতে পার। দশম দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে এলো। চৌষট্টি ঘোড়ার পসরা (মদের) দেওয়া হল। গ্রাক ঢুকলো, তার আর নিষ্ক্রমণ নেই। একটি ছোট ঘড়া, সরু নল। বিরুবা বলছে, স্থিরভাবে চাল দাও।
চর্যাপদে বিভিন্ন গৃহজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শিকারি মাঝি, নর্তকী, গায়ক, বেদে, কাপালিক, পসারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভুসুকুপাদের ৬ এবং ২৩ সংখ্যক হরিণ শিকারের উল্লেখ আছে। সাধারণত ডোম্বীরাই নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাদের এ পারদর্শিতার কথা ভুসুকুপাদের ১০ সংখ্যক পদেÑ
‘একসো পদমা ছৌষট্টি পাখড়ী।
তা চড়ি নাচই ভোয়ী বাইড়ি।’
অর্থাৎ অর্থাৎ এক পদ্ম। তাতে চৌষট্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে ভোয়া বেচারি নাচে।
নাচ-গানের সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্রও বাজানে হতো। এগুলোর মধ্যে একতারা, বীণা, বাঁশী, ঘণ্টা, মাদল, গোপীযন্ত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
অনেকে তুলাধুনার কাজ করত। জাতিভেদ প্রথা তখনও ছিল। সমাজে ডোয়ারীই ছিল সর্বনিম্ন জাতের। কিন্তু তারাই ছিল সর্বগুণে গুণান্বিত। নাচ-গান ছাড়াও তারা তাঁত বুনত, চাঙারি তৈরি করে বিক্রি করত এবং নৌকা চালাত। নিম্নশ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব গুণের জন্য তারা উচ্চশ্রেণির কাপালিক ব্রাহ্মণদেরও কাম্য ছিল। কাহ্নপাদের ১০ সংখ্যক পদে আছেÑ
‘নগর বাহিরিরে ডোম্বী
তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহসো
বামহন নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বী তো এ সম
করিব মো সাঙ্গে।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি, জোই লাঙ্গে ॥’
অর্থাৎ নগরের বাহিরে ডোম্বী তোমার কুঁড়েঘর। তুমি নেড়া ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোম্বী, আমি তোমাকে সঙ্গী করব। আমি নিঘৃণ, উলংগ লাগী কাহ্ন কাপালিক।
এই ডোম্বীরা নিচুজাতের হওয়াতে এ ঘরের মধ্যে বসবাস করার অধিকার তাদের ছিল না। তাই তারা নগরের বাইরে যেয়ে কুঁড়েঘরে বাস করত। উপরোক্ত চর্যাপদটি এ তথ্য আমরা জানতে পারি। সমাজে চন্ডাল নামে আর একটি নিচু সম্প্রদায় ছিল। অপরদিকে সবরি নামে একটি উচ্চসম্প্রদায় বর্তমান পর্বতের ওপর মহাসুখে বসবাস করত। শবরপাদের ২৮ সংখ্যক পদে আমরা দেখিÑ
‘উষ্ণ উষ্ণ পাবত তহি
বসই সবরি বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরিবহান সবরী
গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা
কর গুলি গুহারী।
তোহারী নিঅ ঘরিনী নামে
সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর শৌললরে
গঅনত লাগেলী ডালী।
এ কেলী সবরী এ বনহিগুই
কর্ণ কুন্তল বজ্রধারী ॥
তিআ ধাড খাঁট পড়িলা সবরো
মহাকুহে সেজি ছাইলি।
সবরো ভুজঙ্গ নইরা মনি দারী পেখরতি পোহাইনি ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাকুহে
কাপুর খাই।
মুন নৈরামনি কণ্ঠে লইআ
মহাকুহে রাত পোহাই ॥’
অর্থাৎ উঁচা উঁচা পর্বত, সেখানে সবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পনিধান করে। সবরীর গলায় গুঞ্জরীমালা। উন্নত সবর, পাগল সর্বর, গোলমাল করো না। তোমার নিজ গৃহিণী সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হল। আকাশে লাগল ভালো। কণ্ঠ কুন্তল বজ্রধারী সবরী একা এই বনেবিহার করে। তিন ধাতুর খাটপালংক হল। সবর মহাসুখে শয্যা বিছাল। সবর ভুজঙ্গ নৈরামনি রমন প্রেমে রাত কেটে গেল। হৃদয় তাম্বলে মহাসুখে কর্পূর খায় এবং শূন্য নৈরামনিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রিযাপন করে।
বলাবাহুল্য, জীবনযাত্রার এ চিত্রের সঙ্গে বর্তমান সমাজচিত্রের অনেকখানি মিল রয়েছে।
বর্তমানকালের মতো তখনও ব্রাহ্মণরা পূজাঅর্চনার কাজে রত থাকত। তারা বেদ পাঠও ও হেসে প্রদান করত। কাপালিকেরা গলায় হাড়ের মালা, কানে কুন্তল এবং পায়ে মল পরিধান করে গায়ে ছাই মেখে উলংগ অবস্থায় থাকত।
কাহ্নপাদের ৪০ সংখ্যক এবং ভুসুকুপাদের ২১ সংখ্যক পদ থেকে আমার জানতে পারি যে, প্রাচীন বাঙালি সমাজেও গুরু-শিষ্য প্রথা প্রচলিত ছিল।
তৎকালীন সমাজে শবদাহের উল্লেখ আছে শবরপাদের ৫০ সংখ্যক পদে।
চিত্তবিনোদনের জন্যনয়বল বা দাবা খেলার প্রচলন ছিল। কাহ্নপাদের ১২ সংখ্যক পদে এ খেলার বিবরণ নিম্নরূপÑ
‘করুণা পীঢ়িহি খেলছ
নঅবল।
সদুগুরু বোহে জিতেল
ভববল।।
ফটিউ দুআ আদেসিরে
ঠাকুর।
উআরি উএসে কাহ্ন
নিঅড় জিনউর ॥
গহিলে তেলিআ বড়িআ
মরাড়িউ।
গঅবরে তোলিআ
পাঞ্চজনা খেলিউ ॥
অবস করিআ ভববল জিত্তা ॥
ভনই কাহ্ন আমহে তলি
দাহ দেহুঁ
চৌষটঠী কোঠা গুণিয়া
লেহু’
অর্থাৎ করুণাপিঁড়িতে নয়বল খেলে সদগুরু বেঁধে ভববল জিতলাম। দুআ (দুটি আভাস) সরিয়ে ঠাকুরকে মারা হলো। উপকারীর উপদেশে এখন কাহ্নর নিকট জিনপুর। প্রথমে সবলে বড় গুলিকে মারা হলো। তারপর গজ দ্বারা পাঁচজনকে ঘায়েল করে মন্ত্রীর সাহায্যে ঠাকুরকে নিবৃত্ত অবস করত ভববল জেতা হলো। কাহ্নপাদ বলছে, আমি ভালো দান দেই। ছকের চৌষট্টি, কোঠা গুণে লই।
এতে দেখা যাচ্ছে, তখনকারও দাবাখেলার নিয়ম-কানুন বর্তমানের মতোই ছিল।
চর্যাপদে আমরা প্রাচীন বাঙালি সমাজের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছু সংখ্যক জিনিসের উল্লেখ পাই, যা আমাদের বর্তমান সমাজেও রয়েছে। যেমনÑ বংশদন্ড (বাখোড়), পিঁড়ি (পাটিহ), দাড় (কেড়আল), দর্পন ( দাপন), রজ্জু (রাজ), দোহনপাত্র (পিটা), কুঠার (কুরাড়ী), বাঁশের চাচরী (চঞ্চালী), ঘড়া (ঘড়ি, ঘড়লী), তালা (তাল), হাঁড়ি (হাঁড়ী ইত্যাদি।
আধুনিক কালের অনেকগুলো পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাণি ও জীবজন্তুর সঙ্গে তৎকালীন বাঙালিরও পরিচিত ছিল। এ সবের মধ্যে ময়ূর (মোরঙ্গ), শকুন (সগুন), কচ্ছপ (ছল), গাভী (গোবআ), বলদ (বলদ), ব্যাঙ (বেঙ্গ), হাঁস (হংস), হস্তি (করিনি) ইত্যাদি।
লাউ (লাউ), তেঁতুল (তেন্তল) প্রভৃতি ফল তখনও পাওয়া যেত।
প্রাচীন বাঙালিরা বিভিন্ন রাগ-রাগিনীতে সংগীতসাধনা করত। প্রতিটি চর্যাপদের প্রথমে বিভিন্নরাগ-রাগিনীর উল্লেখ এর প্রমাণ। চর্যাপদের অনেক রাগ-রাগিনী এখনও আমাদের সংগীত জগতে প্রচলিত আছে। যথাÑ ভৈরবী মল্লারী, রামক্রী ( রামকেলী) ধনসী (ধানশ্রী) ইত্যাদি। এমভিাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, চর্যাকারগণ আধ্যাত্মিক গীতি রচনা করতে গিয়ে সমাজের যে সব জিনিসকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারমধ্যে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাই এগুলো আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক অমূল্য সম্পদ।
প্যানেল