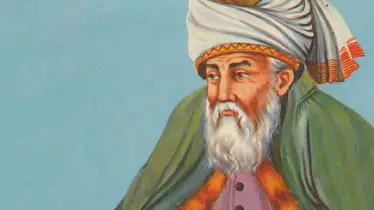‘আমি এখন সময় করেছি-
তোমার এবার সময় কখন হবে
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে।’ - রবীন্দ্রনাথ (প্রতীক্ষা-খেয়া কাব্যগ্রন্থ)
মানুষের জীবন জুড়েই থাকে এই প্রতীক্ষাকাল। কিংবা বলা চলে কখনও কখনও জীবনব্যাপী প্রিয়জনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় মানুষকে। সন্তানের জন্য মায়ের প্রতীক্ষাÑ ‘খোকা তুই কবে আসবি! কবে ছুটি?’ কবিতার এই উচ্চারণ যেন সব মায়ের অন্তরের ধ্বনি। আবার ভালোবাসার মানুষের জন্য প্রতীক্ষারত নারীর অন্তর নিঙরানো গান ‘কোনদিন আসিবেন বন্ধু- কয়া যাও, কয়া যাও রে—’ কিংবা ‘ওকি একবার আসিয়া সোনার চান মোর যাও দেখিয়া রে’ মাঠ-প্রান্তরের গান ভাওয়াইয়ার এই সুর যেন বিরহিণী নারীর প্রতীক্ষার হৃদয় মথিত করা আবেগ। এর সর্বজনীন আবেদনকে উপেক্ষা করার শক্তি কার আছে?
প্রতীক্ষার একটা দিন কিংবা রাত্রিকে কখনো এক একটা বছর মনে হয়। প্রতীক্ষার রাত্রি যেন পৃথিবীর দীর্ঘতম রাত্রি। আনন্দ আর বিষাদে মেশানো এই প্রতীক্ষাকালের অবসান কখনও আনন্দ অশ্রু দিয়ে আবার কখনও সেখানে বেদনার কালো ছায়া চিরদিনের মত ক্ষত রেখে যায়। কাজী নজরুল লিখছেন ‘সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে/ তব গৃহে জ¦লে বাতি/ ফুরায় তোমার উৎসব নিশি সুখে/ প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি’। আবার লিখছেন, ‘সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায় তুমি ফিরিলে না ঘরে /আঁধার ভবন জ¦লেনি প্রদীপ মন যে কেমন করে’। দিন শেষে পাখীরাও ঘরে ফেরে! এক অমোঘ আকর্ষণে তার এই ফিরে আসা। কিন্তু বৃক্ষ-নদী-রাজপথ-পাহাড়-অরণ্য এরাও কি কারো জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে? ভাব জগতের বাসিন্দা যারা, যাদের অনুভূতি আর আবেগ সর্বত্রগামী, সেই ছোটগল্প-কবিতা-গান-চিত্রকলার অমর স্রষ্টাগণ, তাদের ভাবনায় এই প্রতীক্ষা বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। ‘আমি তোমার জন্য পথপ্রান্তে অশ্বত্থের মত দাঁড়িয়ে থাকবো- ঐ বৃক্ষ অনন্তকাল ধরে যোগ্য পথিকের জন্য প্রতীক্ষমাণ ’ (রফিক আজাদ-প্রতীক্ষা)। গল্পগুচ্ছে ‘রাজপথের কথা’ ছোটগল্পে রাজপথ বলছে, ‘প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি’ কিংবা ‘ঘাটের কথা’ ছোটগল্পে বালিকা কুসুমের জন্য ঘাটের প্রতীক্ষা, ‘তখন জানিতাম কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে’। কুসুমের নদীতে আত্মবিসর্জনে ঘাটের মর্মস্পর্শী কথা ‘আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।’ পোস্টমাস্টার ছোটগল্পে রতন প্রতীক্ষা করে ছিলো তার দাদাবাবু আবার ফিরে আসবে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘সে পোস্ট অফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আইসে,- সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না।’ এখানে রবীন্দ্রনাথ মানবমনের এই প্রবণতাকে বলছেন ‘হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়’! বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যরে কবিতা ‘প্রিয়তমাসু’। সেখানে যুদ্ধ শেষ হয়েছে তখন একজন সৈনিক তার ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করছে- ‘যুদ্ধ শেষে ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে। জানি আমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে নেই মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে-তবু একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে / সে তোমার হৃদয়’। জগৎ সংসারে কেউ একজন অপেক্ষা করে আছে এই ব্যাকুলতা মানুষকে ঘরমুখী করে। রবীন্দ্রনাথের বাঁশী কবিতার হরিপদ কেরানি, গভীর রাত্রির একাকিত্বে যার মনে হয় ‘মনে যার নিত্য আসা যাওয়া’ আঙিনাতে সে যেন অপেক্ষা করে আছে। প্রাচীন সোমপুর বিহার পাল যুগের মহাকীর্তি, এর কেন্দ্রীয় মন্দিরের দেয়ালগাত্রে শত শত টেরাকোটার ফলক। যাতে ফুটে উঠেছে তৎকালীন মানুষের ধর্মবিশ^াস, শিল্পবোধ আর জীবনচর্যা। মূল মন্দিরের বাইরের দেয়ালে উৎকীর্ণ একটি টেরাকোটার ফলক যেখানে একজন নারী দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানি দিয়ে দরজার একটি কাঠ শক্ত করে ধরে আছে। সেই নারী যেন কার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। তার সন্তান নতুবা প্রিয়তম কেউ হয়তো কোন দূরদেশে গেছে ভাগ্যান্বেষণে। তাই নারীর এই স্বভাবজাত ব্যাকুলতা। সংস্কৃত শ্লোকে আছে ‘দিশাং মুখং সর্বমসৌ বিলকয়েত্ / তথা চ তিষ্ঠেত্ দিনমানম অক্ষয়ম্’ আমার সর্বগামী দৃষ্টি শুধু তোমারই পথ চেয়ে আছে, আর আমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছি যেন সময় ও কাল সবই থমকে গেছে। মেঘদূত সনেটে মাইকেল লিখছেন- ‘অধীর এ হিয়া হায়, যার রূপ স্মরি/কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি/ মৃদু নাদে কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!’ মহাকবি কালিদাস তাঁর ‘মেঘদূত’ কাব্যে বিরহকাতর দুটি হৃদয়কে অভিন্ন বলে অভিহিত করেছেন। সেখানে প্রিয়া অদর্শনে বিরহী যক্ষ উত্তর মেঘমালাকে বলছে ‘তাং মে দ্বিতীয়ং জীবনং জানীথা:’-তাকে আমার দ্বিতীয় জীবন বা প্রাণস্বরূপ বলে জানবে। একই বিষয় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘উত্তরচরিতে’ দেখতে পাই সীতা অদর্শনে বিরহকাতর রাম বলছেন ‘ত্বং জীবিতং ত¦মসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং/ত্বং কৌমুদি নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে’। তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদি, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত’।
পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ- জোলায়খা’ সেখানে চিরদুঃখিনী বিরহিণী জোলেখার একটি বেদনার অভিব্যক্তি: ‘ নিশি উজাগর আঁখি ঝামর বদন /পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ/ শুনরে পবন মোর দুঃখের কাহিনী/ দন্ডেক বরিখ মোর দীঘল যামিনী/মোর পিয় স্থানে গিয়া কহরে সম্বাদ/ কেমন সহাস্য তান দাসী সঙ্গে বাত।’ গীতগোবিন্দ কাব্যে কবি জয়দেব লিখছেন, ‘উন্মদ মদন মনোরথ পথিক বধূজনজনিত বিলাপে/ অলিকুল সঙ্কুল কুসুম নিরাকূল ব্যাকুল কলাপে’। ওগো সখি, এমন বসন্তদিনে ঐ শোন দিকে দিকে উঠছে বিরহের রোদন ধ্বনি, প্রিয় যাদের গিয়েছে দূর প্রবাসে, কাঁদছে সেই বিরহ ব্যাকুল পথিক বধুরা। প্রস্ফুটিত বকুলের বনে ভ্রমরকূল গুনগুন করে সেই ব্যথাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বড় চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে কৃষ্ণের বাঁশী রাধা-রাধা সুরে ডাক দিয়েছে। পদকর্তার রচনায় রাধার ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। তিনি বড়াই কে বলছেন ‘ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞি কোন দিগে সার ণীসারে-/বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বে-আকুল বড়াই জাইবোঁ তার অনুসারে।’ ঘর থেকে বাইরে এসে নাগর কানাই বাঁশী বাজায়। বড়াই বাঁশীর শব্দে আমার মন হয়েছে ব্যাকুল ,তার খোঁজেই আমি যাব। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীতে ভরা বর্ষার রাতে তাঁর কাব্যের নায়িকার অন্তর বিপুল বিলাপে ভেঙে পড়ে: ‘সখি হমারি দুখক নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর/কম্পি ঘন গর-জন্তি সন্ততি ভূবন ভরি বরিখন্তিয়া’। কৃষ্ণ বিরহে তাঁর শয়ন মন্দির শূন্য হয়ে যায়, চারিদিকে মেঘ গর্জন করে, ভুবন জুড়ে নামে বর্ষণ। আর একটি বৈষ্ণব পদে কাব্যের নায়িকা রাইকিশোরী, কৃষ্ণকানাই এর প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছে। দিন অবসান হতে চলেছে কিন্তু কানাই আসছে না। তার কোলের ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে সে মালা গাঁথা ভুলে গেছে। তখন ফুলগুলো যেন আপনা থেকেই মালায় পরিণত হচ্ছে। মানিনীর চোখের জলে গাঁথা হচ্ছে বিনি সূতোর মালা। ‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ’- ‘সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা/ শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনই পাবো দেখা’। প্রতীক্ষার এই মধুরতম অবসান বিরহী মনে অপার ঐশ^র্য নিয়ে ধরা দেয়। কিন্তু যার জন্য এই প্রতীক্ষা সেও কি প্রতীক্ষার প্লাবনে ধন্য হয়ে যায়? শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্যই লিখছেন ‘উৎকণ্ঠা আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে সেই ধন্য করিবে আমাকে’। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের মালোপাড়ার এক অনাথ বালক অনন্ত, তার আশ্রয়দাত্রী উদয়তারার সঙ্গে তার ভাইয়ের গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় সেই গ্রামের তারই সমবয়সী এক বালিকা অনন্তবালার সঙ্গে। খেলার ছলে বালিকা অনন্তবালা একদিন শাপলা ফুলের মালা পড়িয়ে দেয় অনন্তের গলায়। অনন্ত সেই মালাটি আবার জড়িয়ে দেয় অনন্তবালার খোঁপায়। গ্রামের গোঁসাই বাবাজির কাছে অনন্ত বর্ণ পরিচয় শিখতে থাকে।
একসময় অনন্তবালাও সেখানে পড়তে আসে কিন্তু পড়াশোনায় তার মন বসে না। সে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে অনন্তকে বলে তাদের বাড়িতে তাকে চিরস্থায়ীভাবে রেখে দেয়ার ইচ্ছা তার বাবা-মায়ের। কিন্তু অনন্ত হঠাৎই একদিন শহরের স্কুলে পড়ার জন্য গ্রাম ছেড়ে কুমিল্লা শহরে চলে যায়। এদিকে অনন্তবালা অপেক্ষা করতে থাকে অনন্ত কখনও নিশ্চয়ই গ্রামে ফিরে আসবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখে অনন্ত তার মালোপাড়াকে ভুলে যায়। এদিকে অনন্তের প্রতীক্ষায় বছরের পর বছর পার করে অনন্তবালা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখছেন ‘অনন্তবালার বয়স বাড়িয়াছে। তার বয়সের অন্যান্য মালোর মেয়েরা সকলেই স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। সে এখনো মাঘমণ্ডলের পূজা করে। অনন্ত নাকি তাকে বলিয়া গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া সে যেদিন ফিরিয়া আসিবে, সেদিন যাহা বলিবে অনন্ত তাহাই করিবে। ‘আমি আর কি বলিব। মা খুড়িমা যে কথা অহর্নিশি বলে, আমিও সেই কথাই বলিব’, বলিয়াছিল অনন্তবালা। সেটা ছিল অবোধ বয়সের ছেলেমানুষি। এখন বয়স বাড়িয়া সে চিন্তাটা আরও প্রবল হইয়াছে। তার বয়সের অন্য মেয়েদের যখন বর আসিল, অনন্তবালা দেখিয়াছে, কিন্তু মনে করিয়া রাখিয়াছে, তারও একদিন বর আসিবে। সে বর আর কেউ নয়। সে অনন্ত’। অনন্ত একবার গ্রামে এসেছিল উপোসি মালোদের সাহায্য করতে। কিন্তু সে কাউকে মনে রাখেনি। অনন্তবালার স্মৃতি তার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল। একটি জনপ্রিয় আধুনিক গানের কথায় আছে ‘কেন আশা বেঁধে রাখি/কেন দীপ জে¦লে রাখি/জানি আসবে না-ফিরে আর তুমি/তবু পথপানে চেয়ে থাকি’।
এভাবেই কত প্রতীক্ষাকাল অনাদি থেকে অনন্তের দিগন্তরেখায় প্রতিনিয়ত মিলিয়ে চলেছে।