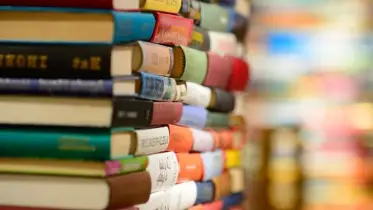১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠেছিলেন। জাহাজটি মাদ্রাজ পৌঁছাতে সময় লেগেছিলো বিশদিন অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার মাইকেল মাদ্রাজ পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তিনি যে কলকাতা ছাড়ছেন এই কথাটি কাউকে বলেননি এমনকি তাঁর একান্ত প্রাণের বন্ধু গৌরদাসকেও না। তিনি হঠাৎ কেন মাদ্রাজ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সে বিষয়ে তাঁর একাধিক জীবনীকার অনুমান করেছেন। তবে অনুমানের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্র মনে করেন-১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিশপস্ কলেজে যে চারজন দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ছাত্র লেখাপড়া করতেন তারা তাঁকে কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দক্ষিণী ছাত্রদের সাথে মধুসূদন এক জাহাজে করে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন বলে অনুমান করেছেন তিনি। আবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর অন্যতম জীবনীকার গোলাম মুরশিদ বলেছেন-‘সত্যিকার ঘটনা হলো এই দক্ষিণী ছাত্রদের কেউ মাইকেলকে মাদ্রাজে যাবার পরামর্শ দেননি। তিনি সে পরামর্শ এবং আশ্বাস পেয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশপস্ কলেজের সাবেক ছাত্র মাদ্রাজের চার্লস এগবার্ট কেনেটের কাছ থেকে। জীবনীকার গোলাম মুরশিদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- ‘কবি এই কলেজে ভর্তি হবার ঠিক পাঁচ মাস পরে-১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ৫-তিনি মিডলটন বৃত্তি নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। বয়সে দু’বছরের ছোট হলেও, কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো।’
তবে মধুসূদনের হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ যাওয়ার পরামর্শ যেখান থেকে যে ভাবেই আসুক না কেন, হয়তো তার পেছনে কিছু কারণও রয়েছে। তিনি কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে, খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করার পর কবির পিতা যখন তাঁকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, তখন বাড়ির পরিবেশ তাঁর জন্য একেবারে অন্যরকম মনে হতে লাগলো। সেইসময় হয়তো তিনি কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা থেকে প্রায় ১৭০০ কিমি দূরত্বের ছোট মফস্বল শহর মাদ্রাজকে বেঁচে নিয়েছিলেন। তবে ইতোপূর্বে তাঁর মাদ্রাজ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না বলেই জানা যায়। তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতেন লন্ডন যাবেন, ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করবেন, হোমার, বায়রন, ভার্জিল, ট্যাসো, দান্তে’র মতো বড় কবি হবেন।
আবার মধুসূদনের মাদ্রাজ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কাউকে না জানানোর পেছনে কারণও রয়েছে। তাই তিন তাঁর এই পরিকল্পনা বন্ধু গৌরদাসকেও জানাননি। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি গৌরদাসকে বিশ্বাস করতে পারেননি। ইতোপূর্বে বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনার কথা গৌরদাসকে জানিয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছিলো সেই স্মৃতি তাঁকে হয়তো নাড়া দিয়ে থাকতে পারে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি যখন বিলেত যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন তখন গৌরদাসকে জানিয়েছিলেন। বিষয়টি গৌরদাস জানার পর তাঁর মা-বাবাকে জানিয়ে দিবেন বলে মধুকে ভয় দেখিয়েছিলেন। যদিও বিষয়টি পরবর্তীতে বন্ধু গৌরদাস গোপন রেখেছিলেন।
মধুসূদন মাদ্রাজে থাকাকালীন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Captive Ladie রচনা করেন। প্রথমে এ কাব্য প্রকাশিত হয় Madras Circulator পত্রিকায়। তিনি এ কাব্যগ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। শেষ করেন এ মাসের ২৫ তারিখে।Captive Ladie কাব্য গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন-‘এটা লেখা হয়েছে জীবনের নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে-অভাব আর অনটনের সঙ্গে লড়াই করে। মাদ্রাজে যাওয়ার এক বছর এক মাস পর ১৮৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রিয়বন্ধু গৌরদাসকে লেখা প্রথম চিঠিতে তিনি তাঁর আর্থিক অভাব অনাটনের কথা, নানা প্রতিকূল অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। বন্ধুকে জানিয়েছিলেন-শত অসুবিধা সত্ত্বেও ছাপানোর জন্য একটি কাব্য রচনার কাজ শেষ করেছেন। মধুসূদনের গ্রন্থকার হওয়ার জন্য এটিই ছিলো প্রথম প্রয়াস।
মধুসূদন এ কাব্য সম্পর্কে বন্ধু গৌরদাসকে মাদ্রাজ থেকে লিখেছেন, ‘এতে আছে দুটি সর্গের একটি কাহিনী-আধা ঐতিহাসিক কাহিনী। ভালো মন্দতে মেশানো মোট প্রায় বারো শো পঙ্ক্তি এ ছাড়া আছে ছোট একটি কি দুটি কবিতা।’
মধুকবি তাঁর এ কাব্যটি প্রকাশ করেছেন ভীষণ উৎসাহ নিয়ে। তিনি আশা করেছিলেন এ কাব্য কবিকে এনে দিবে তাঁর কাক্সিক্ষত কবিখ্যাতি। শুধু বাধা একটি জায়গায় তা হলো এ কাব্যের ছাপা খরচ। তিনি খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন এ কারণে যে, সেই সময় মাদ্রাজে ছাপার খরচ ছিলো খুব বেশি। যা তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানিয়ে ছিলেন। এ কাব্যের জন্য কিছু গ্রাহক জুটিয়ে দিতে পারবেন কিনা তা জানতে চেয়ে বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন-‘আমি জানি তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবে। প্রতি কপির মূল্য মাত্র দু’টাকা। এমন কি আমাদের স্কুলের পুরনো বন্ধুদের মধ্য থেকে তুমি নিশ্চয় কমপক্ষে ৪০ জন গ্রাহক জুটিয়ে দিতে পারবে। আমি এখানে খুব কম লোককে জানি। সেজন্য আমি এ কাব্য বিক্রি থেকে ছাপার খরচ চুকিয়ে দিতে পারবো বলে মনে হয় না।... তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি কোনো আর্থিক লাভের আশায় এ বই ছাপাচ্ছিনে। কেবল লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেলেই হলো।’
শুধু বন্ধু গৌরদাস বসাককে নয়, গ্রাহক সংগ্রহের জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন হিন্দু কলেজের সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক মি মন্টেগু এবং বিশপস কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবার্ট ওয়াকারকে। কবির পত্র অনুযায়ী সববন্ধুরা গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করেছিলেন। গৌরদাস কবির চিঠি পাওয়ার পর অল্প দিনের মধ্য ১৮ জন গ্রাহক নিশ্চিত করেছিলেন। বিশপস্ কলেজের বন্ধুরা জোটান ২৫ জন গ্রাহক। অন্যরাও দু’চারজন গ্রাহক ঠিক করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে তাঁর এ কাক্সিক্ষত কাব্যটি প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে মাইকেল এই প্রথম গ্রন্থকার হিসেবে আত্মতৃপ্তি পেলেন।
এ কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর প্রেস থেকে কবির কাছে টাকার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। কবি এটি ছাপিয়েছিলেন ১৪২ নম্বর মাউন্ট রোড়ের Madras Advertiser প্রেস থেকে। প্রেসের মালিক অ্যাবেল পেন সিমকিন্স। যদিও সেখানে কবি কিছু টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু তারা বাকি টাকা পরিশেধের জন্য তাড়া লাগিয়েছিলো। প্রেসের মালিক কবিকে ছাপানোর টাকার জন্য বারবার তাগাদা দিলেও পরে অবশ্য কবির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।
মধুসূদন তাঁর এ কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন মাদ্রাসের বিশেষ নামকরা ব্যক্তি জর্জ নর্টনের নামে। তবে এটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু রিচার্ড নেইলরের নামে। কিন্তু গ্রন্থ আকারে প্রকাশের সময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন এটি উৎসর্গ করবেন অ্যাডভোকেট- জেনারেল জর্জ নর্টনকে। কবি তাঁর নামে এ কাব্যটি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অনুমতি পাওয়ার জন্য কাব্যের প্রথম সর্গটি এবং দ্বিতীয় সর্গের কিছু অংশ জর্জ নর্টনের কাছে পাঠিয়েছিলেন পড়ে দেখার জন্য। নর্টন দেখলেন এ কব্যের ভিতর অনেক শক্তি আর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর আছে তাই তিনি আপত্তি করেননি। কবি হয়তো মনে করেছিলেন জর্জ নর্টন এর মতো একজন নামকরা মানুষকে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করতে পারলে মাদ্রাজে বেশ আলোচিত হবে। তাইতো তিনি বেশ বিনয়ীও ছিলেন অনুমতি পাওয়ার জন্য।
কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার পর জর্জ নর্টন কবিকে বললেন: এমন অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতি যে কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি কাব্যটি তাঁর নামে উৎসর্গ হতে দেখে তিনি সম্মানিত বোধ করেছেন।
পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কবি যে প্রেস থেকে তাঁর প্রথম কাব্যটি ছাপিয়েছিলেন মালিক ছিলেন অ্যাবেল সিমকিন্স। তিনি একজন দক্ষ মুদ্রকের পাশাপাশি একজন প্রকাশক। তিনি তাঁর ছাপাখানা থেকে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি একসময় চিন্তা করলেন ইউরেশিয়ানদের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। মাইকেল তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে লেখালেখি করে বেশ পরিচিত হয়েছেন। ইংরেজিও ভালো জানেন। তাই সিমকিন্স মনে করলেন অল্প বেতনে মাইকেল মধুসূদনকে এই পত্রিকাটির দায়িত্ব দেবেন।
১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর মাইকেল মধুসূদনকে সম্পাদক করে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার। পত্রিকাটির নাম Eurasian। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কারণ হলো কবি তখন আর্থিক সংকটের ছিলেন। কন্যার জন্মের পর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে স্কুলের বেতনে চলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাড়তি আয়ের উদ্দেশ্যে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও এই পত্রিকা তাঁর নিজের রচনা প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম হলো। যে কারণে তিনি পত্রিকাটির দায়িত্ব পেয়ে আনন্দিতও হয়েছিলেন। Eurasian পত্রিকাটিকে তিনি খুব আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে কাজ করতেন।
পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ ১০ নভেম্বরের সংখ্যায় তিনি তাঁর জরুরধ Empress of Inde কাব্যনাট্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১২ জানুয়ারি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট নয়টি পর্ব প্রকাশিত হয়েছিলো। এই জরুরধ নাটক রচনার মাধ্যমে কবির নাটক রচনার হাতেখড়ি হলো।
মাদ্রাজ স্কুলে চাকরি করার সময়ে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর এই বক্তৃতাটি পরবর্তীতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো এপ্রিল মাসে। এই পুস্তিকার নাম ‘The Anglo Saxon and the Hindu. Lecture1। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ Spectator পত্রিকাটি সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশের পরিবর্তে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় ‘Madras Spectator’। এই পত্রিকাতে তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন। সহকারী সম্পাদক হলেও তাঁকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হতো। ৯ মার্চ তারিখে মধুসূদন চতুথ সন্তান-দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের পিতা হলেন। এই সময় তিনি অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছিলেন। পত্রিকার চাকরি ও স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মোটামুটি যাচ্ছিল। সংগ্রাম আর নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ তিনি পাড়ি দিয়ে চলেছেন, হঠাৎ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ তারিখ বুধবার বন্ধু গৌরদাসের একটি পত্র হাতে পেলেন। এই চিঠিতে গৌরদাস লিখেছেন-
‘কয়েক বছর পর তোমাকে লিখছি। তোমার এবং আমার যোগাযোগবিহীন নীরবতার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ সময় চলে গেছে, সেটাকে তোমার এবং আমার উভয়ের জন্যে একটা গুরুতর এবং নিন্দনীয় কর্তব্যচ্যুতি বলে বিবেচনা করি। একমাত্র ভগবান জানেন, আমি কতবার তোমার কথা মনে করেছি। আমার চিন্তা যদি কোনো ভাষা না পেয়ে থাকে, তা হলে তার একমাত্র কারণ আমি জানতাম না তুমি কোথায় আছো। তুমি কেমন আছো, সে সম্পর্কেও কোনো কথা শুনতে পাইনি। সর্বত্র খুঁজেও হদিস পাইনি তুমি কোথায় আছো।—- আমি এখন তোমাকে লিখছি এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে তুমি তোমার শৈশব এবং বাল্যকাল-না আমার বরং বলা উচিত-তোমার যৌবনের সবচেয়ে ভালো সময় কাটিয়েছো। আমি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সেটা আমি এক্ষুণি তোমাকে বলছিনে, তোমার উত্তর না পাওয়া পর্যন্তই বলছিনে।—- আমি তোমার প্রতি একটা ভালোবাসা চিরদিন অনুভব করেছি, সে জন্যে তোমাকে ভুলে যেতে পারিনে।—আমি দুঃখিত, তোমার পরিবার সম্পর্কে, বরং যদি বলি তোমার বাবার পরিবার সম্পর্কে, ভালো কোনো খবর দিতে পারছিনে। তুমি বোধহয় অনেক আগেই শুনোছো যে, তোমার বাবা-মা উভয়ই এখন মৃত। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরা কাড়াকাড়ি করছে। তোমার দুই বিধবা বিমাতা বেঁচে আছেন। কিন্তু তোমার লোভী এবং স্বার্থপর আত্মীয়দের কাড়াকাড়ির জন্যে তাঁরা তাঁদের মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়েছেন।’
উল্লেখ্য মাদ্রাজ স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর মধুসূদন কয়েকবার বাড়ি বদল করেছিলেন। যে কারণে গৌরদাসের সাথে মাদ্রাজ যাওয়ার পর বেশ কিছুুদিন যোগাযোগ থাকলেও পরবর্তীতে আর যোগাযোগ ছিলো না। দীর্ঘদিন পর আকস্মিক গৌরদাস বসাকের এই পত্রখানা পাওয়ার পর মধুসূদন ভীষণ কষ্ট পেলেন। বাবা মারা গেছেন ভাবতেই তাঁর বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠলো। কারণ যোগাযোগ না থাকলেও বাবাকে নিয়ে মধুর যে খুব অহংকার ছিলো তার প্রমাণ বিভিন্ন সময়ে পাওয়া যায়। গৌরদাসের চিঠি পড়ার সাথে সাথে তিনি তাঁকে চিঠির উত্তরে লিখলেন-‘তুমি খবর না-দিলে আমার বাবার মৃত্যু খবর আমি হয়তো বছরের পর বছর জানতেই পারতাম না। গৌর, কখন এবং কেমন করে বাবা মারা গেলেন? আমার মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। তুমি যা যা জানতে পারো, আমাকে জানিয়ো। এই চিঠি পাওয়া মাত্র ফিরতি ডাকে আমাকে লিখো।’
এই চিঠিখানা লিখতে লিখতেই মধুসূদন স্থির করলেন আগামী ২৭ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় ফিরবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ফিরতে পারেননি। ওদিকে গৌরদাস মধুসূদনের চিঠি পেয়ে ভীষণ আনন্দিত। তিনি মধুসূদনের চিঠির উত্তর দিলেন ৫ জানুয়ারি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই চিঠিতে গৌরদাস মধুকে সপরিবারে কলকাতায় ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। গৌরদাসের এই চিঠিখানা মধুসূদনকে দেশে ফেরার জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলো। সেই সময় মধুসূদনের সহকর্মী জর্জ হোয়াইট-এর কন্যা হেনরিয়েটার সাথে তাঁর প্রেম চলছিলো। মধুসূদন দীর্ঘ দিনের জন্য কলকাতায় চলে যাচ্ছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের প্রেমের খবরও ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির মধ্যে মধুসূদন স্ত্রী রেবেকা, সাড়ে ছয় বছরের বড় মেয়ে ব্যর্থা, চার বছর দশ মাসের ছোট মেয়ে ফিবি, সাড়ে তিন বছরের বড় ছেলে জর্জ জন ম্যাকট্যাভিশ, আর দশ মাসের ছোট ছেলে মাইকেল জেমসকে রেখে ২৮ জানুয়ারি, সোমবার ৮ বছর ১১ দিনের মাদ্রাজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে কলকাতার উদেশ্যে জাহাজে উঠলেন। ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ফিরে এলেন স্বদেশের মাটিতে।
লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক