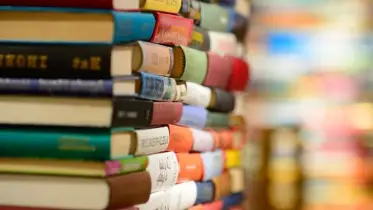‘বল বীর-/বল উন্নত মম শির,/শির নেহারি’ আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!/বল বীর-...উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!’
[ এক ]
পুনরাবৃত্তি ‘বল বীর’ শিরোনাম ও প্রথম পঙক্তিতে। যা একটি কেন্দ্রীয় কাঠামো গড়ে তোলে। ‘বল’ ক্রিয়াপদটি বারবার এসেছে, যা সংগ্রাম, চ্যালেঞ্জ ও আত্মপ্রকাশের প্রতীক। ‘শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির’ এখানে অস্তিত্বকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় তুলে একটি বিপরীত সন্ন্যাস [এ্যান্টিথিসিস], সৃষ্টি করে কবিতার কাঠামোগত শক্তির বেগ প্রবল করা হয়েছে। রয়েছে উচ্চারণগত সমুদ্রগর্জন এবং বাইনারি অপজিন দ্বারা কবিতাটিকে বিশেষ অর্থদ্যোতনা দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ছাড়া এই কবিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভাবগত/বস্তুগত এবং স্বাধীনতা প্রিয়তা ও অর্জনের আকাশচুম্বি মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ যা আমিকে সার্বজনীনতা দিয়েছে। তার আলোচনা যৎকিঞ্চিতও এই পরিসরে উপস্থাপন সম্ভব নয়। কবিতাটি যখন রচিত হয় তখন কবির দুর্দান্ত যৌবন, সারা ভারতবর্ষ উপনিবেশিক শাসনের অধীন। নিৎশের অতিমানব ভাবনার সঙ্গে এই কবিতার দার্শনিক ভাবনার মিল রয়েছে।
লিও টলস্টয় শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখে গেছেন তার ‘হোয়াট ইজ আর্ট’ গ্রন্থে। তিনি বিশ^াস করতেন ‘শিল্পের মূল সত্য মানবিক সংযোগ সৃষ্টি করা, মানুষের অনুভূতি মানুষের সঙ্গে যুক্ত করা’। একজন শিল্পী যে অনুভূতি তার সৃষ্টিতে উন্মুক্ত করেন, সমাজ সংযোগে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত, পাঠক/শ্রোতা/দর্শক সেই অনুভূতির সঙ্গে তার আবেগ ও কল্পনার জগত তৈরি করে এবং আত্ম-অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। অয়নীয় দার্শনিকরা প্রকৃতি, বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হেরাক্লাইটাস বিশ্বাস করতেন, ‘সব কিছু প্রবাহিত হচ্ছে’। কবিতা কেবল ভাষার প্রকাশমাত্র নয়, বরং এটি মানুষের বোধ ও উপলব্ধির গভীর সত্যকে ধারণ করে। তিনি হোমারের সমালোচনা করেছিলেন এজন্য ‘হোমার এবং হেসিয়ড মিথ্যার কাব্য রচনা করেছে।’ জেনোফিনিস হোমার ও হিসিয়ডের কাব্যেরও কঠিন সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন দেবতাদের নিয়ে এই সব কাহিনী মানুষের নৈতিক বিকৃতি ঘটায়।’ ‘কবিরা যখন দেবতাদের চুরি, ব্যভিচার ও প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত করেন, তখন তারা নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটান’। তার মতে ‘কাব্য যদি সত্য ও যুক্তিনির্ভর হয়, তবে তা মানুষের জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে।’ আধুনিক সময়ের দার্শনিক আলবেয়ার ক্যামুর মতালোকে ‘মানুষ জীবনের অর্থ খোঁজে, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র সেই অর্থ দিতে অক্ষম’ এরূপ দ্বন্দ্বের ফলে মানুষ এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায়, কারণ সে আশা করে যে তার জীবন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।’ ফলে, অস্তিত্বই এক ধরনের ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ পরিস্থিতি সমাজে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে এবং একজন ব্যক্তিমানুষ পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে সৃষ্টিশীল মনে বৃত্তি হারিয়ে ফেলে এবং সৃষ্টির লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটে।
[ দুই ]
‘শিল্প এমন হওয়া উচিত, যা সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে।’ [টলেস্টয়] তাঁর ‘দ্য ডেথ অফ ইভান ইলিচ’ উপন্যাসে ইভান ইলিচ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে উপলব্ধি করেন, জীবন আসলে কৃত্রিমতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার কাহিনী নয়। উপন্যাস দেখায়, সমাজে সম্পর্কগুলো প্রথাগত ও স্বার্থনির্ভর হয়ে উঠলে মানুষ একাকীত্বের সংকটে পড়ে। ‘নৈতিক ও নৈতিকতাবিরোধী’ শিল্পকে তিনি ‘শিল্প’ বলে স্বীকৃতি দিতে চাননি। দার্শনিক প্লেটো তার ‘দ্য রিপাবলিক’-এ ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন, ‘যেখানে শাসকের নৈতিকতা নিশ্চিত করাই সমাজের সামগ্রিক ন্যায়ের শর্ত’। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে কাব্য ও শিল্পের প্রতি সন্দিহান ছিলেন, কারণ শিল্প মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করে ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। টলস্টয়ের ধারণা প্লেটোর বিপরীত; তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘প্রকৃত শিল্প রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামোকে প্রশ্ন করে এবং সমাজকে জাগিয়ে তোলে।’ কেবল রূপ-সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্ট শিল্পকর্মের প্রতি মহামতি টলেস্টয়ের তেমন আগ্রহ ছিল না; বরং তিনি চাইতেন, শিল্প এমন কিছু হোক যা সমাজকে ন্যায় ও নীতির পথে চালিত করবে। এই ন্যায় ও নীতি মূলত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত। টলস্টয়ের ‘নৈতিক শিল্প’ ধারণা কেবল শিল্পের আদর্শিক দিক নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নৈতিক অবস্থানকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। [শিল্পের স্বরূপ] কোনো সমাজের শাসনব্যবস্থায় অন্যায় ও অসাম্য প্রতিষ্ঠা পেলে শিল্প-সাহিত্য যে নিছক শাসকের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয় তার উদহরণ আমাদের সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রশ্ন হলো বাস্তবে রাষ্ট্র কতটা জনগণের রাষ্ট্রীয় [যার মালিক জনগণ বলা হয়?] দায়িত্ব পালন করে? গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও কেবল মাত্র ভোট নামক প্রহসন দ্বারা নেতা নির্বাচন করা ছাড়া আর কোনো মালিকানা দৃশ্যমান নয়, সেটাও প্রায়শই জনগণের হাতছাড়া থাকে। কেবল কর্তৃত্ববাদী শাসকের রাষ্ট্র শাসক ও তার শ্রেণির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তারা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমন কী শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও কর্তৃত্ববাদিতা থেকে রেহাই পায় না। এর ফলে অধিকাংশ শিল্পী কবির সৃষ্টিতেও জটিলতার উদ্ভব ঘটে, অনেকে নিষ্কৃয় হয়ে পড়ে। আবার অনেকের সৃষ্টিতে দুর্বোধ্যতা, যৌনতা, পরাজীবন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্তুতি, গণবিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। কর্তৃত্ববাদী শাসন জনাকাক্সক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং জনশক্তির নির্মম অপচয় ঘটায়। অনৈতিক শাসন, গণতন্ত্রহীনতা ও বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে প্রথমেই সমাজের যে অংশ বিদ্রোহের উপস্থিতি ঘটায় তারা কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ। তারাই চেতনাকে সামাজিক জলাশয়ে আবর্তের মতো ছড়িয়ে দেয়, যা আস্তে আস্তে কুল অবধি পৌঁছায়। আবর্ত যেমন দীর্ঘ যাত্রায় সরু চিকন হয়ে কুলে লগ্ন হবার মধ্যেই প্রায় অদৃশ্য থাকে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য চেতনা খুবই নীরবভাবে সমাজ মনে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। একটা সময় পর্যন্ত তার উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় আমরা দেখতে পাই কাঠামোগত শক্তির প্রবল বেগ। আলোচ্য কবিতাটিতে রয়েছে উচ্চারণগত সমুদ্রগর্জন এবং বাইনারি অপজিন দ্বারা কবিতাটিকে বিশেষ অর্থদ্যোতনা দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ছাড়া এই কবিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভাবগত/বস্তুগত এবং স্বাধীনতা প্রিয়তা ও অর্জনের আকাশচুম্বি মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ ‘আমি’র সার্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। কবিতাটি যখন রচিত হয় তখন সারা ভারতবর্ষ উপনিবেশিক শাসনের করতলগত। নিৎশের ‘অতিমানব’ ভাবনার সঙ্গে এই কবিতার দার্শনিক ভাবনার মিল রয়েছে।
[ তিন ]
‘শিল্প এমন হওয়া উচিত, যা সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে।’ টলেস্টয়ের ‘দ্য ডেথ অফ ইভান ইলিচ’ উপন্যাসে ইভান ইলিচ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে উপলব্ধি করেন, জীবন আসলে কৃত্রিমতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার কাহিনী নয়। উপন্যাস দেখায়, সমাজে সম্পর্কগুলো প্রথাগত ও স্বার্থনির্ভর হয়ে উঠলে মানুষ একাকীত্বের সংকটে পড়ে। ‘নৈতিক ও নৈতিকতাবিরোধী’ শিল্পকে তিনি ‘শিল্প’ বলে স্বীকৃতি দিতে চাননি। দার্শনিক প্লেটো তার ‘দ্য রিপাবলিক’-এ ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন, ‘যেখানে শাসকের নৈতিকতা নিশ্চিত করাই সমাজের সামগ্রিক ন্যায়ের শর্ত’। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে কাব্য ও শিল্পের প্রতি সন্দিহান ছিলেন, কারণ শিল্প মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করে ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। টলস্টয়ের ধারণা প্লেটোর বিপরীত; টলেস্টয় বিশ্বাস করতেন, ‘প্রকৃত শিল্প রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামোকে প্রশ্ন করে এবং সমাজকে জাগিয়ে তোলে।’ কেবল রূপ- সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্ট শিল্পকর্মের প্রতি মহামতি টলেস্টয়ের তেমন আগ্রহ ছিল না; বরং তিনি চাইতেন, শিল্প এমন কিছু হোক যা সমাজকে ন্যায় ও নীতির পথে চালিত করবে। এই ন্যায় ও নীতি মূলত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত। টলস্টয়ের ‘নৈতিক শিল্প’ ধারণা কেবল শিল্পের আদর্শিক দিক নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নৈতিক অবস্থানকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।
[ চার ]
কোনো সমাজের শাসনব্যবস্থায় অন্যায় ও অসাম্য প্রতিষ্ঠা পেলে শিল্প-সাহিত্য যে নিছক শাসকের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয় তার উদহরণও আমাদের সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। শিল্পীর মুক্তি গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সম্ভাবনা থাকলেও কেবল মাত্র ভোট নামক প্রহসন ছাড়া আর কোনো মালিকানা জনগণের তো নেই। কর্তৃত্ববাদী শাসকের রাষ্ট্র, শাসক শ্রেণির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তারা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে এমনকী শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও কর্তৃত্ববাদীতা থেকে মুক্ত থাকে না। এর ফলে অধিকাংশ শিল্পী কবির সৃষ্টিতেও জটিলতার উদ্ভব লক্ষ করা যায়। অনৈতিক শাসন, গণতন্ত্রহীনতা ও বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নৈতিক ভাবে প্রথমেই সমাজের যে অংশ বিদ্রোহের উপস্থিতি ঘটায় তারা বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাদখলের মনেবৃত্তিতে জনমনোকাঙ্খাকে রাজনৈতিক রূপ দেয়, মানুষের চেতনাকে তাদের স্বার্থে পরিচালিত করে। তাই শিল্প-সাহিত্য যদিও ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যতা থেকে সৃষ্টি তারপরও তা ‘সামাজিক চৈতন্যের রূপায়ন’। কারণ ‘মানুষের চেতনা তার সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ণিত হয়’।