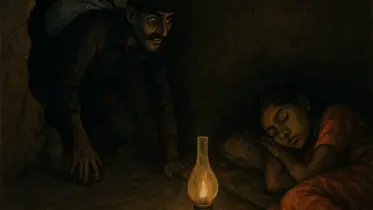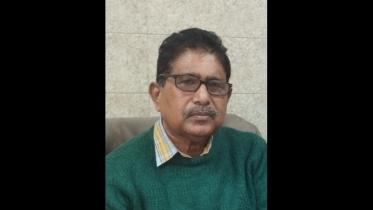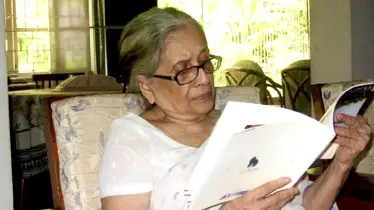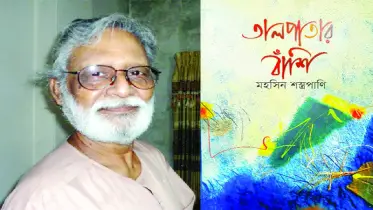আইয়ুব আল আমিন
বাঙালির অস্তিত্ব-অবস্থান-স্বপ্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লেখচিত্র করা না-গেলেও বাঙালির জীবন-প্রবাহের ক্রমবিকাশ লিখতে গিয়ে প্রথমেই ভাষার উদ্ভব ও ভাষার দীর্ঘ পরিভ্রমণ-পরিধি নিয়ে বিশেষ উপস্থাপন দরকার। অন্যদিকে স্বীকার করছি, অত সহজ নয় সে কাজটি।
এ জাতির সংস্কৃতিকে লক্ষ্য করলে যতটা বৈচিত্র্য ধরা পড়ে সেসবের সমন্বয়ে বাঙালি সংস্কৃতি যে স্বতন্ত্র চেহারা পেয়েছে- তা বিশেষত ভাষার স্বকীয়তায়। বাংলা ভাষার। এ ভাষা অগ্রসর হয়েছে, পরিণত হয়েছে, গভীর হয়েছে- কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ ছিলই। রাষ্ট্রের সাহায্য যতটা পাওয়ার কথা, ভাষা কি তা কোনোকালে পেয়েছে! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এগোতে হয়েছে ভাষাকে।
ইতিহাসে দেখা যায় বাংলায় পালবংশের রাজত্বকালে বাঙালি থাকা সত্ত্বেও বাংলার কোনো স্থান ছিল না রাজসভায়। অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সংস্কৃতের ব্যবহার। এরপর সেনদের আগমন। অবাঙালি।
পাঠান ও মুঘল আমলেও রাজভাষা ভিন্ন। ইংরেজরা এসেও চাপাল তাদের ভাষা। তার মধ্যে বাংলা ভাষার উঠে দাঁড়ানোর উন্মুখতা। তবে তা- সাধারণ মানুষের, ব্রাত্যজনের, অবহেলিত জনগণের মুখের ভাষায়। রাজদরবারে যে ভাষা চালু থাকে তা সম্ভ্রান্তজনের ভাষা, যা ভক্তিতে যতটা অনুকরণীয় তারও বেশি ভয়ে। এই ভয়মিশ্রিত ভক্তি এবং কতিপয় সুবিধাভোগীর খানিকটা জাতে ওঠার লোভ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বংশপরম্পরায়।
একের পর এক শাসনামল এসেছে কিন্তু বাংলার মূলধারা কখনোই আত্মসমর্পণ করেনি, বাংলাকে এগোতে হয়েছে বিদ্রোহ করেই। মধুসূদন ইংরেজি প্রত্যাখ্যান করে প্রবেশ করলেন বাংলায়। রাজা রামমোহন ইংরেজিতে লিখলেও তার চর্চা বাংলার। বিদ্যাসাগরের সামাজিক বিদ্রোহের পাশাপাশি ভাষাগত বিদ্রোহ ছিল প্রকট। বঙ্কিম তার ভেতরের বিদ্রোহ দিয়েই বাংলায় উপন্যাস শুরু করেন। ইংরেজ চলে গেল, বঙ্গ ভাগ হলো, উর্দুর দাপট গলা চেপে ধরে বাংলা ভাষার। আবারও বিদ্রোহ। তবে আগের চেয়ে তীব্র।
শতাব্দীকালের বাঙালিকে প্রকারান্তরে যদি দেখি- হতদরিদ্র-শ্রমজীবী শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নারী ও সংখ্যালঘু ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমস্যাসংকুল জীবন অতিবাহিত করছে। দৃশ্যত সমস্যাগুলো মাত্রায় তফাৎ, সজ্ঞায় তফাৎ। কিন্তু অন্তরবস্তুতে অভিন্ন। কেউ ভালো নেই। এই যে ভালো না থাকা আক্রমণে তারা এক হয়ে যায় একইসূত্রে। ভূমিদস্যুদের দ্বারা ভূমিহীন হচ্ছে কৃষক। তারা ভিটেমাটি ছেড়ে জীবিকার জন্য শহরে পাড়ি জমায় উদ্বাস্তু হয়ে। ফলে তাদের ভাষাও উদ্বাস্তু। শহরে তাদের ভূমি গৃহ কোথায়! তাদের ভাসমান জীবন যাপন শুরু হয় বস্তিতে। ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও বাস্তুচ্যুত। বাংলা ভাষা হারাচ্ছে ভাষার বৈচিত্র্য ও সম্পদ।
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভাগ করেছে মানুষ ও মাটিকে। বিচ্ছিন্ন করে তুলছে বাঙালিত্ব থেকে। শুধু হিন্দু বাবুরা নন, মুসলমানেরাই বিব্রত মৌলবাদীদের আগ্রাসনে। ভারতের বাঙালিরা ভারতীয়; প্রাদেশিক। বলা যায় বাংলাদেশের সব বাঙালি উদ্বাস্তু। মধ্যবিত্তরা বাঙালি হতে চায়, ভালো কথা। উচ্চবিত্তরাও তো চায়! বিশেষ দিনে সানকিতে করে পান্তা ভাত খাওয়ার জন্য মরিয়া হয় বাঙালি হওয়ার আগ্রহে।
গরিব মানুষ গরিব হয় তো নিরুপায় হয়ে। কিন্তু ধনীরা কেন গরিব হওয়ার চেষ্টা করে! আমরা কি এমন দিন দেখব না যে- বাঙালি হওয়ার জন্য সানকি আর পান্তার আবশ্যকতা থাকবে না! ব্যাপারটা এমন- গরিবদের গরিব থাকা অবধারিত। এবার যদি আসি, বিদেশী ফ্যাশনের পোশাক দখল করেছে বাঙালির হাটবাজার। তাহলে অবশিষ্ট ভরসা নিহিত ভাষার ভেতরে। বাংলা ভাষা। এত উত্থান পতন যুদ্ধ ঝড়ঝঞ্ঝা সংকটের পরে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলেও রাষ্ট্রের উপর কি বাঙালির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে!
ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বাঙালি যে উদ্বাস্তু তার সাক্ষ্য- ডিশ এন্টিনা ও ইউটিউব ভিডিওর কল্যাণে আজকে আমরা সারা বিশ্বকে দেখি। কিন্তু বিশ্বের কেউ দেখে না আমাদের। খোঁজ রাখে না, যদি না ঝড়ে, বানে বা ভূমিকম্পে মরণাপন্ন হই।
একইভাবে অনুবাদ সাহিত্যের অগ্রগতিতে বিদেশী সাহিত্য বাঙালি পড়ছে। বাংলার কতটুকু কি জানছে বিদেশীরা? ছিটেফোঁটা যা হচ্ছে তা ব্যক্তিক আত্মপ্রচার। সেটা হোক; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করবে এমন কিছু হয়েছে বা হচ্ছে অনুবাদ!? আমাদের মানিক, শওকত আলী, ইলিয়াস, ওয়ালিউল্লাহ চলে গেছেন। তাদের রচনা কি এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়! সেসব অনুবাদে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কোথায়! বাংলা একাডেমিতে কিছুই হচ্ছে না যেমন নয়, কার্যকরী কিছু হচ্ছে না, সেটাও সত্য।
বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে বলতে গেলে বাঙালি ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ অপরিহার্যরূপে সম্মুখে আসবে এ আর নতুন কি! বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ ধরে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্র আবার ইংরেজির দিকে ঝুঁকেছে, কেননা- অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশ মোটেই স্বাবলম্বী নয়। পরনির্ভরতার প্রেক্ষিতে ঋণ-সাহায্যে এনজিওর তৎপরতা বেড়ে গেছে দিনে দিনে। বিশ্বব্যাংকের ভাষা তো আর বাংলা নয়! কতিপয় আমলা আর উচ্চবিত্তের সন্তানরা তাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে। বাঙালি অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষই বাঙালি। খাঁটি বাঙালি। বাংলা তাদেরই ভাষা।
ধনী অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ বাঙালি থাকতে চায় না। বিদেশী পণ্য ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষাও ব্যবহার করে তারা। তাদের আদর্শ পুঁজিবাদী বিশ্ব। উদ্যাপনেও পশ্চিমা রীতি। আবার বাস্তবতা এমন যে- বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজিকে আর হঠানো যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য আর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন থাকেই।
প্রভাতফেরি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ অতিপ্রত্যুষে খালিপায়ে মানুষ বেরিয়ে পড়তো রাজপথে- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’ গানটি সমস্বরে গলায় তুলে। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল দিত শহীদ মিনারে। অথচ এখন অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে যেটা উদ্যাপন হয় সেটা প্রভাতে শুরু হয় না। শুরু হয় রাত বারোটা এক মিনিটে, মধ্যরাতে। সেই সারিতে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণে বিঘœ ঘটা স্বাভাবিক। এই যে মধ্যরাতের শুরু তো ইউরোপীয় প্রথা। সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ পর্যুদস্ত হয়েছে কতিপয়ের সুবিধা-স্বার্থে।
অস্তিত্বের প্রসঙ্গে বাঙালির ভবিষ্যৎ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশেই। কেননা অবিভক্ত বঙ্গে এই দেশ পশ্চাৎপদ থাকলেও এখন পশ্চিবঙ্গের বাঙালি হিন্দির আগ্রাসনে বিপন্ন। অন্যদিকে বাঙালি ভয় পায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। এটা তার ঐতিহাসিক গ্লানি। অতীতে বাংলা ভাষার জন্য বরাদ্দ ছিল অবজ্ঞা, অবহেলা। বাংলা অভিজাতদের ভাষা ছিল না কখনো। তবে ভাষার প্রতিবাদী চরিত্র শুধুমাত্র অতীতের ব্যাপার নয়। বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও।
বর্তমানে ভাষার অদ্ভুত ব্যাবহার বড় শোচনীয়। একটা বাক্যের এক তৃতীয়াংশ ইংরেজি, এক তৃতীয়াংশ হিন্দি, বাকিটুকু বাংলা। সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিও বলে না, শুদ্ধ শব্দে বাংলাও বলে না। দুটো মিশিয়ে বলে, পাছে শুধু বাংলায় অনাধুনিক গেঁয়ো তকমা লাগে! এ ব্যাধি অল্প কিছু লোকের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংখ্যার বিচার করে লাভ নেই। কারণ এই অল্পসংখ্যকদের অন্যরা অনুকরণ করে।
এ ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় আছে, যদিও তা কতটা কার্যকর বর্তমান পরিস্থিতিতে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা- বাংলা ভাষা ও বাঙালির বর্তমান দুর্দশার কারণ এক ও অভিন্ন। সেটা হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদই আমাদের অবাঙালি করছে। যদিও পূর্ব হতেই অধিকাংশ বাঙালি বাঙালিত্ব নিয়ে কখনই গর্ব করেনি ততটা সচেতনভাবে, যতটা অবচেতনে ঘটেছে। কেবল আক্রমণ এলে বাঙালি সজাগ থেকেছে অধিকারের প্রশ্নে। বাংলাদেশে এখন ধনীরা বাংলা ব্যবহার করে না। গরিবরা ব্যবহার জানে না। এখন বাংলা যেন মধ্যবিত্তের নিরুপায় উচ্চারণ। অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষার মানুষেরা পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে জীবিকার তাগিদে শহরমুখী বিধায় আঞ্চলিক ভাষাও ভুগছে অস্তিত্ব সংকটে।
অবশিষ্ট বাঙালিপনা থাকল ভাতে। মোটা চালের ভাত নিজে খাই বলেই বলছি। যেটার সঙ্গে কৃষকের প্রত্যক্ষ সংযোগ। কৃষকের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি নেই। যে দেশে মাঠের ধান ঘরে তোলার খরচের চেয়ে ধানক্ষেত আগুনে পুড়িয়ে কৃষককে মুক্ত হতে হয়, সে দেশে মহাজনকে কৃষক ঘৃণা করে। কিন্তু সা¤্রাজ্যবাদকে আজ আমরা ঘৃণা করি না। কৃষকের শত্রু যে সামন্তবাদ, তারই রক্ষাকর্তা সা¤্রাজ্যবাদ।
দেশে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করার জন্য নানা শ্রেণির গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কোনো গোষ্ঠী নেই। সাধারণ মানুষের কোনো সংগঠন দেশে নেই। থাকলে টিসিবির গাড়ির পেছনে পেছনে হাজারও কান্নার রোল বাতাস ভিজিয়ে তুলত না। আমাদের আরেকটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা হলো প্রতিবাদের ভাষা। অস্বীকার করার জো নেই যে- দারিদ্র্যের সঙ্গে মৌলবাদের যোগসূত্র আছে। এ কথাও ঠিক- দারিদ্র্যের সংজ্ঞা আপেক্ষিক; কিন্তু তবু দারিদ্র্য যে কি জিনিস বাংলাদেশের মানুষ ভালোমতো বোঝে। দারিদ্র্য তো আজকের নয়, যুগযুগান্তের। এই অন্তহীন দারিদ্র্য ব্যক্তির জীবনে এমন অভ্যাস তৈরি করে রেখেছে যে ঈর্ষা অবিশ্বাস ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহ ঝগড়া ফ্যাসাদ নিত্যসঙ্গী হিসেবে পর্যবসিত।
কাজেই দারিদ্র্য যখন সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম কাটে না। দরিদ্র মানুষের ভরসা করার মতো আশ্রয় নেই, বিচার নেই, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নেই, কতভাবে উদ্বাস্তু হয় এ রকম মানসিক অবস্থায় ইহজাগতিক চর্চা কিভাবে সম্ভব! মানুষ যে ইহকালের ভাবনা ছেড়ে জীবিত অবস্থাতেই পরকালের দিকে ভীষণভাবে ধাবিত হতে পছন্দ করে, তার কারণ ইহকালেরই দুরবস্থা।
তো অভাব, দারিদ্র্য, দুরবস্থা এ সকল অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ব্যাধির জন্য দায়ী কি? নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না, তা হলোÑ অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রভাবশালীর দুর্নীতি, ধনীর ভোগবাদিতা। আদতে এ ব্যাধি কি আর সারবে! পুঁজিবাদী বিশ্ব জিইয়ে রাখতে চায় এ ব্যাধি। সাম্প্রদায়িকতা ঘোচানোর চেষ্টাও নেই। তার গভীরতর কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদ মৌলবাদের বিকাশের অন্যতম প্রধান উৎস। মানুষ ধর্মপ্রাণ, অদৃষ্টে বিশ্বাসী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্তরালে যে প্রচ- অবিশ্বাস লুকিয়ে আছে সেটা অসত্য নয়। ধর্মে আস্থা রাখার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে জগতের প্রতি আস্থাহীনতা। অধিকাংশ মানুষ সংকটকালে দৈব শক্তির উপরে ভরসা করে।
আমাদের সংস্কৃতিতে বিবিধ মানবিক গুণ রয়েছে যেমন- সামাজিক প্রীতি, ধর্মে-বর্ণে অসাম্প্রদায়িকতা। এ কথা জোর দিয়ে বলব- মানুষ সাম্প্রদায়িক থাকতে চায় না। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা কোনোটিই সংঘবদ্ধতা চায় না। চায় বিচ্ছিন্নতা। বাঙালির রক্তে এখন সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ প্রবাহ।
আর ওই যে ‘বিশ্বায়ন’ শব্দটি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। বিশ্বায়ন কি বাংলাদেশকে বিশ্বের দিকে নিচ্ছে? না-কি পুঁজিবাদী বিশ্বকে আমাদের দেশে আনাচে-কানাচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন!
গত পঞ্চাশ বছরে জাতি গঠন বিষয়ক নানা কথা হয়েছে, কিন্তু বড় সত্য হলো- জাতি নয়, গঠিত হয়েছে শ্রেণি। যে জিনিসটা খুবই দর্শনীয়রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে তা হলো বিদেশে গমনে আগ্রহ। শ্রমজীবীরা বিদেশে গেলে ক্ষতি নেই বরং লাভ। কেননা তারা অর্থ পাঠাবে বিদেশ থেকে। ক্ষতি বিত্তবানদের (রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী) যাওয়াতে। এরা বিদেশে গিয়ে দেশের টাকা খরচ করে বাড়ি কেনে।
বাংলাদেশের বিস্তর মানুষ এখন বাইরে। কিন্তু কোন মানুষকে বলা যাবে দেশের প্রতিনিধি? অল্প কয়েকজন পাওয়া যাবে- লেখাপড়ায় দক্ষতায় যোগ্যতায় অগ্রসর। সেই অল্প কয়েকজন কি দেশবাসীর মুখপাত্র? বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়, নিষ্প্রভ বলা চলে। উজ্জ্বল মানুষেরা এর দায়ভার বহন করতে যাবেন কেন! বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসন্ধানের আদর্শবাদ কাজ করছে এখন। আর একেবারেই অর্থ উপার্জনের জন্য যারা গেছেন তাদের তো সময়েরই অভাব এসব ভাববার।
বাঙালির মর্মান্তিক সত্য যন্ত্রণা- আকাশে উঠতে থাকা দ্রব্যমূল্য। মূল্য যতই বৃদ্ধি পাক কতিপয় বিত্তবানের (দেশের মানবিক-¯œায়ু গঠন, সমাজের মনন বিকাশ নিয়ে যাদের মাথাব্যথা নেই তাদের মানুষ বলতে ভালো লাগছে না, প্রাণী বলাই যথার্থ) ভোগবিলাসে বাধা পড়ে না। এখনো আমরা ধরে নিই পুঁজি আসবে বিদেশ থেকে। সাহায্য, ঋণ সব বিদেশীরাই দেবে।
দ্রব্যের এই উচ্চমূল্যের বাজারে অভাব যে কত মাত্রায়, কত গভীরে বেশিরভাগ মানুষ টের পাচ্ছে, কিন্তু কোনো উচ্চারণ নেই এই বিষয়ে। কি অদ্ভুত! প্রথমেই ধরি যদি উৎপাদন কম হয়; তাহলে উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় কী এবং কারা? অবশ্যই দরিদ্র মানুষ নয়। দরিদ্র মানুষ শ্রম করতে চায়। অভাব শ্রমের নয়, অভাব হলো পুঁজির। আমাদের অর্থনীতি পুঁজিবাদী কিন্তু এখানেও পুঁজিরই অভাব। অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত কম। যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকছে- অধিপতি শ্রেণির জন্য কোটি কোটি টাকার ঘরবাড়ি, সুইমিংপুল করতেই কাজে লেগে যাচ্ছে। তার মানে উৎপাদনের রাজনীতি অনুৎপাদক শ্রেণিকে দিয়ে হওয়ার নয়।
সবকিছুকে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলে দেওয়ার যে ব্যবস্থা বা সুপারিশ বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অনবরত করছে এটাই এখন নীতি। এই নীতিতে বাংলাদেশও দীক্ষিত। ব্যক্তিগতকরণের উন্মত্ততায় সমষ্টিগত কাজ তলানিতে। বিপন্ন মানুষের দুঃখ নিরসনে মানবাধিকার সংগঠন, সিভিল সোসাইটি, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও অনেককিছু তৎপর, কিন্তু তারা কেউই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। তাদের কাজ এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। শোষণ আগেও ছিল, কিন্তু বর্তমানের মতো এমন সুনসান নীরব থাকার নজির নেই। বাঙালি স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি হলো কই! দিন দিন চুপ হয়ে পড়ছে বাঙালি। যদি চাকরি চলে যায়, যদি কর্তাবাবুরা বিরূপ হয়! অথচ কত অজ¯্র কথা বাঙালির বলার কথা! স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বস্তুবাদী।
ক্ষুধা অভাব অনিবার্যভাবে বস্তুবাদী করে রেখেছে- দার্শনিক অর্থে নয়, স্থূল ও বৈষয়িক অর্থে। অন্তরে ভয় ও লোভ। আধ্যাত্মিকতা নয়। স্থূল বস্তুবাদিতা মানুষকে এত বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, দার্শনিক বস্তুবাদিতার স্থান পাওয়া কঠিন।
আজকাল মানুষ সাঁকো খোঁজে না, খোঁজে সিঁড়ি। মানুষকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় সাঁকো। সাঁকো দুপ্রান্তকে মেলায়। সিঁড়ি দেয় ব্যবধান। বৈষয়িক উন্নতির আশাগ্রস্ত মানুষকে সিঁড়ি ক্রমাগত উপরের দিকে নিয়ে যায়, তাতে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় সেটি সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর। বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে শত্রুতা হয় বিশ্রি উপায়ে। অধিকাংশ মানুষকে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ রেখে। অধিকাংশ মানুষ কেবল অশিক্ষিতই নয়, রাজনৈতিকভাবে অশিক্ষিত। উপরন্তু তারা (শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয়ই) বাঁচার সংগ্রামে বিধ্বস্ত। আনন্দ-সমাগম হোক কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ; মানুষ ভিড় করছে ঠিকই, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। অর্থনীতির বিপন্নতা মোকাবিলার সামর্থ্য, জ্ঞান ও জাতিগত ঐক্য ভীষণ জরুরি হয়ে উঠেছে বাঙালির জন্য।