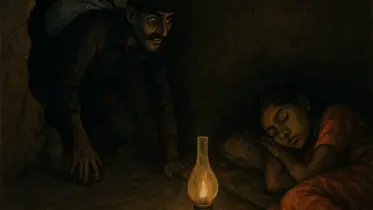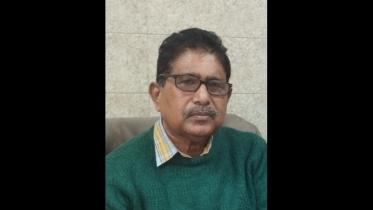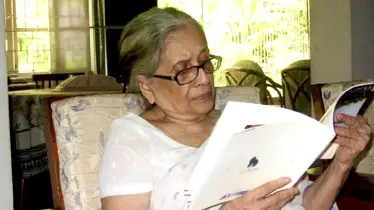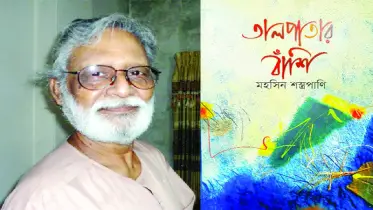কবি-কথাশিল্পী-শিশুসাহিত্যিক-সাংবাদিক আহসান হাবীব (জন্ম : ০২ জানুয়ারি ১৯১৭, মৃত্যু : ১০ জুলাই ১৯৮৫) বাংলা কবিতাচর্চা আর কবিতাযাপনে এক অনন্য পরিচর্যাকারী হিসেবে আজ প্রায় সর্বমহলে তর্কাতীতভাবে সমাদৃত। শিল্পকর্মে রুচিশীলতার লালনকর্তা-প্রশ্রয়দানকারী হিসেবেও তাঁর মর্যাদা ঈর্ষণীয়। লোভ আর অস্থিরতা-প্রবণতাকে তিনি শিল্পের প্রতিকূল শক্তি বলে জানতেনÑমানতেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যচিন্তা আর ইতিহাসজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন নির্বিকার চিত্তে। স্থায়ুবিভ্রান্তির সর্পিল দিনের যাত্রাপথে কবি হাবীব ইতিহাসের আলো দেখেছেন; দেখেছেন ইতিহাসের খেড়োখাতার পাতায় পাতায় অনাগত বিস্তার আর বিকাশের আহ্বান। বিশ শতকের সমাজ আর রাষ্ট্রগতিকে তিনি অবলোকন করেছেন; অনুধাবন করেছেন। লিখছেন : ‘বিংশ শতকী সভ্য দিন-/শাণিত কৃপাণ শঙ্কাহীন/শস্যে হানবে শুনো ক্ষেতে তার হবে স্বার্থের হীন জরিপ/নীল রক্তের অভিশাপে ঘেরা জাগে নিপিষ্ট রিক্ত দ্বীপ।’ বৈপ্লবিক যুগে’ ভূমিজ-উৎপাদনবিমুখ যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার কালো ধোঁয়া যে প্রকৃতপক্ষেই ঋণশোধের রাজনীতির ফল; উন্নয়নের আর পরিবর্তনের রাজনীতি যে এটা নয়Ñ তা তিনি বুঝতে কালমাত্র বিলম্ব করেননি। প্রখর সমাজসচেতন-রাজনীতিমনস্ক-পরিবর্তনপ্রত্যাশী কবি আহসান হাবীবের কর্মপ্রয়াসে তাই অনিবার্যভাবে নির্মিতি লাভ করেছে রাষ্ট্রের-সমাজের বিচিত্র প্রবণতা আর মানব চরিত্রের বিবিধ গতিপথ। অবলোকন-অনুভব-অভিজ্ঞতাÑ এই তিনের সমষ্টি তাঁর সমূহ প্রকাশের ভার বহন করেছে শিল্পী জীবনের প্রেরণা-শ্রান্তি-অভিঘাত আর অপ্রতিরোধ্য অগ্রগমন-কাতরতায়। তিনি ভাবেন : ‘আছে সেই অনাগত দিন/হাতে আছে সেই সূর্য-পরিক্রমা স্বপ্ন রঙিন।’
এই স্বপ্নবাজ-আশা জাগানিয়া কবি আহসান হাবীব জন্মভূমিতে ভিনদেশী বণিক-শাসকদের দীর্ঘদিনের শোষণ-অত্যাচার আর দেশবাশীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাসের আলোকশলাকা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞ জীবনবাদীর অবস্থান থেকে। বিশ শতকের জাগরণ-পুনর্জাগরণের চেতনা যে আমাদের পরাধীনতার বিরান-গ্রাম থেকে অন্য সবুজ-গ্রামে স্থানান্তর করার সময়সেতু, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর ভারত-বিভাগের প্রাক্কালে। রাষ্ট্রের অবমুক্তি আর মানুষের স্বস্তি প্রসঙ্গ তাই তাঁর কাব্যভাবনার উপাদান হয়েছে অনিবার্যভাবে। হাবীব লিখছেন : ‘দ্বারপ্রান্তে তোমাদের বন্দী আমি দুই শতকের,/আমার আত্মার তলে অগ্নিশিখা সাতান্ন সনের/আজো অনির্বাণ,/তবু কি পাহারা দেবে হাসিমুখে আমার জিন্দান?’ (সেতু-শতক) যুদ্ধচলাকালে সাধারণ মানুষের দিনলিপি যে সাধারণ থাকে নাÑ ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক জীবনে পারিপার্শ্বিকতার প্রবল চাপ পড়ে; অর্থনৈতিক প্রসঙ্গাদিতে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগ, তার বাস্তবতা আঁকতে গিয়ে কবি আহসান হাবীব লিখেছেন যুদ্ধ এবং যোদ্ধার পরিচয়-পঞ্জিকা। পরোক্ষভাবে যুদ্ধের প্রভাব পড়ে যাদের ওপর, তারাও যে যোদ্ধা-মর্যাদার দাবিদার সে বিষয়ে কবির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ও বিশ্বাস্য। তাঁর ভাষ্য :
মাসান্তের মাসোহারা অর্ধেক বিলিয়ে দেই
একটি বস্ত্রের বিনিময়ে,
কাগজ-কলম কেনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে
খোকাদের যেতে দেই ব’য়ে।...
আবার আসবে সন্ধ্যাÑ
আবার প্রতীক্ষা আর আবার দেহের রক্ত
বিন্দু বিন্দু ক্ষয়;
একি যুদ্ধ নয়! (সৈনিক)
গ্রামের সমাজ-অর্থনীতির ক্রম-পরিবর্তন, নগরায়নের ফলে গ্রাম জীবনের প্রায়-বিলুপ্ত লোকাচার তাঁকে বিচলিত করেছে; করেছে ভাবনাক্লান্ত। নীলচাষ, কারখানা-সভ্যতার বিকাশ আর নগরজীবনের আপাত আরাম-আয়েশ যেন কেড়ে নিয়েছে গ্রামের প্রকৃত শোভা; আসল সৌন্দর্য। শান্ত-নিবিড়, শস্য স্রোত গ্রাম- উৎপাদনমুখী কৃষি-ব্যবস্থা, হাজার হাজার বছরে ধাপে ধাপে তৈরি হওয়া গ্রামীণ সংস্কৃতি আর গ্রামনির্ভরতা এসব যে প্রকারান্তরে নগর-সংস্কৃতির লালনভূমি তা বোধ করি আমরা মাঝে মাঝে ভুলতে বসি। কিন্তু কবি জানেন, মানুষের আসা-যাওয়া যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি প্রকৃতির নির্মলতা, ভূমিনির্ভরতার অকৃত্রিম বাস্তবতা। মানুষের এই সাময়িক বিভ্রমকে তিনি একটি ঐতিহাসিক পরিভ্রমণ-পথে দাঁড় করিয়ে প্রকৃত সমাজসত্য অনুভব করতে চেয়েছেন। পেছনে ফিরে তাকালে তিনি যেন দেখতে পান : ‘অনেক মানুষ ছিল মরেছে অনেক।/সেই সঙ্গে মরে গেছে তারো চেয়ে বেশিÑ/শতাব্দীর গ’ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম।’ (একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ)
বাঁচবার প্রয়োজনে কোমলতা পরিহার করে কঠোর-কঠিন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের পক্ষপাতী কবি আহসান। এই পৃথিবী আর তাতে বিচরণরত মানুষ যেন সত্যিই ‘শক্তের ভক্ত নরমের যম’, তাই তিনি সকল নরমতাকে শক্তকে পরিণত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কান্নার জলে প্লাবন বইয়ে দিতে চান তিনি সকল শত্রু-আস্তানার দোরগোড়ায়। তিনি জানেন, মানেন- দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সামনে অগ্রসর হওয়া-ভিন্ন কোন পথ নেই। ইংরেজ শাসকদের এদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করতে হলে প্রয়োজন সমবেত প্রতিরোধ, আর সেজন্য তাঁর অনুরোধ :
হে বাঁশরী অসি হও তুমি!
কেননা দুর্গের দ্বারে হানা দিল হায়েনা নয়ন;
কেননা উদ্যত আজ শাণিত নখর বহু
শিবিরের উলঙ্গ আকাশেÑ ...
এবার বন্যার মতো আঁখিজল আনুক বিদ্রোহ।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে অগ্নিময় ঝলসি উঠুক,
বাঁচিবার পণ! (হে বাঁশরী অসি হও)
আধিপত্যবাদী রাজনীতি, অহংকার প্রকাশের সংস্কৃতি আর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কারণে গোটা পৃথিবীতে দখলবাজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে আমেরিকা-ব্রিটেন। দরিদ্র আর আধাদরিদ্র দেশগুলো তাদের লোভী দৃষ্টির শিকারে পরিণত হয়েছে। কোন কোন দেশের তেল-গ্যাস-মেধা-নিম্নমূল্য শ্রমবাজার তাদের আকৃষ্ট করে নেশার মতো। খোলাবাজার অর্থনীতি আর আকাশনির্ভর সংস্কৃতির অন্তরালে তারা নির্মাণ করে চলেছে বদ্ধবাজার-পকেটনির্ভর রাজনীতি (পরিবারকেন্দ্রিক রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর বাধ্যবৃত্তির শাসন-ব্যবস্থা)। কয়েকজন ব্যক্তি আর পরিবারের হাতে রাজনীতি জিম্মি থাকলে শোষণে-ভোগে বেশ সুবিধাÑ তা বুঝে গেছে ইংরেজ জাতি। তাই তারা বাহ্যত দূরে থেকেও কাছে থাকার মতোই শাসন-পরিচালনা করছে প্রায় পুরো নিকটপ্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য। সারা পৃথিবীর বিচিত্র জাতিসত্তার বিনাশ-প্রচেষ্টার এই মহাযজ্ঞে আহসান হাবীব হতাশ হয়েছেন। দেশ-জাতির আপন আপন অস্তিত্ব আর পরিচয় অক্ষুণœ রাখতে তিনি দৃঢ়-সংকল্প। তাঁর অভিব্যক্তি :
আমাকে বিশাল কোনো সমুদ্রের ঢেউ হতে বলো।
হতে পারি, যদি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারো-
সমুদ্রের ঢেউ/হারায় না সমুদ্রের গভীরে এবং
ফিরে আসে শৈশবের নদীর আশ্রয়ে।
সমুদ্রে বিলীন হতে চাই না। কেননা
সমুদ্র অনেক বড় আর বড় বেশি দম্ভ আছে বলে
তাকে ভয়;
সে আছে নদীকে গ্রাসের প্রমত্ত লোভে মত্ত হয়ে। (সমুদ্র অনেক বড়)
হাজার বছরের ইতিহাসের পরিক্রমায় আহসান হাবীব খুঁজে পেয়েছেন ইতিবাচকতার উদার আহ্বান। সকল প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এক এক করে অগণন মুহূর্ত পার হয়ে মানবসভ্যতা নির্মাণ করে চলেছে তার কাক্সিক্ষত দৃশ্যাবলী; হাবীব জানেন এ সত্য অনিবার্যÑঅনতিক্রম্য। মানবিক বিজ্ঞান আর পরিবর্তন-প্রবণতা সমাজগতি রূপান্তরে রাখে অবিস্মরণীয় সব অবদান। কবি লিখছেন : ‘বন্দরে নিঃশেষ রাত; এখন সকাল,/ক্লান্তমুখে সকালের সূর্যের মহিমা।/এখন হৃদয়ে ডাক বসন্তেরÑ/স্তব্ধবাক পাখিরা মুখর।’ (ইতিহাস-বিন্যাসের পথে) শান্তি আর সুখের প্রত্যাশা কোন অন্যায় অভিপ্রায় নয়; এ ধরনের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিও বহন করে না কোনো অর্জনের আনন্দ। শান্তির জন্য সতর্ক অবস্থান ও ভূমিকা জরুরী। প্রয়োজন চেষ্টা আর প্রত্যয়ের। সৃজনশীল প্রতিভা কিংবা বলা চলে সৃজনক্ষম মানুষ অন্য মানুষের শান্তি আর সুখের জন্য নিয়োগ করেন তাঁদের কর্ম-প্রবণতা আর সৃজনবিলাস। শান্তিহারা মানুষের স্বস্তির জন্য বহুবার সংগ্রামে নামতে হয়েছে; প্রতিনিয়ত পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে আজও চলছে এ সংগ্রাম। যেহেতু প্রত্যাশার কোন পরিসীমা নেই, তাই শান্তিরও নেই কোন সঠিক সংজ্ঞা কিংবা নিশ্চিত ঠিকানা। প্রেম-স্বস্তি-শান্তিকামনা কবি আহসান হাবীবের কবিতার এক বিশেষ প্রবণতা। তাঁর অভিপ্রায় আমরা শুনতে পাই এসব পঙ্ক্তিতে :
যুদ্ধ-হত্যা লুণ্ঠনের উলাসের মুখে
যে পৃথিবী শঙ্কায় আকুল;
আমি সেই পৃথিবীর সতর্ক সন্তান।
...নীড় যদি চেয়ে থাকি,
শান্তি যদি আমারো কামনা;
শপথ সে নীড় আর সেই শান্তিকামনার নামে-
আমার রচনা সেই সংগ্রামের অজেয় বিষাণ।
... শপথ প্রেমের নামে,
শপথ শান্তির নামে,
পৃথিবীর শান্তিহারা মানুষের নামে। (প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা)
দারিদ্র্য আর অপ্রত্যাশিত লজ্জা ঢাকার অপপ্রয়াসে আচ্ছন্ন বাংলাদেশের অনটন-পীড়িত অগণন মানুষের জীবন। সারা দুনিয়ার বিপুল মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। মানুষের অল্পকয়টি মৌলিক অধিকারÑখাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা আজও প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। এরপর আবার যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত-বিস্ময়কর পরিসর। মৌলিক চাহিদাই যেখানে সোনার হরিণ, সেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আধুনিক ও প্রাগ্রসর সুবিধা মানুষের কাছে সহজলভ্য করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। দারিদ্র্যের কশাঘারে নুয়ে-পড়া কঙ্কালসার শরীর দেখেছেন হাবীব; দেখেছেন খাদ্যের-বস্ত্রের-স্বস্তির জন্য হাহাকারের ব্যাকুলতা। আমাদেরকে জানাচ্ছেন তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা :
একদিন দেখা গেল নুন নেই ঘরে
দেখা গেল পরদিন বৌয়ের ছতরে
ইজ্জত বাঁচার মত তেনাটুকু নাই
আচম্বিত শরমেতে নজর নামাই।
ফুরায়েছে কেরাসিন, নিভে গেল আলো
ভাবি এ রাতের মত মন্দের ভালো।
তারপর ক্রমে ক্রমে অনেক দেখেছি
অনেক দুঃখের কথা স্মরণে রেখেছি। (ছহি জঙ্গেনামা)
আশাবাদী প্রবণতা আহসান হাবীবের কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। উৎপাদনমুখী কৃষি-ব্যবস্থা আর মেধাবি-প্রসন্ন-প্রজন্মের অপেক্ষায় তিনি যেন অটল; তাঁর অপার আস্থা- অদূর ভবিষ্যতে আমরা পাবো মানসিক প্রশান্তির অবসর-প্রহর। তাঁর অমিত অনুভব- সমূহ কষ্ট-গানি পেরিয়ে হয়তো আমরা পৌঁছুবো কোনো আশাজাগানিয়া কালপর্বে। পরাধীনতার বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত-পথিকের মতো একটু জিরিয়ে নেবার অবসরে কবি ডুবে যাচ্ছেন যেন কোন অজ্ঞাত স্বপ্ন-বিভোরতায়। চিন্তা-স্বপ্ন আর কথা বুননের উৎসাহে সাড়া দিয়ে তিনি কবিতা-পাঠকের জন্য সাজিয়েছেন প্রেরণা-প্রদায়ক ভাবনারাজি। কবির কথামালা :
হাতে হাতে
সরাবো রাতের অন্ধকার, ভোর হবে
ফুটবে ফুল, দুটি একটি পাখির ডানায়
শেষ ঘুম ঝরে যাবে হিজলের ডালে
আদিম আবেগে দেখা দেবে ধানের মঞ্জরী, সেই ধান
মুঠোমুঠো আমরা ছড়াবো সারা মাঠে
সঙ্গে তার কিছু মেধা আর কিছু প্রতিভা ছড়াবো
অজস্র ফসলে যারা এই সব অমর আত্মাকে
অন্ন দেবে
এবং বিশ্রাম দেবে রৌদ্র আর ছায়ার মিছিলে। (ফুটবে ফুল)
মানুষের জানা-চেনার জগৎ আর জানবার-বুঝবার-চিনবার আগ্রহ ভুবনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। এই পৃথিবীর তাবৎ রহস্যের কতটুকুই-বা জানতে পারা যায়! হয়তো দৃশ্যবস্তুর কতকটা আর অনুভবজ্ঞানে কতকটা জেনে নিয়েছি আমরা। আর বাকিসব! যতটুকু জানা যায়; বোঝা যায় তাতেও কি রয়েছে আমাদের গভীর সম্পৃক্ততা? হয়তো নেই। তবে যাপিত জীবনে চারপাশের দেখা-জানা জগৎকে নিজের করে অনুভব করার ব্যবকুলতা মানুষের চিরন্তন। হাবীব তাই বোধহয় বলেন : ‘আমরা পরিচিত নই পরস্পর/তবু পরিচয়/প্রাত্যহিক ভ্রমণের পথে আর/সন্ধ্যার আঁধার এই প্রান্তরে কি লেখা নেই?’ (স্বরূপে মহিমা তার) নিরাপদ মাটি আর নিশ্চিত যাত্রাÑএইটুকু প্রত্যাশা নিশ্চয়ই বেশি কিছু নয়। আহসান হাবীব ভেবেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবেন বিচরণের অভয়ারণ্য; বসবাসের জন্য নিরাপদÑজীবনবান্ধব ভূমি। পরিবারকেন্দ্রিক রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের (!) দেশে সত্যিই কি তাঁর এই আকাক্সক্ষা দূরাশা নয়! মুক্তবাজার অর্থনীতি, আকাশ-সংস্কৃতির উদার বিস্তার আর শিক্ষাকে পণ্যবাজারে হাজির করবার এই বিশেষ সময়ে আমরা বন্দী হয়ে পড়ছি কতিপয় মানুষের রাজনৈতিক সুবিধা হাজিলের ক্রিতদাসের কঠিন ফিতায়। নানানবৃত্তির পাশাপাশি এখন আমাদের ঘারে চেপে বসেছে বাধ্যবৃত্তির অমোঘতা। গণতন্ত্র নয় বরং যেন ব্যক্তিবিশেষ-পরিবারবিশেষের গদিনেশায় অসহায় কতিপয় নির্বোধ পশু বৈ আর কিছু নই আমরা! এই অবস্থা থেকে নতুন-অনাগত প্রজন্মকে বাঁচাতে তাঁর কী অস্থিরতা; কী অধীর-প্রাণান্ত আশীর্বাণি প্রক্ষেপণ! তাঁর বিবৃতি :
কি জানেন, আমি যাব, আপনিও যাবেন,
শিশু আর কিশোর যুবক সন্তানেরা আমাদের
রয়ে যাবে।/সেঞ্চুরীর চারা
দীর্ঘদিন পরে জানি ফুল দেবে।
দীর্ঘদিন/আমরা তখন বেঁচে নেই পৃথিবীতে।
তাহোক তবুও
আমাদের সন্তানেরা এই পথে প্রত্যহ সকালে
লোহা কিম্বা ডালের আড়তে যাবে যখন
তখন/আমাদের কিছু ¯েœহ
কিছু দোয়া বুকে মেখে নিয়ে যাবে তারা। (রেখে যাবো)
ঐতিহ্য আর উত্তরণ প্রীতিকে অবহেলা করার পক্ষপাতী নন হাবীব; তিনি এ সব প্রবণতা আত্মস্থ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। বাসনা-প্রাপ্তি আর পরিভ্রমণ জীবনকে বিকশিত করে বিচিত্র মাত্রায়Ñতা তিনি অনুব করেছেন মনীষীদের জীবনযাত্রার আলোক থেকে। দিনে দিনে এই পৃথিবীতে জমতে দেখেছেন অনেক আশাÑঅনেক আলোকÑঅনেক প্রসন্নতা। আর সে অভিজ্ঞতার কথা কবিতার পাতায় পরিবেশন করতেও ভোলেননি তিনি। লিখছেন : ‘পথে পথে বিকশিত হয়েছে আমার প্রাণ/আমি দেখেছি শত শত মানুষের আত্মার বিকাশ,/আমাদের জীবনের সব তৃষ্ণা চিত্রিত দেখেছি/পথে পথে।’ (আশা রাখি কেননা) প্রকৃতির নিত্যদিনের চালচিত্র থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি; নিতে পারি নিয়তির দুর্নিবার অমোঘতা থেকে। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে কতক সংশয়ের পরেও বিশ্বাস রাখি যে, কোনো অসীম শক্তি আমাদের সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণভার সংরক্ষিত রেখেছে। আমরা এখানে অসহায় পুতুল মাত্র। তিনি যেভাবে খেলাচ্ছেন, সেভাবেই খেলছি আমরা! আর প্রতিনিয়ত আমাদেরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কুমতি-সুমতির দারুণ বিতণ্ডা-বাতাস। পিঠে দায় আর দায়িত্বে মুখ-আটা বস্তা নিয়ে আমরা ক্রম-ধাবমান যেন : ’নিয়তি!/নিয়তি আমাকে দেখো/কেমন অন্ধের মতো ঘোরায় তোমার হাতে!/তোমার হাতেই শিকার/আর তোমার লোভেরই শিকার ওরাÑ/আমি দেখো কুখ্যাতি কুড়াই সারা জীবন।/তোমার লোভের বলি সংগ্রহের ভার/আমি বইÑ’ (জাল)
দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, সেই দুর্যোগময় দিনগুলোতে তিনি রচনা করেছেন রাজনৈতিক-প্রজ্ঞাসম্পন্ন বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ও উদ্দীপনামূলক কবিতা। নদীমাতৃক শান্ত-স্থির মমতার দেশে দুরাচারের আক্রমণে যে দুর্বিষহ যন্ত্রণা আর প্রিয়মুখ হারাবার হাহাকার শুরু হলো, তার ভয়াবহতা-নির্মমতা কবি আহসান হাবীব আঁকেন আপন অভিজ্ঞতায়। আদিম-চিরন্তন গ্রামের ভেতর-পাটাতনে স্থির-রাখা অনুভন জ্ঞানে তিনি অনুধাবন করেছেনÑনিস্তরঙ্গ গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া অভিশাপ-বাতাস যেন সবকিছু বিকল করে দিয়ে গেছে; কিছুতেই আর প্রাণটুকুও যেন অবশিষ্ট নেই। কবি লিখেছেন :
হায়রে নদী সখের নদী সখের মেলা
বন্ধুবিহীন একলা পথে ফুরায় বেলা
ঘর ভোলানো হায়রে ভানুমতির খেলা!
আদ্যিকালের একটি মেয়ে সেই যে মেয়ে
ঘাটের পাশে কলসী রেখে রইলো চেয়ে
’নিয়তি!/নিয়তি আমাকে দেখো/কেমন অন্ধের মতো ঘোরায় তোমার হাতে!/তোমার হাতেই শিকার/আর তোমার লোভেরই শিকার ওরাÑ/আমি দেখো কুখ্যাতি কুড়াই সারা জীবন।/তোমার লোভের বলি সংগ্রহের ভার/আমি বইÑ’ (জাল)
দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, সেই দুর্যোগময় দিনগুলোতে তিনি রচনা করেছেন রাজনৈতিক-প্রজ্ঞাসম্পন্ন বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ও উদ্দীপনামূলক কবিতা। নদীমাতৃক শান্ত-স্থির মমতার দেশে দুরাচারের আক্রমণে যে দুর্বিষহ যন্ত্রণা আর প্রিয়মুখ হারাবার হাহাকার শুরু হলো, তার ভয়াবহতা-নির্মমতা কবি আহসান হাবীব আঁকেন আপন অভিজ্ঞতায়। আদিম-চিরন্তন গ্রামের ভেতর-পাটাতনে স্থির-রাখা অনুভন জ্ঞানে তিনি অনুধাবন করেছেনÑনিস্তরঙ্গ গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া অভিশাপ-বাতাস যেন সবকিছু বিকল করে দিয়ে গেছে; কিছুতেই আর প্রাণটুকুও যেন অবশিষ্ট নেই। কবি লিখেছেন : হায়রে নদী সখের নদী সখের মেলা
বন্ধুবিহীন একলা পথে ফুরায় বেলা
ঘর ভোলানো হায়রে ভানুমতির খেলা!
আদ্যিকালের একটি মেয়ে সেই যে মেয়ে
ঘাটের পাশে কলসী রেখে রইলো চেয়ে
রইলো চেয়ে/পারুল গেলো গেলো বকুল শেফালী যায়
চৈতী খরা রোজ দুপুরে ধুলো ওড়ায়...
সেই যে ছেলে একলা ছেলে ফেরে না হায়! (কাহিনী নিরন্তর)
অভিজ্ঞ সংসারির মতো, পরাজিত অভিভাবকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কবি আহসান হাবীব বলছেন জীবনের না-পাওয়ার ইতিহাসের ভেতর-কথা। আর জানাচ্ছেন মধ্যবিত্ত-নি¤œমধ্যবিত্ত আমজনতার স্বাভাবিক প্রাপ্তি-আকাক্সক্ষার বাস্তবতা। ধৈর্যকে সঙ্গী-মানা আর পরাজয় মেনে-নেওয়া সাধারণ মানুষ কি রকম কষ্ট বুকে নিয়ে পার করছেন প্রতিটি মুহূর্ত, তা যেন টের পান হাবীব; হয়তো নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের থালায় ঢেলে কিংবা অন্যকে নিজের মতো করে ভেবে কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন কবি। তাঁর কবিতায় আমরা অন্তত সেরকম অনুভবের বিররণ পাই:
আপনি ত জানেন। সব দেখেছেন, আমি
আজীবন অপেক্ষাই করেছি। আমার অপেক্ষাই সার হলো।
আজীবন আমি কী চেয়েছি? একটি বার
কেবল একটি বার। একটি বার বাস্-এ চড়ে
যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছবো। আর যথাযথ সময়ে। কেবল
এই আশা নিয়ে
কেটে গেছে সমস্ত যৌবন, সমস্ত জীবন, আহা
অসীম অনন্তকাল যেন। (বাস নেই) মুক্তির আনন্দ, স্বাধীনতার সুখ আর উদ্দীপনা কবি আহসান হাবীব কবিতার সাথী করেছেন; তবে কবিতাকে তিনি রাজনীতির মঞ্চ বানাননি। তাঁর কবিতায় রাজনীতির পরিবেশ-আভাস আছে; রাজনৈতিক অভিযানে জনতার অংশগ্রহণের প্রেরণার নিষ্ঠাপূর্ণ বিবরণ আছে। অধিকার আর মর্যাদা আদায়ের দাবিতে যে জনতার উল্লাস, তাকে তিনি পরিহার করতে পারেননি। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যে অঅকুলতা-অপেক্ষা তার বাস্তবতাকে তিনি কবিতার পঙ্ক্তিমালায় স্থান দিয়েছেন গভীর আগ্রহেÑনিবিড় পরিচর্যায়। যেমন :
মিছিলে অনেক মুখ
দেখো দেখো প্রতি মুখে তার
সমস্ত দেশের বুক থরোথরো
উত্তেজিত
শপথে উজ্জ্বল!
...আর সেই মুখের আভায়
পথের ধুলোয় দেখো আলো জ্বলে,
জানালার মুখ
উদ্ভাসিত এবং চঞ্চল।’ (মিছিলে অনেক মুখ)
প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বরাবর বড় অসহায় হয়ে পড়ি। ১৯৭০ সালের ১২ নবেম্বরের সর্বোপাবি বন্যায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে নেমে-আসা দুর্ভোগ আর দর্শনার্থীর অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে হাবীবের ‘ক্ষমাই প্রার্থনা’ কবিতায়। তিনি জানাচ্ছেন দুর্গতের জন্য তাঁর তেমন কিছুই না-করার কথা; তাঁর অক্ষমতার কথা : ‘আমার এ অক্ষমতা,/ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি/মৃত আর মৃতপ্রায়/এই সব মথিত আত্মার কাছে/গলিত শবের/পবিত্র দুর্গন্ধ কিছু গায়ে মেখে/রুগ্ন এ আত্মার শুশ্রুষায় রত হতে পারি।’
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আর সামাজিক অসমতা আহসান হাবীবকে একরকম বিনয়ী প্রতিবাদী করে তুলেছিল। প্রতিবাদ করতে গেলেই, দাবির কথা জানাতে গেলেই উচ্চকণ্ঠ হতে হবেÑএমন বিশ্বাসে আস্থাশীল নন আহসান হাবীব; তিনি হৈ চৈ উপস্থাপনের চেয়ে কৌশল অবলম্বনের পক্ষপাতী। বাঁচবার তাগিদÑহাজির থাকবার তাগিদ তাঁর কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর তাই বিধাতার কাছে শক্তি কামনাও ছিল তাঁর কবিস্বভাব-অন্বিষ্ট; তিনি লিখছেন :
তুমি আমার শোকের পবিত্রতা
লালনের ভার দাও আমাকেই
আমাকে কেবল
ক্ষুধার এই অন্ধকার থেকে মুক্ত করো
আমাকে বাঁচতে দাও। (আমাকে দাও)
আর তাঁর প্রতিবাদের ভাষা কখনো কখনো এরকম দাঁড়ায় : ’যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই দৃশ্য বারবার।/অথচ এবার/কি আশ্চর্য, লোকটা চেনা, তার সেই বিভ্রান্ত দুচোখ/শান্ত, অর্থময় ঘোরে না দুচোখে মিনতির ছায়া টেনে, তার/গলায় চিৎকার নেই, একমনে বসে/লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়।’ (যতবার এবং এবার) বিভ্রান্তি-মনোবিকলন আর অনাস্থা আধুনিক জীবনাচারের অন্যতম অনুষঙ্গ। আহসান হাবীবের কবিতায় আমরা পাই সমাজের এই বিশেষ স্থিতির প্রতি সবিশেষ অভিনিবেশ। ক্রমাগত কেবল স্বস্তিহীন একটা গুমোট ভুবনে প্রবেশ করছি আমরা; সঙ্গে আছে যেন অমিত জিজ্ঞাসা : ‘আমার ত কোথাও না কোথাও/ যেতে হবে/অথচ কোথায় যাবে কোন পথে/কেউ বলে না, কেবল/যার যার নিজের নির্দিষ্ট পথে যেতে যেতে/চমকে ওঠে/থমকে থমকে খানিক দাঁড়ায়/যেখানে আমি আর আমার সঙ্গীরা/সমবেত জিজ্ঞাসায় সোচ্চার...।’ (আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে) কিন্তু যাবার পথ কি অনুকূলÑকণ্টকমুক্ত! বণিক-স্বভাব এই সমাজে কার কী গন্তব্য জানা সাধ্য কার!
নগর-ব্যবস্থাপনা এমনকি অফিস-ব্যবস্থাপনা কিংবা সভা-সমিতি পরিচালনার জন্য মতবিনিময় যেমন জরুরী, তেমনি জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক কোন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও দরকার জনমত-জরিপÑনাগরিক কবি আহসান হাবীব এই সত্য প্রকাশ করতে কোন অস্বস্তি বোধ করেননি। অনেক সময় সরকারপক্ষীয় নেতা-প্রশাসকদের খেয়ালি সিদ্ধান্ত জাতির মাথায় চাপাতে দেখা যায়Ñযা বাস্তবিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। জনপ্রশাসন এবং লোকপ্রশাসন বিষয়ে তাঁর এই কবিতানির্মাণ-প্রচেষ্টা আমাদেরকে আশান্বিত করেÑকথা বলতে, মত প্রকাশ করতে সাহস যোগায় :
ডাস্টবিনগুলো সাফ করবার ব্যবস্থায়
তৎপর হওয়ার আগে
ফুল চাষের জন্য মালী সংগ্রহের আগে
এবং টিকা ইনজেকশান ছড়িয়ে দেবার আগে
পানি ফোটাবার ঘোষণার আগে
আপনার পরার্থপর সভ্যদের নিয়ে
এবার একটি বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন আছে
আপনি স্বীকার করেন কি? (সমীপেষু)
‘আত্মম্ভরিতা’র চেয়ে ’আত্মরক্ষা’র প্রয়োজনকে তিনি বড় করে দেখেছেন। শিল্প-কারখানানির্ভর নগর-কোলাহল, গ্রামসভ্যতার ক্রম-বিলোপে ছিল তাঁর বড় ভয়। যদিও বিজ্ঞান আর গতিময়তাকে জানিয়েছেন সাদর অভিবাদন। বলেছেন : ’জয়তু বিজ্ঞান! জয়/জয় গতিময়তার অপার বিস্ময়!’ দিনবদলের স্বপ্ন-বিভোরতা নিয়ে কবি আহসান হাবীব সমাজে সকল মানুষের অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। চলমান দিনের, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের অভিমুখে যাত্রার আবাহন শুনতে পাই তাঁর কবিতাকথায়। পক্ষ-বিপক্ষ, পজিশন-অপজিশনÑসবাই মিলে সমবেতভাবে নতুন দিনের আলোকসভায় যোগ দেবেন এই প্রত্যাশা লালন করতেন কবি আজহসান হাবীব। লিখেছেন :
সবাই মিলে
নতুন নতুন শহর গড়ব
নতুন নতুন গ্রাম বানাব
সবই নতুন
নতুন পথ আর নতুন বাহন
চলাফেরার এক ব্যবস্থা
যার যার সব নিজের বাড়ি
নিজের দরজা নিজের উঠোন
ঘরগেরস্থি সবই নিজের। (আমার আমার)
রইলো চেয়ে/পারুল গেলো গেলো বকুল শেফালী যায়
চৈতী খরা রোজ দুপুরে ধুলো ওড়ায়...
সেই যে ছেলে একলা ছেলে ফেরে না হায়! (কাহিনী নিরন্তর)
অভিজ্ঞ সংসারির মতো, পরাজিত অভিভাবকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কবি আহসান হাবীব বলছেন জীবনের না-পাওয়ার ইতিহাসের ভেতর-কথা। আর জানাচ্ছেন মধ্যবিত্ত-নি¤œমধ্যবিত্ত আমজনতার স্বাভাবিক প্রাপ্তি-আকাক্সক্ষার বাস্তবতা। ধৈর্যকে সঙ্গী-মানা আর পরাজয় মেনে-নেওয়া সাধারণ মানুষ কি রকম কষ্ট বুকে নিয়ে পার করছেন প্রতিটি মুহূর্ত, তা যেন টের পান হাবীব; হয়তো নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের থালায় ঢেলে কিংবা অন্যকে নিজের মতো করে ভেবে কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন কবি। তাঁর কবিতায় আমরা অন্তত সেরকম অনুভবের বিররণ পাই:
আপনি ত জানেন। সব দেখেছেন, আমি
আজীবন অপেক্ষাই করেছি। আমার অপেক্ষাই সার হলো।
আজীবন আমি কী চেয়েছি? একটি বার
কেবল একটি বার। একটি বার বাস্-এ চড়ে
যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছবো। আর যথাযথ সময়ে। কেবল
এই আশা নিয়ে
কেটে গেছে সমস্ত যৌবন, সমস্ত জীবন, আহা
অসীম অনন্তকাল যেন। (বাস নেই)
মুক্তির আনন্দ, স্বাধীনতার সুখ আর উদ্দীপনা কবি আহসান হাবীব কবিতার সাথী করেছেন; তবে কবিতাকে তিনি রাজনীতির মঞ্চ বানাননি। তাঁর কবিতায় রাজনীতির পরিবেশ-আভাস আছে; রাজনৈতিক অভিযানে জনতার অংশগ্রহণের প্রেরণার নিষ্ঠাপূর্ণ বিবরণ আছে। অধিকার আর মর্যাদা আদায়ের দাবিতে যে জনতার উল্লাস, তাকে তিনি পরিহার করতে পারেননি। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যে অঅকুলতা-অপেক্ষা তার বাস্তবতাকে তিনি কবিতার পঙ্ক্তিমালায় স্থান দিয়েছেন গভীর আগ্রহেÑনিবিড় পরিচর্যায়। যেমন :
মিছিলে অনেক মুখ
দেখো দেখো প্রতি মুখে তার
সমস্ত দেশের বুক থরোথরো
উত্তেজিত
শপথে উজ্জ্বল!
...আর সেই মুখের আভায়
পথের ধুলোয় দেখো আলো জ্বলে,
জানালার মুখ
উদ্ভাসিত এবং চঞ্চল।’ (মিছিলে অনেক মুখ)
প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বরাবর বড় অসহায় হয়ে পড়ি। ১৯৭০ সালের ১২ নবেম্বরের সর্বোপাবি বন্যায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে নেমে-আসা দুর্ভোগ আর দর্শনার্থীর অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে হাবীবের ‘ক্ষমাই প্রার্থনা’ কবিতায়। তিনি জানাচ্ছেন দুর্গতের জন্য তাঁর তেমন কিছুই না-করার কথা; তাঁর অক্ষমতার কথা : ‘আমার এ অক্ষমতা,/ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি/মৃত আর মৃতপ্রায়/এই সব মথিত আত্মার কাছে/গলিত শবের/পবিত্র দুর্গন্ধ কিছু গায়ে মেখে/রুগ্ন এ আত্মার শুশ্রুষায় রত হতে পারি।’
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আর সামাজিক অসমতা আহসান হাবীবকে একরকম বিনয়ী প্রতিবাদী করে তুলেছিল। প্রতিবাদ করতে গেলেই, দাবির কথা জানাতে গেলেই উচ্চকণ্ঠ হতে হবেÑএমন বিশ্বাসে আস্থাশীল নন আহসান হাবীব; তিনি হৈ চৈ উপস্থাপনের চেয়ে কৌশল অবলম্বনের পক্ষপাতী। বাঁচবার তাগিদÑহাজির থাকবার তাগিদ তাঁর কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর তাই বিধাতার কাছে শক্তি কামনাও ছিল তাঁর কবিস্বভাব-অন্বিষ্ট; তিনি লিখছেন :
তুমি আমার শোকের পবিত্রতা
লালনের ভার দাও আমাকেই
আমাকে কেবল
ক্ষুধার এই অন্ধকার থেকে মুক্ত করো
আমাকে বাঁচতে দাও। (আমাকে দাও)
আর তাঁর প্রতিবাদের ভাষা কখনো কখনো এরকম দাঁড়ায় : ’যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই দৃশ্য বারবার।/অথচ এবার/কি আশ্চর্য, লোকটা চেনা, তার সেই বিভ্রান্ত দুচোখ/শান্ত, অর্থময় ঘোরে না দুচোখে মিনতির ছায়া টেনে, তার/গলায় চিৎকার নেই, একমনে বসে/লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়।’ (যতবার এবং এবার) বিভ্রান্তি-মনোবিকলন আর অনাস্থা আধুনিক জীবনাচারের অন্যতম অনুষঙ্গ। আহসান হাবীবের কবিতায় আমরা পাই সমাজের এই বিশেষ স্থিতির প্রতি সবিশেষ অভিনিবেশ। ক্রমাগত কেবল স্বস্তিহীন একটা গুমোট ভুবনে প্রবেশ করছি আমরা; সঙ্গে আছে যেন অমিত জিজ্ঞাসা : ‘আমার ত কোথাও না কোথাও/ যেতে হবে/অথচ কোথায় যাবে কোন পথে/কেউ বলে না, কেবল/যার যার নিজের নির্দিষ্ট পথে যেতে যেতে/চমকে ওঠে/থমকে থমকে খানিক দাঁড়ায়/যেখানে আমি আর আমার সঙ্গীরা/সমবেত জিজ্ঞাসায় সোচ্চার...।’ (আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে) কিন্তু যাবার পথ কি অনুকূলÑকণ্টকমুক্ত! বণিক-স্বভাব এই সমাজে কার কী গন্তব্য জানা সাধ্য কার!
নগর-ব্যবস্থাপনা এমনকি অফিস-ব্যবস্থাপনা কিংবা সভা-সমিতি পরিচালনার জন্য মতবিনিময় যেমন জরুরী, তেমনি জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক কোন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও দরকার জনমত-জরিপÑনাগরিক কবি আহসান হাবীব এই সত্য প্রকাশ করতে কোন অস্বস্তি বোধ করেননি। অনেক সময় সরকারপক্ষীয় নেতা-প্রশাসকদের খেয়ালি সিদ্ধান্ত জাতির মাথায় চাপাতে দেখা যায়Ñযা বাস্তবিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। জনপ্রশাসন এবং লোকপ্রশাসন বিষয়ে তাঁর এই কবিতানির্মাণ-প্রচেষ্টা আমাদেরকে আশান্বিত করেÑকথা বলতে, মত প্রকাশ করতে সাহস যোগায় :
ডাস্টবিনগুলো সাফ করবার ব্যবস্থায়
তৎপর হওয়ার আগে
ফুল চাষের জন্য মালী সংগ্রহের আগে
এবং টিকা ইনজেকশান ছড়িয়ে দেবার আগে
পানি ফোটাবার ঘোষণার আগে
আপনার পরার্থপর সভ্যদের নিয়ে
এবার একটি বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন আছে
আপনি স্বীকার করেন কি? (সমীপেষু)
‘আত্মম্ভরিতা’র চেয়ে ’আত্মরক্ষা’র প্রয়োজনকে তিনি বড় করে দেখেছেন। শিল্প-কারখানানির্ভর নগর-কোলাহল, গ্রামসভ্যতার ক্রম-বিলোপে ছিল তাঁর বড় ভয়। যদিও বিজ্ঞান আর গতিময়তাকে জানিয়েছেন সাদর অভিবাদন। বলেছেন : ’জয়তু বিজ্ঞান! জয়/জয় গতিময়তার অপার বিস্ময়!’ দিনবদলের স্বপ্ন-বিভোরতা নিয়ে কবি আহসান হাবীব সমাজে সকল মানুষের অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। চলমান দিনের, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের অভিমুখে যাত্রার আবাহন শুনতে পাই তাঁর কবিতাকথায়। পক্ষ-বিপক্ষ, পজিশন-অপজিশনÑসবাই মিলে সমবেতভাবে নতুন দিনের আলোকসভায় যোগ দেবেন এই প্রত্যাশা লালন করতেন কবি আজহসান হাবীব। লিখেছেন :
সবাই মিলে
নতুন নতুন শহর গড়ব
নতুন নতুন গ্রাম বানাব
সবই নতুন
নতুন পথ আর নতুন বাহন
চলাফেরার এক ব্যবস্থা
যার যার সব নিজের বাড়ি
নিজের দরজা নিজের উঠোন
ঘরগেরস্থি সবই নিজের। (আমার আমার)
ঢাকা, বাংলাদেশ শনিবার ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ১২ বৈশাখ ১৪৩২