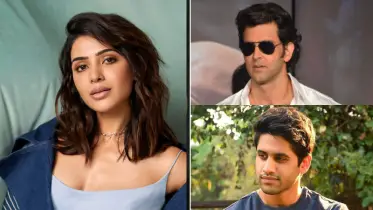ড. সন্জীদা খাতুন
ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে উৎসবে মেতে ওঠার সময়। হাতে রয়েছে মাত্র তিনটি দিন। সেই সূত্রে বিদায় নেবে বঙ্গাব্দ ১৪৩১। রাশি রাশি আনন্দের সঙ্গে আগামীর সম্ভাবনা ও কল্যাণের বারতা নিয়ে হাজির হবে নতুন বাংলা সন ১৪৩২। রকমারি রঙে ভর করে হৃদয়ের উষ্ণতায় সাড়ম্বরে রাজধানীসহ দেশব্যাপী উদ্যাপিত হবে নববর্ষ। তবে দেশজুড়ে নববর্ষ আবাহনের বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে তাকাতে হয় একটু পেছনে।
কারণটি হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্পর্শময় বাংলা নববর্ষের সঙ্গে একসময় শহরবাসীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। মূলত গ্রামে-গ্রামে মেলা, নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তি, নতুন কাপড় পরিধান, পিঠা-পুলির আয়োজনে উদ্যাপিত হতো নববর্ষ। সেই প্রেক্ষাপটে শহর কিংবা নাগরিক জীবনে নববর্ষ আবাহনের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন গুটিকয়েক মানুষ। তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সম্প্রতি প্রয়াত সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা ছায়ানট সভাপতি ড. সন্জীদা খাতুন।
ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের মাধ্যমেই নাগরিক জীবনে নববর্ষ উদ্্যাপনের সূচনা। ১৯৬৭ সালে প্রথম রমনা বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতি অনুূষ্ঠানের মাধ্যমে নগর জীবনে বর্ষবরণের সংযোগ ঘটে। ওই প্রভাতি অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই সময়ের ¯্রােতধারায় বাংলা নববর্ষ একইসঙ্গে সর্বজনীন ও জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। আর নববর্ষ উদ্যাপনের অন্তর্গত চেতনা, বাঙালিত্বের বোধ জাগিয়ে তোলা, প্রান্তিক স্তরে সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে না পারার আক্ষেপসহ নানা বিষয়ে কথা হয় সন্জীদা খাতুনের সঙ্গে ।
২০১৭ সালে রমনা বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতি অনুষ্ঠানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সে আলাপচারিতায় নববর্ষের পাশাপাশি সংস্কৃতির সামগ্রিকতাসহ নানা বিষয়ে ভাবনার কথা মেলে ধরেন সন্্জীদা খাতুন। সঙ্গে ছিল নববর্ষ নিয়ে নেপথ্যের স্মৃতিচারণ।
রমনা বটমূলে বর্ষবরণের সূচনা প্রসঙ্গে সন্জীদা খাতুন বলেন, সবাই জানে ১৯৬৭ সালে ছায়ানট প্রথম বর্ষবরণের আয়োজন করে। তবে শুরুটা হয়েছিল আরও আগে। সময়টা ছিল ১৯৬৩ সাল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকার ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলে (বর্তমানে উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রথম আয়োজনটি করেছিলাম। সেটা ছিল আসলে ছায়ানটের বর্ষপূর্তির আয়োজন। সরু একটা গলির ভেতর অপূর্ব সুন্দর এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে প্রথম নববর্ষ উদ্যাপন করেছিলাম।
এরপর চৌষট্টি সালেও একই স্থানে করলাম। সেই আয়োজনে যুক্ত হলো কিছু নববর্ষের গান। পঁয়ষট্টিতে এসে পড়ল ঈদুল আজহা। সেবার কিছুই হলো না। ছেষট্টি সালে আমাদের বন্ধুজন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড. নওয়াজেশ আহমেদ বকুনি দিলেন। বললেন, এই এসব কী হচ্ছে? আমরা কী এখানে বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান দেখতে আসি? আমরা আসি নববর্ষ দেখতে। নববর্ষের একটা বাণী থাকবে। একটা বার্তা থাকবে।
এতটুকু জায়গায় কি সেটা হয়? এরপর তিনি বিস্তৃত পরিসরে বর্ষবরণের জন্য রমনা বটমূলের জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন। আমাদেরও টনক নড়ল। উপলব্ধি করলাম, নববর্ষ বাঙালির জীবনে অনেক বড় ব্যাপার। বাঙালিত্বের এই গৌরবকে সবার কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারলে এর সার্থকতা থাকে না। আমাদের ভাবনায় ছিল, মানুষের মধ্যে বাঙালিত্বের গৌরববোধের উপলব্ধি ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, সেই সময় আমাদেরকে বাঙালির পরিবর্তে মুসলমান বানানোর চেষ্টা চলছিল।
তাই আমরা মুসলমানের আগে বাঙালিত্বের বোধটিকে জাগ্রত করতে চেয়েছি সবার মনে। বর্ষবরণের মাধ্যমে স্বাধিকারের চেতনা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি। সেই স্বাধিকারের চেতনা থেকেই এসেছিল স্বাধীনতা। জাতিসত্তার জাগরণের সেই ভাবনাতেই রমনা বটমূলে প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়। সেই বর্ষবরণ ছিল বাঙালি জাতির জাগরণের যাত্রা।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পহেলা বৈশাখ বটমূলে নববর্ষের কোনো আয়োজন ছিল না। কেমন ছিল সে বছরের পহেলা বৈশাখের দিনটিÑএই প্রশ্নের জবাবে সন্জীদা খাতুন বলেন, সেদিন আমরা ছিলাম সাভারের গ্রামে একটি মাটির ঘরে। সেখানেই বটমূল কল্পনা করে বসে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি ও ওয়াহিদুল হক সকালবেলায় গান গেয়েছিলাম।
মনে হয়েছিল, পহেলা বৈশাখ উদ্্যাপিত হবে না-সেটা হতে পারে না। আমরা পারিবারিকভাবে পালন করেছিলাম। বড় করে আয়োজন করার সুযোগ ছিল না। পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। অনেকেরই নাম ছিল এলিমিনেশন লিস্টে।
নববর্ষে ছায়ানটের প্রভাতি অনুষ্ঠানকে সরকারিকরণ না করার বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরে সন্্জীদা খাতুন বলেন, প্রজ্ঞা ও মেধার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণের তাৎপর্যটি। তাই দেশ স্বাধীনের পর ছায়ানটকে ছোট পরিসরে আটকে না রেখে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সরকারিকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তবে আমরা তখন রাজি হইনি। কারণ, আমরা নিজেদের মতো করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে চেয়েছি।
রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য গঠনমূলক কিছু করতে চেয়েছি। সরকার পরিবর্তন হলে নতুন সরকারের মনোভাব কেমন হবেÑসেটা নিয়েও আমাদের সংশয় ছিল। তা ছাড়া কথা বলার জন্যও কিছু লোক থাকা দরকার।
বর্ষবরণের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণটি আসলে অশ্বত্থমূল না বটমূল-এ প্রসঙ্গে সন্্জীদা খাতুন বলেন, যে গাছটির নিচে আমরা বর্ষবরণের আয়োজন করি, সেটা বট নয় অশ্বত্থ গাছ। যদি আমরা বলতাম, অশ্বত্থতলায় অনুষ্ঠান, তাহলে মনে হতো গ্রামের হাট বসেছে এখানে। অশ্বত্থের মঙ্গে পঞ্চবটির সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই অশ্বত্থতলাকে বটমূল বলেছিলাম। সেটা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেছে। এমনকি পত্রপত্রিকায় পোস্ট এডিটরিয়ালও লেখা হয়েছে। মানুষ ভাবে আমরা বুঝি আহাম্মক! এটা আমাদের মস্ত বড় দুঃখ।
বর্ষবরণে পান্তা-ইলিশ প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলেন, নববর্ষ উদ্্যাপনে পান্তা ইলিশ খেতে হবেÑএমনটা কখনো দেখিনি, শুনিনি। কারণ গ্রামের মানুষ পান্তা ভাত খায়। সেখানে ইলিশ থাকে না। কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে অথবা মরিচ পুড়িয়ে পান্তা খায়। ইলিশ তো দামি মাছ, এটা গ্রামের মানুষ কোথায় পাবে? এ এক অদ্ভুত জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বর্ষবরণের আয়োজনে।
বর্ষবরণের আয়োজনটি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টাকে কিভাবে দেখেনÑজানতে চাইলে সন্জীদা খাতুন বলেন, আমি দুঃখের সঙ্গে বলব এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। যতটা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। এটা এখন ‘ফ্যাশন’ হয়ে গেছে। আর কে কত ভালো করতে পারে, কোন টেলিভিশনে কত ভালোভাবে দেখানো যায় সেই প্রতিযোগিতা চলছে।
অথচ আমারা তো টেলিভিশনের জন্য বর্ষবরণের আয়োজন করিনি। আমরা করেছিলাম অন্তরের তাগিদে। আমাদেরকে এখনো সেই তাগিদ নিয়েই চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের অন্য কথা ভেবে লাভ নেই। গঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে এবং সে কাজের ধরনও একটু বদলানো দরকার। কেবল শহরে বসে গান গাইলে হবে না।
আমাদের একটু বেরুতে হবে, গ্রামে-গ্রামে যেতে হবে। আসলে আমি নিজে তো বুড়ো হয়ে গেছি। তাই নিজে আর পারছি না। আমি না পারি তরুণ-তরুণীরা পারবে। তাহলে হয়তো একটু ভালো কাজ হবে। কারণ সংস্কৃতির বাহন মানুষের মনকে অনেক বেশি স্পর্শ করে।
বাঙালিত্বের বোধ প্রসঙ্গে সন্জীদা খাতুন বলেন, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই জানে না বাঙালিত্ব কাকে বলে। দুঃখের সঙ্গে বলছি, এমনকি রাষ্ট্রও সেটা জানে না। সে কারণেই গালে পতাকা এঁকে কিংবা একতারা হাতে নিয়ে বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করে। মূল বিষয়টি অনুধাবনের চেয়ে সেখানে হৈ-হুল্লোড়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। অনেকে এসে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের গান শোনে কিন্তু গানের ভেতরের অর্থগুলো বোঝা বা উপলব্ধির চেষ্টা করে না। বর্ষবরণ উদ্্যাপনে আমাদের ভাবনায় ছিল মানুষের মনের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।
মানুষের কাছে মানবতার কথা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের কথা বলার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথের অনেক ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু মানুষ সেসব বোঝে না। তাই বলতে হবে নজরুলের কথা। রবীন্দ্রনাথ নয় নজরুলের কথা তুলে ধরা দরকার গ্রামের মানুষদের কাছে। লালনের সহজ কথাগুলো তুলে ধরতে হবে প্রান্তিক মানুষের কাছে। লালন বলেছে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?
লালন বলছে জাতের কি রূপ দেখলাম না, এই জীবনে বুঝলাম না। এই যে কথাগুলো কিন্তু মানুষ শুনে। সুরাশ্রিত বাণীগুলো গ্রহণ করে। নজরুলের একটি গান আছে ‘ক্ষমা কর হযরত’। সেখানে বলা হয়েছে, তুমি আমাদের যে পথ দেখিয়েছিলে আমরা সেই পথে চলিনি। আমরা অন্যায় করেছি। আমরা বিধর্মীর কথা ভাবিনি। আমরা ছুটি মন্দির ভাঙতে। এই যে আমাদের মানসিকতা এই শিক্ষা কিন্তু তুমি দিয়ে যাওনি। ক্ষমা কর হযরত।
এখন বুঝি এইজন্যই তোমার রহমত আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে মুসলমান বাতিক আছে, মানুষ বাতিকটা নেই। এই বাতিকটাই সর্বনাশ করছে। সেইজন্যেই আমাদেরকে একটু কৌশল করতে হবে।
বিভিন্ন প্রলোভন অগ্রাহ্য করে আমৃত্যু সাংস্কৃতিক সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছেন সন্জীদা খাতুন। তাই আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে অনেকে ডেকেছে, কমিউনিস্ট পার্টি ডেকেছে, একসময় এমপি হওয়ার জন্য বিশেষ দলের সদস্য হতে বলা হয়েছে। আমার একটাই কথা, কোনো দলের হতে পারব না।
তাহলে আমার নিজের কোনো কথা আমি বলতে পারব না। আমার কথা বলতে হবে। কথা বলারও কিছু লোক চাই। সংস্কৃতির আশ্রয়েই নিজের ভাবনাটাকে তুলে ধরতে চেয়েছি। নিজে মঞ্চে উঠে গান গাওয়ার পরিবর্তে সংগঠকের ভূমিকাটাকেই বড় করে দেখেছি।