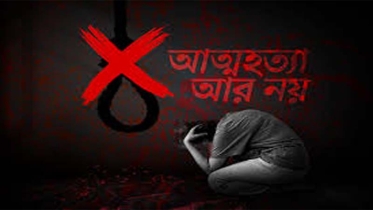বৈশাখী মেলায় মহিলা ও শিশুরা পছন্দের খেলনা কিনছেন
স্মৃতিময় করে তোলে
বাঙালির জীবন
চড়ক পূজার মেলা বা চৈত্রসংক্রান্তি মেলা, বৌমেলা, জামাইমেলা, ঈদমেলা, বইমেলা, বিজয়মেলা, সাধুমেলা, কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যমেলা, মৃৎশিল্পমেলা, ঘাটু সন্ন্যাসীর মেলা, বৈশাখীমেলাসহ গ্রামবাংলায় নানা প্রান্তিকে এমন নানা নামের মেলার নাম রয়েছে। তবে বৈশাখীমেলাই একমাত্র মেলা, যা বাঙালির জীবন রঙ্গ-রসে, ভোগ বিলাসে স্মৃতিময় করে তোলে। ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষ একসময় বৈশাখীমেলার এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতেন। এখনো করেন, হয়তো যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করবেন। কেননা বৈশাখীমেলা বাঙালির অস্থিমজ্জায় স্থান করে নিয়েছে।
‘এসো এসো, এসো হে বৈশাখ’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানের তালে তালে গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে বৈশাখীমেলায় নানা আয়োজন করা হয়। নতুন পোশাক, পায়েশ পান্তা পিঠাপুলি তৈরি থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাবারের আয়োজন হয় নিজের ঘরেই। মেলায় মুড়ি, মুড়কি, খাজা গজা, মাটির তৈরি পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ শিশু-কিশোরদের অন্যতম আকর্ষণের বস্তু । এছাড়াও খই, বাতাসা, রসগোল্লা, চমচম, কদমা, জিলাপি আর দানাদার নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রী মেলায় বিক্রি হয়। তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলনা বাঁশির কথাও বলা যায়। আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে গ্রাম- গ্রামান্তর।
এই মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামের টিনের চালার মাটির ঘরগুলো কাদা মাটি দিয়ে লেপে পরিচ্ছন্ন করে তাতে আঁকা হতো নানা চিত্র। সেখানে ফুটে উঠত গ্রামীণ জীবনের নানা নান্দনিক ছাপ। এ জন্য রং হিসেবে ব্যবহার করা হতো গাছের ছাল-বাকল। তবে যুগ পাল্টেছে। মেলার সেকাল এখন আর নেই। মেলা আছে, তবে পরিবর্তন হয়েছে মেলার নানা অনুষঙ্গ। আধুনিকতার নামে মেলাকে শহরমুখী করা হয়েছে। নির্ভেজাল বাঙালিয়ানা এখন চোখে পড়ে না। এখনো পঞ্চাশোর্ধ অনেকের মাঝেই শৈশবের স্মৃতিগুলো তাড়িয়ে বেড়ায়। বৈশাখীমেলা সার্বজনীন অনুষ্ঠান হিসেবেই তারা পালন করতে দেখেছে; পালনও করেছে।
আধুনিক এই যুগ যাত্রায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাসমূহ এখন অনেকটাই তার চরিত্র বদলে আধুনিকতার নামে ভিন্ন পথে ঝুঁকে পড়েছে। এর মাঝে তাকে নানা উত্থান পতন ও অবক্ষয়ের ধকল সইতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামীণ জনপদের মেলাগুলো কিছুতেই তার ঐতিহ্য বিলুপ্তির কিনারায় পৌঁছায়নি। গ্রামীণমেলাগুলো এখন আগের সনাতন চেহারা থেকে রূপান্তরিত হয়ে আধুনিকতায় স্নো-পাউডারের প্রলেপে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।
মেলা উদ্্যাপনের উপলক্ষ
মেলা উদযাপনের স্বাভাবিক উৎসকথা হচ্ছে কোনো এক উপলক্ষ। কিন্তু উপলক্ষ যা-ই থাকুক গ্রামীণমেলার একটা সর্বজনীন রূপ আছেই। এদেশের মেলায় অংশগ্রহণে সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিন্নতা কোনো দিনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। গ্রামীণ জনপদের সব মেলাই আর্থ-সাংস্কৃৃতিক বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে মানুষের মধ্যে মিলনকথাকেই প্রকাশ করে থাকে। সে কারণে এদেশের মেলায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও শ্রেণির মানুষের আনাগোনা ঘটে। অতএব, গ্রামীণমেলা মানে মৈত্রী সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র। নারী-পুরুষ, শিশু -কিশোর সকলেই আসে এই মেলাতে।
এখানে সকলের অভিন্ন আকাক্সক্ষাও থাকে। সে আকাক্সক্ষা একটিই, আর তা হলো- মেলা দেখা। যার সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে আরেকটি বিষয় জড়িয়ে থাকে, তা হচ্ছে-বিকিকিনির আশা আর বিনোদনের টান। মেলাতে গাঁয়ের বধূর ঝোঁক থাকে আলতা-সিঁদুর-স্নো-পাউডার-সাবান আর ঘর-গৃহস্থালির টুকিটাকি সামগ্রীর প্রতি। আরেকটি আকর্ষণ থাকে বিনোদনের প্রতি, আর তা হচ্ছে- যাত্রা, পুতুলনাচ বা সার্কাস প্রদর্শনী দেখা। যেমন- নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ম্যাজিক, সার্কাস, যাত্রা, বাউল-ফকির বা কবিগান, বায়োস্কোপ, লাঠিখেলা, কুস্তি, জারিগান ইত্যাদি। কিছু কিছু মেলাকে মাতিয়ে রাখে সং-এর কৌতুক ও মশকরা, তারা স্বাধীনভাবে মেলাতে ঘুরে ঘুরে রঙ্গ করে থাকে।

এছাড়া, মেলায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাড়ি-মদ আর জুয়ার আসর বসে থাকে। নেশায় এমন ডুবে এবং জুয়ার খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে অনেকেই। এটা বাংলাদেশের মেলার একটি প্রাত্যহিক চিত্র। তবে, শিশু-কিশোরদের টান থাকে মূলত খেলনার দিকে, যেমন- মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ। শিশু-কিশোরদের আরেক আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে- খই, বাতাসা, রসগোল্লা, চমচম, কদমা, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর দানাদার নানা ধরনের খাবার। তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলনা বাঁশির কথাও বলা যায়। মেলার প্রাঙ্গণে গিয়ে গ্রামের প্রতিটি শিশু-কিশোরই বাঁশি কিনে এবং তা বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরে। মেলায় যেতে যেতে গাঁয়ের মেঠোপথে শিশু-কিশোরদের দুরন্তপনায় ছুটে চলা ও পাগলা হাওয়ায় দোল খাওয়া সবুজ ধানের খেতে ভাই-বোনের লুকোচুরি খেলা আনন্দটা আরও বাড়িয়ে দেয়। আর মেলা থেকে ফেরার পথে তালপাতার বাঁশি, খেলনা টমটম গাড়ি ও কিশোরীর হাতে কাচের চুড়ির ঝনঝন আওয়াজে মুখরিত থাকে পথ-প্রান্তর।
বৈশাখী মেলার অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য
বৈশাখীমেলার অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যকে কোনোদিনই কোনো ধর্মের গোঁড়ামি খর্ব করতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই বৈশাখীমেলারও রয়েছে অন্যান্য মেলার মতো দুটো দিক। একটি বাণিজ্যিক আর একটি সাংস্কৃতিক। বাংলার ব্যবসায়ীরা চৈত্রের শেষ দিন বা ‘চৈত্রসংক্রান্তি’তে এবং বৈশাখের প্রথম দিনে ‘হালখাতা’ করে থাকে। আসলে ‘চৈত্রসংক্রান্তি’র দিনটা পালন করে বাংলাদেশের মানুষেরা পুরনো বছরকে বিদায় দেওয়ার উৎসব করে থাকে।
এতে মেলা, গান-বাজনা ও খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে বাংলার একটা বছর বিদায় নেয় এবং নতুন একটা বছরের সূচনা হয়। এই দেশে তাই বৈশাখীমেলার সূচনা হয় বৈশাখের আগে থেকেই মানে চৈত্রের শেষ দিক থেকে। তবে, বৈশাখের প্রথম দিনটিই আসলে উৎসবের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সবাই পরিষ্কার ও সুন্দর জামা-কাপড় পরে। ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। আর ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছোটে মেলাতে।
তালপাতার রঙিন বাঁশি
বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কৃষক, কামার, কুমোর, তাঁতি, ময়রা এবং অন্যান্য শিল্পী-কারিগরেরা যে সব সামগ্রী তৈরি করে, বৈশাখীমেলায় তা প্রদর্শন ও বিক্রি করার সুযোগ এনে দেয়। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য, কুটির শিল্পজাত পণ্য, মাটি ও বেতের তৈরি শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি নিয়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা দোকান সাজায় এই মেলায়। বাঁশ ও তালপাতার রঙিন বাঁশি, ভেঁপু, একতারা, দোতারা, ডুগডুগি, বেলুন, লাটিম, মার্বেল, ঘুড়ি-লাটাই, চরকি, পুতুল, মাটির ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া, কাঠ, কাগজ ও বাঁশের পাখি, মাটির হাঁড়ি-বাসন, কলস, কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা ইত্যাদি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে ছোট ছোট দোকানিরা।
এছাড়া আছে কাঠের আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক, চৌকি, চেয়ার-টেবিল, আলনা, আলমারি, ঢেঁকি, পিঁড়ি, গাড়ির চাকা প্রভৃতি। মেলায় আরও পাওয়া যায় পিতলের হাঁড়ি, কলস, বাসন-কোসন, লাঙল-জোয়াল, লোহার দা, বটি, কুড়ুল, খন্তা, কাঁচি, নিড়ানি, গরুর গলার ঘুঙুর। ময়রারা তৈরি করেন নানা রকমের মিষ্টান্ন দ্রব্যÑ কদমা, জিলিপি, বাতাসা, খাজা, ছাঁচের মিঠাই, খাগড়াই আরও কত কি। বলে রাখা ভালো এসব মিষ্টান্নদ্রব্য মেলাতে আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে মেলার প্রচলিত রীতিকে ধরে। মুড়ি, মুড়কি, খই, চিড়ে, ছাচ খাজা, মোয়া, নারিকেলের নাড়ু, বুট, চানাচুর, বাদাম ভাজা আর দিল্লির লাড্ডু, মটরভাজা, তিলের খাজা আজও মেলায় আগত মানুষের প্রিয় খাবার।
তাঁত বস্ত্র
বৈশাখীমেলার আরেক আকর্ষণ হচ্ছে তাঁতবস্ত্র। এই মেলাতে তাঁতিরা নিয়ে আসে নকশীপাড়ের শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, বিছানের চাদর প্রভৃতি। মেলার একপাশে ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি জামা-কাপড়ও পাওয়া যায়। স্যাকরার দোকানে মেয়েরা ভিড় জমায় রুপা, তামা ও পিতলের গহনা কিনতে। বৈশাখীমেলায় গ্রামের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবন গঠনের উপযোগী কিছু শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে।
এর মধ্যে রয়েছে- পশু প্রদর্শনী, চরকায় সুতা কাটা, গালার কারিগরি, গাছের চারা বা নার্সারি এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রদর্শনী। গ্রামের মেয়েদের তৈরি নানাপ্রকার পাখা, মাদুর, কাঁথা, শিকে, বেত ও বাঁশের তৈরি হরেক রকম জিনিসপত্র সাজানো হয়। আর থাকে উন্নত ধরনের শাক-সবজি, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, শস্যের বীজ প্রদর্শনী ও কেনার ব্যবস্থা।

মেলায় এসে মানুষ আনন্দের উপকরণ খোঁজে। তাই এখানে থাকে আনন্দলাভের নানা আয়োজন। পালাগান, বাউলগান, যাত্রা, কবিগান, গম্ভীরা, জারিগান, পুতুল নাচ, সার্কাস প্রভৃতি বৈশাখীমেলার প্রধানতম সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। দেশজ খেলাধুলাও যে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে তার প্রমাণ মেলে আমাদের বৈশাখীমেলায়। লাঠিখেলা, কুস্তি, হা-ডু-ডু, ঘুড়ি উড়ানো, ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়দৌড়, মোরগের লড়াই, বানরের খেলা ইত্যাদি দেশজ মজার খেলা সবাইকে মাতিয়ে রাখে।
হালখাতা
পহেলা বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এলাকার ব্যবসায়ীদের দোকানে হালখাতা। হালখাতা বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। বছরের প্রথম দিন ব্যবসায়ীরা তাদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করে এদিন হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এজন্য খদ্দেরদের বিনীতভাবে পাওনা শোধ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ‘শুভ হালখাতা’র কার্ডের মাধ্যমে ওই বিশেষ দিনে দোকানে আসার নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করান। খদ্দেররাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুরনো দেনা শোধ করেন। অতীতে ব্যবসায়ীরা লাল কাপড়ে মোড়ানো একটি মাত্র মোটা খাতায় তাদের যাবতীয় হিসাব লিখে রাখতেন। এই খাতাটি বৈশাখের প্রথম দিন নতুন করে হালনাগাদ করা হতো। এই হিসাবের খাতা হালনাগাদ করা থেকেই ‘হালখাতা’র উদ্ভব। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোটো-বড়ো-মাঝারি যে কোনো দোকানেই এটি পালন করা হয়ে থাকে। মূলত পহেলা বৈশাখ সকালে সনাতন ধর্মাবলম্বী দোকানি ও ব্যবসায়ীরা সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বিত্তের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করে থাকেন এই কামনায় যে, তাদের সারা বছর যেন ব্যবসা ভালো হয়। দেবতার পূজার্চনার পর তার পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুরে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত ও চন্দনচর্চিত খাতায় নতুন বছরের হিসাব-নিকাশ শুরু করে। এদিন গ্রাহকদের আপ্যায়নে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, লুচি, মালপোয়া, পানতোয়া, ফল পরিবেশন করা হতো। এটিও ছিল আনন্দের অন্যতম বিষয়। বছরজুড়ে কোনো দোকান থেকে বাকি সদাই না করলেও প্রভাবশালী পরিবারের কারণে স্থানীয় সব মহাজন এবং অন্যান্য দোকান থেকে দেবী লক্ষ্মী ও দেবতা গণেশের ছবি আঁকা হালখাতার কার্ড পাঠানো হয়ে থাকে অনেকের বাড়িতে।
৭৪ শুভেচ্ছা কার্ড
পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাতে নিজ হাতে বানানো শুভেচ্ছা কার্ড এখন আর দেওয়া হয় না। তবে মনে পড়ে বৈশাখ আসার পনেরো দিন আগে থেকে আর্টপেপার আর রেইনবো কালার বক্স কিনে কার্ড বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। এই কার্ডগুলো নিয়ে আমার বাড়িতেই প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন আমার বড়ো ভাই। থাকত পুরস্কারের ব্যবস্থা। ওই অনুষ্ঠানগুলোতে ঢাকা থেকে কখনো কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু কবি জুলফিকার হায়দার, কবি আল-মুজাহিদী, কখনো প্রয়াত সাংবাদিক ও কবি এবং আমাদের পারিবারিক বন্ধু অরুনাভ সরকার উপস্থিত থাকতেন। প্রতিবারই আমি পুরস্কৃত হতাম বলে কোনো কোনো সময় বড়ো ভাই বিরোধিতা করতেন অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু বিচারকদের বিচারে আমি প্রথম হতাম। এসবই এখন প্রযুক্তি দখল করে নিয়েছে। পহেলা বৈশাখে গ্রামীণমেলাগুলো এখন খুব মিস করি। মাটির ব্যাংক, ঘোড়া, হাতি, সিংহ, বাঘসহ রকমারি পণ্যের দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপন এখন আর তেমন দেখতে পাই না। তবে এখনো মির্জাপুরের সরিষাদাইড়, মহেড়া জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গণ, জামুর্কি, ভাদগ্রাম, দেওহাটা, ওয়ার্সীসহ অনেক জায়গায় বৈশাখীমেলা হলেও সেই আগের প্রাণ আর নেই। মেলার মুড়ি-মুরকি, মোয়া, বিন্নি ধানের খই, সাজ (চিনির তৈরি হাতি, ঘোড়া, ঝাউ গাছ, বট গাছের আকৃতির তৈরি এক ধরনের শুকনো মিষ্টি), জিলাপির ওপর মৌমাছির গুনগুন শব্দটা এখনো কানে ভাসে। ছোটো ছোটো মেয়েরা বেদেদের ঝুড়িতে রাখা নানা আকৃতির চুড়ি কিনে রিনিঝিনি শব্দ করে মেলার মাঠ শব্দময় করে দিত। মেলায় শুধু আনন্দ হতো তাই নয়, বৈশাখীমেলাকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্য হতো সেটাও অনেক বড়ো বিষয় ছিল।
সিরাজগঞ্জে কোথায়
কোথায় মেলা
সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কালিয়া কান্দাপাড়া গ্রামে প্রতি বছরই বসে এমন এক ঐতিহ্যবাহী মেলা। শতবছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা মেলাটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সায়দাবাদ, শিয়ালকোল ও বাগবাটি কাঠের মেলাটিও ঐতিহ্যপূর্ণ। এসব মেলা একদিন থেকে সাত দিনব্যাপী হয়ে থাকে। বৈশাখ উপলক্ষে কামারখন্দের বিয়ারা ও উল্লাপাড়ার আঙ্গারু মেলাটি চলে মাসব্যাপী। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রত্যেকটি শনিবারই এ মেলা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই থেকে আড়াইশ বছর ধরেই এ মেলা চলে আসছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।
এছাড়াও চৈত্রসংক্রান্তি আর বৈশাখ উপলক্ষে অসংখ্য মেলা বসে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জ। শতাব্দী ধরে চলে আসা মেলাগুলোর কথাই লোকমুখে বেশি প্রচারিত। এর মধ্যে সদর উপজেলার কালিয়া, শিয়ালকোল, সয়দাবাদ, বাগবাটি, কাজিপুরের ভানুডাঙ্গা, চরকাদহ, মাথাইলচাপড়, নাটুয়ারপাড়া, তাড়াশের বারুহাস, গুরমা, উল্লাপাড়ার আঙ্গারু, লাহিড়ীপাড়া, রায়গঞ্জের সিদ্ধেশ্বরী, গুইয়াবানি, ভূইয়াগাঁতী ও কামারখন্দের বিয়ারাসহ জেলার অর্ধ শতাধিক স্থানে ঐতিহ্যবাহী বৈশাখীমেলা বসে।
সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কালিয়ায় প্রতিবছরই বসে এমন এক ঐতিহ্যবাহী মেলা। শত শত বছর ধরে চলে আসা মেলাটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সয়দাবাদ, শিয়ালকোল ও বাগবাটি কাঠের মেলাটিও ঐতিহ্যপূর্ণ। এসব মেলা একদিন থেকে সাত দিনব্যাপী হয়ে থাকে। বৈশাখ উপলক্ষে কামারখন্দের বিয়ারা ও উল্লাপাড়ার আঙ্গারু মেলাটি চলে মাসব্যাপী। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রত্যেকটি শনিবারই এ মেলা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই থেকে আড়াইশ বছর ধরেই এ মেলা চলে আসছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।
বৈশাখীমেলা এখন গ্রাম থেকে শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা ও উপজেলা শহরের নাগরিকরাও এখন বৈশাখী উৎসবে অংশ নিয়ে থাকেন। সকালে শোভাযাত্রা আর শহরের বিভিন্ন স্থানে পান্তা-ইলিশের মেলার পাশাপাশি লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই নববর্ষ পালন করা হয়। এ বছর শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ^বিদ্যালয় বৈশাখীমেলায় ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বর্বর হামলা প্রতিচ্ছবি এঁকে প্রদর্শন করা হয়েছে।
এলাকার মানুষের কথা
কালিয়াকান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, কালিয়া কান্দাপাড়ার মেলাটি ঐতিহ্যপূর্ণ। মেলাটি একসময় চৈত্র মাসের শেষের দিক থেকে শুরু করে পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত চলত। মেলা উপলক্ষে কালিয়াসহ আশপাশের অন্তত ৫০ গ্রামে চলতো উৎসব। বাড়ি বাড়ি থাকতো আত্মীয়স্বজনের ভিড়, মেয়ে ও জামাইদের কলরব। তিনি বলেন, মেলায় আমরা যাত্রাপালা দেখতাম। কোনো কোনো বছর চলচ্চিত্রের শিল্পীদেরও এ যাত্রায় অভিনয় করানো হতো। এছাড়া পুতুল নাচ, সার্কাস, সাপখেলা, লাঠিখেলা, বাদর নাচসহ নানা চিত্তবিনোদনের আয়োজন থাকতো মেলায়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বর্তমানে মেলাটির ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। জেলা প্রশাসন থেকে মেলার অনুমোদনও দিতে নানা গড়িমসি করা হয়।
ঐতিহ্যবাহী আঙ্গারু মেলা সম্পর্কে সলঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান বলেন, প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে এ মেলাটি বসত। মেলার জন্য কোনো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানান দিতে হয় না। দূর-দূরান্তের মানুষ তিথি অনুযায়ী আগেই এসে জমায়েত হতো।
পহেলা বৈশাখে অপর ঐতিহ্যবাহী মেলা তাড়াশের বারুহাস। চলনবিলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। বারুহাস ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোক্তার হোসেন বলেন, শুধু সিরাজগঞ্জ নয়, অর্ধশত মাইল দূর থেকে পার্শ্ববর্তী বগুড়া ও নাটোর জেলার মানুষও এ মেলায় কেনা-বেচা করতে আসেন। এক সময় রাস্তাঘাট না থাকায় দুর্গম অঞ্চলে বসা এ মেলায় মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে মানুষ আসতেন। এক সময় বৈশাখীমেলা উৎসবমুখর থাকলেও ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলো বর্তমানে বন্ধ হতে চলেছে।
মেলায় আধুনিকতার ছোঁয়া
সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ মেলাতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এদেশের গ্রামীণমেলার স্বাভাবিক ও সাধারণ চিত্র কুটির শিল্পজাত গ্রামীণ পণ্যের বদলে দেশী-বিদেশী চোখ ধাঁধানো বাহারি পণ্যের জৌলুস ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী চ্যানেলে প্রচলিত কাটুনের চরিত্রের মুখ ও নকশা এখন প্লাস্টিক ও বাতাস দিয়ে ফোলানো বেলুনের ওপর শহর থেকে গ্রামের মেলায় বাতাসে উড়তে দেখা যায়। বিশেষ করে জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র মটু-পাতলু সারা বাংলাদেশের মেলাগুলোতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলোই এখন শিশুদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে গেছে।
এদেশের বহু নাগরিক প্রয়াসের সঙ্গেই বাংলায় প্রচলিত মেলার লৌকিক ধারা এসে মিশেছে। যেমন- বৈশাখীমেলা, ঈদমেলা, বইমেলা, বিজয়মেলা ইত্যাদি মূলত এদেশে প্রচলিত মেলার লোকধারার প্রেরণা নিয়ে নতুন আঙ্গিক ও মাত্রায় আজ নগরজীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং তা এর মধ্যেই ঐতিহ্যে পরিণতি লাভ করেছে। এমত ধারায় সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে বিজয়মালা, যা যথার্থ অর্থেই ‘ঐতিহ্য ও আধুনিক চেতনার অপূর্ব সমন্বয়’। বর্তমানে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এদেশের মেলায় এখন হর-হামেশাই মাইকে বা সাউন্ড বক্সে উচ্চ আওয়াজে গান বাজে। মেলায় পসরা সাজিয়ে বসা দোকানে দোকানে এখন মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে ইউটিউব থেকে পছন্দমতো গান বেছে নিয়ে তা সাউন্ডবক্সে বাজানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো করা হয়।
বৈশাখী মেলার সূচনা
সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলাবর্ষ নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। বৈশাখ হচ্ছে বাংলা সনের প্রথম মাস। ঐতিহাসিকদের তথ্যমতে, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল থেকে যখন বাংলা সনের গণনা শুরু হয় তখন বছর সূচনার মাস হিসেবে বৈশাখকেই প্রথমে রাখা হয়। অনেকের ধারণা, সম্ভবত তখন থেকেই নববর্ষ উদ্্যাপনের অংশ হিসেবে বৈশাখীমেলার সূচনা। বৈশাখীমেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এ মেলা ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালির মেলা।
বাবু ইসলাম, সিরাজগঞ্জ
প্যানেল