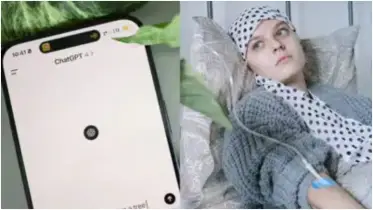.
পরনে দক শাড়ি, দক মান্দি। কারো লাল, কারো সবুজ, কারো নীলসহ বিভিন্ন রঙের মান্দি নারীদের পরনে দক শাড়ি ও দক মান্দা। মাথার ওপরে কপালে প্যাঁচ দিয়ে পিঠে বাঁশের তৈরি খাচির মতো। এ বিশেষ ধরনের খাচির নাম খক মান্দি। কোনো কোনো এলাকায় খকখ্রেং বা খক বলে থাকে। তবে টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে খক মান্দি বলে থাকে আবিমার মান্দিরা। আবার শেরপুর অঞ্চলে খকখ্রেং বা খক বলে থাকে। খকখ্রেং গারো বা মান্দি শব্দ। খকও মান্দি শব্দ। গারো সম্প্রদায়ের নানা পূজা পার্বন আত্মীয়-স্বজন, আত্মীয় গোষ্ঠীদের বাড়িতে বিয়ে শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে সাংসারিক আচার অনুষ্ঠান ও ওয়ানগালাতে নানা শস্য, খাবার জিনিসপত্র বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ খক মান্দি। মান্দিদের নানা অনুষ্ঠানে পিঠে খক মান্দি নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায়। মান্দিরা তাদের সাংসারিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য মনে করে তারা বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে যাচ্ছে। খক মান্দি তৈরির কারিগরের অভাবে ব্যবহার আগের চেয়ে কম বলে মনে করেন অনেকেই। তবে এখন মান্দিদের মধ্যে অনেকেই নতুনরূপে আধুনিক মানের খক মান্দি তৈরি শুরু করেছে।
টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার বিভিন্ন গারো বা মান্দি পল্লী ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খক মান্দি তাদের আদি ঐতিহ্য। বংশ পরম্পরায় তারা বিয়ে সাদিতে মেয়েদের জন্য জামাই আনতে বেয়াই বাড়িতে যাওয়ার সময় খক মান্দিতে শূকর, মোরগ, চাল, চিনি, চা, পান, সুপারি, মিষ্টি, চু (পানীয়)সহ নানা জিনিসপত্র ভরে নতুন গামছা বা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার ফেরার সময় বেয়াই বাড়ি থেকে ভাত, তরকারিসহ নানা খাদ্য সম্মান করে দিয়ে দেয়। ফিরে এসে আবার ঘরের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেন। এটা কোনো সাধারণ কাজে ব্যবহার হয় না। শ্রাদ্ধ বাড়িতে আত্মীয়দের জন্য খক মান্দিতে ভরে শূকর, মোরগ, চাল, চিনি, চা, পান, সুপারি, চুসহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে জমা দিলে নাম লিখে নাম রেখে দেন। পরে আবার নিজেদের বিয়ে সাদি শ্রাদ্ধতে ওই সম পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে তারা আসে। এই রীতিতে চলে আসছে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানসহ নানা পর্ব। এসব সাংসারিক কাজে এই খক মান্দি ব্যবহার হয়ে থাকে। মধ্যম সারি থেকে ওপর দিকে বৃত্তবান মান্দিদের প্রায় বাড়িতেই রয়েছে খক মান্দি। ওয়ানগালা উৎসবসহ নানা উৎসবেও ব্যবহার করা হয় খক মান্দি।
পীরগাছা গ্রামের চিত্রা নকরেক জানান, তাদের ঐতিহ্যের খক মান্দি। তারা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে জিনিসপত্র বহন করার কাজে ব্যবহার করে থাকে। তিনি খক মান্দিসহ মান্দিদের বাঁশের তৈরি নানা জিনিসপত্র তৈরি করছে বলে জানান। মরিয়ম নগরের শিল্পী ম্রং জানান, তাদের এলাকায় খকগ্রেং বা খক বলে থাকে। আদি থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এখন অনেকটা কমে যাচ্ছে। তবে কোচদের খক ব্যবহার করতে দেখা যায়। তার মতে, পার্বত্য ও সিলেট এলাকায় বেশি ব্যবহার হয়।
জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সাবেক সভাপতি অজয় এ মৃ বলেন, খক মান্দি তাদের বংশ পরম্পরায় একটি ঐতিহ্য। এটা অনেক সম্মানের। আত্মীয়-স্বজন বাড়ি বিয়ে শ্রাদ্ধসহ নানা উৎসবে খক মান্দিতে উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া অনেক সম্মান ও ঐতিহ্যের। তিনি মনে করেন, আগের চেয়ে এর ব্যবহার কমেছে। তার মতে, খক মান্দি তৈরির কারিগরের অভাবে ব্যবহার কমেছে। তার দাবি, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাদের আদি ঐতিহ্যে খক মান্দি ব্যবহার বাড়বে এবং ঐতিহ্যের খক মান্দি তাদের সমাজে সগৌরবে আগামী প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হবে যুগ যুগ টিকে থাকবে বলে তিনি মনে করেন।
আচিক মিচিক সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সুলেখা ম্রং বলেন, বিয়ে সাদিতে গারো রীতিতে মেয়েদের জন্য জামাই আনতে বেয়াই বাড়িতে যাওয়ার সময় খক মান্দিতে শূকর, মোরগ, চাল, চিনি, চা, পান, সুপারি, মিষ্টি, চু(পানীয়)সহ নানা জিনিসপত্র ভর্তি করে নতুন গামছা বা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার ফেরার সময় বেয়াই বাড়ি থেকে ভাত তরকারিসহ নানা খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দেয়। দাওয়াত শেষে ঘরের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেন। এটা কোনো কোনো সাধারণ কাজে ব্যবহার হয় না। আবার, শ্রাদ্ধ বাড়িতে আত্মীয়দের জন্য খক মান্দিতে ভরে শূকর মোরগ চাল চিনি চা পান, সুপারি চুসহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে জমা দিলে নাম লিখে নাম রেখে দেন। পরে আবার নিজের বিয়ে সাদি শ্রাদ্ধতে ওই সমপরিমাণ সামগ্রী নিয়ে তারা আসে। এই রীতিতে চলে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানসহ নানা পর্ব। এসব সম্মানের কাজে এই খক মান্দি ব্যবহার হয়ে থাকে। তার মতে, প্রায় মধ্যম সারি থেকে বৃত্তবান মান্দিদের প্রায় বাড়িতেই রয়েছে খক মান্দি।
সাংসারিক ধর্মের গারো রীতি-নীতি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এ বিশেষ ধরনের খক মান্দি। আগামী প্রজন্মের কাছে টিকিয়ে রাখতে হলে দরকার সচেতনতা, কাঁচামাল ও খক মান্দি তৈরির কারিগর। এজন্য সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।
বনে গারোরাই এখন সংখ্যালঘু
নিজেদের আচিক ভাষায় গারোরা মধুপুর বনকে বলেন ‘আবিমা’ বা ‘উর্বর মাটি’। টাঙ্গাইলের ঝরাপাতার শালবন মধুপুরে প্রথম বসতি স্থাপনকারী গারো জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন এ ‘উর্বর মাটি’তে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। বনের ৬৫ শতাংশ মানুষই বাঙালি। কয়েকশ’ বছর ধরে বাস করলেও ৯৬ ভাগ গারোরই ভূ-সম্পত্তির কোনো দলিল নেই।
মধুপুরের ৪৪টি বনগ্রামে পরিচালিত এক জরিপে এ চিত্র পাওয়া গেছে। বেসরকারি সংগঠন সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এ জরিপ করে। মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় উদাসীনতায় একটি সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠী কী বিপর্যয়ের মুখে আছে, জরিপটি তারই প্রমাণ। নৃগোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ভূমির অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্রকে আমলে নিতে হবে। এটা তাদের দায়িত্ব। গবেষণাটি পরিচালনা করেন সেড পরিচালক ফিলিপ গাইন। গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, বনের আদি বাসিন্দা গারোদের আর্থসামাজিক অবস্থা, এখানকার জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেসলাইন তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতেই এ জরিপ। গারোদের বিপণ্ন্নতার চিত্র উঠে এসেছে এ জরিপে। এর দিকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য।
এখন মধুপুর শালবন বলতে যে অঞ্চলটি বোঝায়, মধুপুর উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নজুড়ে বিস্তৃত। সেডের জরিপ হয় এসব ইউনিয়নের ৪৪ গ্রামের ১১ হাজার ৪৮টি পরিবারের ওপর। ৪৪টি গ্রামে বাঙালি ও গারো মিলিয়ে সংখ্যা ৪৭ হাজার ৭২৬। এর মধ্যে ৬৪ দশমিক ৬১ শতাংশই বাঙালি। গারোদের সংখ্যা ৩৫ দশমিক ৩৯। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মধুপুরের অরণখোলা ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৮০০। জনসংখ্যার প্রায় সবাই ছিল গারো, কিছু ছিল কোচ। ব্রিটিশ আমলের আগে মধুপুরের বন টাঙ্গাইলের পন্নীদের মালিকানা ছিল। একপর্যায়ে নাটোরের মহারাজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয় বনটি। ১৯৫০ সালে বনটি বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর মধুপুরের চেহারা পাল্টাতে শুরু করে। অনুপ্রবেশ ঘটে বাঙালিদের।
ভূমির দখল ও মালিকানা মধুপুর বনের একটি জটিল বিষয়। জরিপে ভূমির মালিকানার চিত্রও উঠে এসেছে। মাত্র ৪ শতাংশ গারো পরিবারের এবং ১৩ শতাংশ বাঙালি পরিবারের এবং বসতবাড়ির সিএস অথবা আরওআর (স্বত্ব দলিল) আছে। ৪৪ গ্রামে বাঙালি ও গারো মিলিয়ে সংখ্যা ৪৭ হাজার ৭২৬ এরমধ্যে ৬৪ দশমিক ৬১ শতাংশ বাঙালি গারো আছে ৩৫ দশমিক ৩৯ ভূমির এই বিন্যাস একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে। তা হলো বনের গারোদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের বিষয়ে সরকার ও বন বিভাগের সঙ্গে এক ধরনের দ্বন্দ্ব আছে। সরকার ভূমির ওপর প্রথাগত অধিকার স্বীকার করে না। যদিও বনবাসী মানুষ চায় এ ধরনের মালিকানার আইনি স্বীকৃতি।
মধুপুরের জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক বলছিলেন, ভূমি নিয়ে আমরা এমন এক নাজুক অবস্থায় আছি। যে কোনো মুহূর্তে আমরা উদ্বাস্তু হয়ে যেতে পারি। যে ভূমিতে শত শত বছর ধরে আছি, তাতে আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা প্রথাগত মালিকানার আইনি স্বীকৃতি চাই। বন বিভাগ মাঝেমধ্যেই বনবাসী মানুষদের উচ্ছেদ নোটিস পাঠিয়ে ‘বনভূমি’ থেকে চলে যেতে বলে। বনবাসী মানুষ যদিও এটা উপেক্ষা করেই টিকে আছে। বনবাসী মানুষকে এভাবে অবৈধ দখলদার হিসেবে চিহ্নিত করে সর্বশেষ ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এখনকার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে। গেজেটে বনের অরণখোলা মৌজার শালবনের ৯ হাজার ১৪৫ দশমিক ০৭ একর জমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করে। যেসব বনগ্রাম এই সংরক্ষিত বনের মধ্যে পড়েছে, সেগুলো মূলত গারো-অধ্যুষিত। এছাড়া কিছু কোচ ও বাঙালিও থাকে এসব গ্রামে।
সাংসারিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মান্দি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে। মান্দি মানে মানুষ। বিশেষ করে লাল মাটির টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে গারোদের মধ্যে মান্দি শব্দের প্রচলন লক্ষণীয়। সাংসারিক ধর্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হলেও আপ্যায়ন, খাদ্য, বৈচিত্র্যময় পোশাক, পড়াশোনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পরিচ্ছন্ন বসবাস, সাজানো-গোছানো বাসস্থানসহ নানা পার্বণে রয়েছে তাদের আদি ঐতিহ্যের ছোঁয়া।
তাদের বিভিন্ন পর্বে দিক্কা, চুমান্থি আর বিন্নি ধানের চাল এখনো অনন্য। মান্দি ভাষায় চু তৈরির মাটির পাত্র হলো দিক্কা। চু বা বিচ্চি তৈরির ব্যবহৃত বীজ বা খামিকে চুমান্থি আর তৈরির মূল প্রক্রিয়ায় যে চালটি আদি থেকে ব্যবহার করে আসছে তা হলো বিন্নি ধানের চা। বিয়ে-শাদি, জামাই-বউ নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বিন্নি চাল সমধিক প্রচলিত। বংশ পরম্পরায় টিকে থাকবে মান্দি গারোদের আদি-ঐতিহ্যের এ আপ্যায়ন রীতি, এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।
জানা যায়, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গারো সম্প্রদায়ের লোকদের মঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশ ও ভারতের আসামে বসবাসরত গারো জনগোষ্ঠীর বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চু গুরুত্বপূর্ণ। চু’র উৎপত্তি নিয়ে ভারতের গারো পাহাড়ে বসবাসরত গারোদের মধ্যে লোকগল্প রয়েছে। এক সময় তারা চু পান করা জানত না। চু তৈরির উপকরণ খামি এবং গাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কার তখনো হয়নি। ধীরে ধীরে এর প্রচলন শুরু হয়েছে।
স্থানীয় মান্দিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ এপারকে আবিমা আর ওপারকে আফাল বলে অভিহিত করে থাকে। তাদের মতে, আবিমা হলো মা মাটি। অর্থাৎ মাটির মা। মধুপুর অঞ্চলের মাটির উর্বরতা শক্তির কারণে আবিমা বা মাটির মা বলে তাদের পূর্বপুরুষেরা অভিহিত করে গেছে। আবিমা গারোদের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে ওয়ানগালা, রংচুগালা, মিমাংখাম বা শ্রাদ্ধ, নকনাবা বা নতুন ঘরে প্রবেশ, রান্দি মিকচি গালা বা মৃত. স্বামীর স্মরণ অনুষ্ঠান, বিয়েসহ অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানে খাবার দাবার শেষে আতিথেয়তায় নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বিন্নি ধানের চালের ভাত, পিঠা পরিবেশন করে থাকে। শেষে মেহমানদের সম্মানার্থে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় একই চালের তৈরি চু পরিবেশন করা হয়।
জিনিয়া গ্লোরিয়া ম্রং বলেন, এক সময় গারো পরিবারের শিশুদের চু’র সঙ্গে পরিচিত করতে ভাত খাওয়ানোর সময় হাতের আঙুলে যৎ সামান্য মুখে দেওয়া হতো। এখন সাংসারিক ধর্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হবার পর আর হয় না বললেই চলে। তবে কোনো কোনো এলাকায় এখনো থাকতে পারে। তার মতে, এটা আপ্যায়ন করা তাদের মধ্যে অনেক সম্মানের। শিল্পী ম্র্রংয়ের মতে, বিন্নি ধানের চাল আঠালো। পান-চিনি, জামাই দেখা অনুষ্ঠানসহ বিয়ে-শাদিতে বিন্নি ধানের চালের ভাত, পিঠা পরিবেশন করা হয়। আঠালো থাকার কারণে আত্মীয়তার বন্ধনটাও হবে আঠালো। যুগ-যুগ ধরে এমনটা মনে করে আসছেন তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা। ইদিলপুর গ্রামের পান্না চাম্বুগং বলেন, তাদের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও আতিথিয়েতায় সম্মানিত করতে চু, বিচ্চি আর বিন্নি চালের ভাত পরিবেশন হচ্ছে আদি ঐতিহ্য।
মধুপুর গড়াঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নেতা ইউজিন নকরেক বলেন, তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চু, বিচ্চি, বিন্নি চালের গুরুত্ব রয়েছে। তাদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে দেবতার নামেও চু উৎসর্গ করা হয়। আতিথিয়েতায়ও চু অন্যতম। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার রাতে চুজাঙ্গি করা হয়। এক দেড়মাস আগে থেকেই এ চু তৈরি করা হয়। ভূমিষ্টের রাতে যেসব দাইরা থাকে তারা খেয়ে থাকে। তার মতে, ওই নবজাতকের মুখেও একফোঁটা দেওয়া হয়। এ চু মানতের মতো। চুমান্থি ও বিন্নি ধান তাদের আদি ঐতিহ্য।
হারিয়ে যাচ্ছে গারোদের মাতৃভাষা ‘আচিক’
টাঙ্গাইলের আদিবাসী গারো-অধ্যুষিত মধুপুর অঞ্চল থেকে আচিক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। গারোদের মাতৃভাষা আচিক রক্ষার জন্য সরকারি-বেসরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এ অবস্থা হচ্ছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেছেন। এ ভাষা রক্ষায় গারো শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।
মধুপুরের আদিবাসী নেতা অজয় এ মৃ জানান, আচিক ভাষার লিখিত কোনো বর্ণমালা নেই। কথিত আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত তিব্বত অঞ্চল ত্যাগ করে গারোরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে আসছিলেন, তখন যার কাছে পশুর চামড়ায় লিখিত আচিক ভাষার পুঁথি-পুস্তকাদি ছিল, সেই ব্যক্তি পথে ক্ষুধার জ্বালায় সব পুঁথি-পুস্তক সিদ্ধ করে খেয়ে ফেলেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটি গোপন রাখেন। এ উপমহাদেশে আগমন ও বসতি স্থাপনের দীর্ঘদিন পরে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। কিন্তু ততদিনে গারো বর্ণমালা বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। কারণ, এ উপমহাদেশে প্রবেশের পর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং স্থায়ী বাসযোগ্য স্থান নির্বাচনের জন্য দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে অভিজ্ঞ গারোরা প্রাণ হারান। ফলে আচিক ভাষার বর্ণমালা চিরতরে হারিয়ে যায়। তবে গারোদের মুখে মুখে আচিক ভাষার প্রচলন ছিল।
মধুপুরের গারো ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, একটা সময় ছিল, যখন এ অঞ্চলের গারোরা আচিক ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না বা ব্যবহার করতেন না। কিন্তু জীবন-জীবিকার তাগিদে অথবা লেখাপড়া করতে বনের সন্তান গারোরা এসেছেন তাদের আশপাশে বাঙালি প্রধান এলাকায়। বাঙালিরা গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন আদিবাসী এলাকায়। এভাবে এক সময় নিজ এলাকাতেই আদিবাসী গারোরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন। গারো শিক্ষার্থীদের স্কুলে লেখাপড়া বাংলা মাধ্যমেই করতে হয়। কর্মজীবনে অফিস-আদালতসহ সব কাজেই তাদের বাংলা ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে তাদের মাতৃভাষার চর্চা কমে যায়।
আদিবাসী নেতারা জানান, বাংলাদেশে প্রায় সোয়া লাখ গারো আদিবাসী রয়েছেন। যাদের প্রায় ২৫ হাজারের বসবাস মধুপুর গড় অঞ্চলে। সম্প্রতি মধুপুর গড় এলাকায় বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের অধিকাংশই তাদের মাতৃভাষা ভালোভাবে জানে না। কেউ কেউ নিজ বাড়িতে মা-বাবার মুখে শুনে এ ভাষা সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে শিখলেও তারা আচিক ভাষায় উত্তর দিতে পারে না।
এ প্রসঙ্গে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মধুপুর শাখার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঝুমুর মৃ বলেন, মাতৃভাষা ধরে রাখার জন্য আমরা নিজেরা বাড়িতে সব সময় আচিক ভাষায় কথা বলি। তবু আমাদের ভাষা রক্ষা করা যাচ্ছে না। বাংলার সঙ্গে ক্রমেই মিশে যাচ্ছে। জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক জানান, তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০০৮ সালে গড় এলাকায় ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছিল। যেখানে গারো শিশুদের আচিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। তিন বছর চলার পর দাতা সংস্থার অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।
আদিবাসী লেখক রাখী ম্রং বলেন, বিগত ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতিমালায় শিশুদের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। গারো শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। না হলে আগামী প্রজন্ম হয়ত এ ভাষা হারিয়ে ফেলবে।
ভালো নেই আদিবাসী নারীরা
বৈচিত্র্যময় প্রথাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ দেশের আদিবাসী জাতিগুলো। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, নাচ, গান, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, অলংকার, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি। আরও রয়েছে লোকসাহিত্য। এছাড়া চাষ পদ্ধতিতেও আদিবাসীদের রয়েছে ভিন্ন জ্ঞান, যা মূল জনগোষ্ঠীর কৃষি পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। মূলত আদিবাসী নারীরা হচ্ছেন নিজ সংস্কৃতির ধারক-বাহক। নারীরা তাদের সন্তানদের জন্মের পর থেকে নিজস্ব ভাষা, প্রথাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করান। লোককাহিনী, গান শুনিয়ে মায়েরা তাদের শিশুদের ঘুম পাড়ান। এতে শিশুদের এসব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এছাড়া নিজস্ব পোশাক সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আদিবাসী নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নিজস্ব তৈরি পোশাক দৈনন্দিন জীবনে পরিধান ও বুননের কাজ করে। উৎসবগুলোতে বাদ্য-বাজনার সঙ্গে গান, নাচ পরিবেশন করেন নারীরা। এসব দেখে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও প্রথাগত ঐতিহ্যগুলো চর্চা এবং সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত হয়।
কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক-বাহক এই আদিবাসী নারীরা ভালো নেই। কারণ, মধুপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসী নারীদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত আছে।
মধুপুর বনের গারোরা সর্বপ্রথম ১৮৭৮ সালে তাদের ধানি নিচু জমি ভারতীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধমে রেজিস্ট্রিভুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে আদিবাসীদের জমির মালিকানা ঝুঁকিগ্রস্ত হতে থাকে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালে মধুপুর বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা এবং ১৯৬২ সালে ৪০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে জাতীয় উদ্যান করার ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ সরকার ন্যাশনাল পার্ক বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রাখে। সরকার ১৯৮৪ সালে গেজেট নোটিফিকেশন করে মধুপুর এলাকায় বসবাসরত অধিকাংশ আদিবাসী জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি আদালতে তোলা হলে ভূমি সেটেলমেন্ট অফিস গারোদের কাছে সংরক্ষিত জমির মালিকানার দলিলাদিও শনাক্তকরণে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং আদিবাসীদের রেজিস্ট্রিকৃত জমিগুলো খাসজমি হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে বন বিভাগের লোকজন মধুপুরের আদিবাসীদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে নানাভাবে দমন-পীড়ন শুরু করে।
বিলুপ্তির পথে বহু বর্ষজীবী গাদিলা বৃক্ষ
খুব বেশি দিনের কথা নয়। সত্তর দশকের শেষের দিকেও দেশের তৃতীয় বৃহত্তর লালমাটির টাঙ্গাইলের মধুপুর বনেও আধিক্য ছিল গাদিলা গাছের। বহু বর্ষজীবী এ গাছটির পাতা ছিল ওই সময়ে চাহিদার শীর্ষে। বনাঞ্চলের মানুষের কাছে অতি প্রিয় একটি গাছের নাম। টেকসই দেশী প্রজাতির গাদিলার পাতা ছিল মোটামুটি বড় সাইজের। ছিল শিরা উপশিরায় বিভক্ত। এ পাতা দিয়ে তৈরি হতো বিড়ি। পাতা কেটে সাইজ মতো ভেতরে তামাক ভরে সুতা দিয়ে বেঁধে বিড়ি বানানোর কোনো জুড়ি ছিল না। অবশ্য তখনো কাগজের বিড়ির তেমন প্রচলন শুরু হয়নি। করাচিতে পাতা যেত পূর্ববাংলার এজেন্সিদের মাধ্যমে।
ইফতেখারুল অনুপম
টাঙ্গাইল